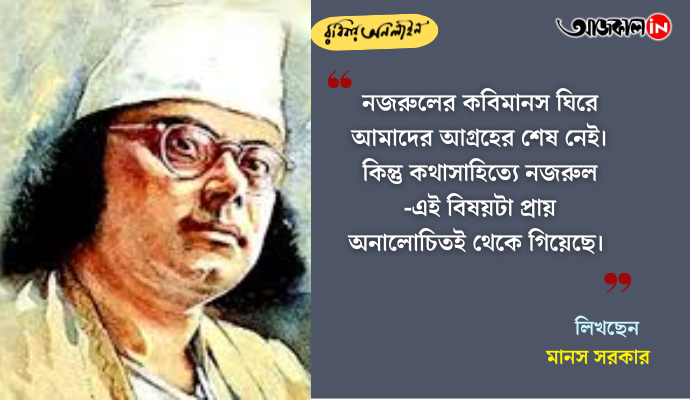
নজরুলের কবিমানস ঘিরে আমাদের আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু কথাসাহিত্যে নজরুল -এই বিষয়টা প্রায় অনালোচিতই থেকে গিয়েছে। লেখকের আলোকপাত সেই অনালোচিত অধ্যায় ঘিরেই-
ঔপন্যাসিক নজরুল ইসলাম সেই বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হননি, যে অনুপাতে ওঁর কবিতা ও গান, এমনকী ওঁর জীবনও আলোচনায় এসেছে। সেই বিস্তৃতিতে আলোচনায় আসেনি ওঁর ছোটগল্পও। কিন্তু কিছু লেখনি সময়ের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সমসময়ে আলোড়ন না তুললেও আমরা পরে হয়তো ঘটনার প্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করি।
নজরুলের গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যাও সুবিশাল নয়। উপন্যাসের সংখ্যা তিনটি – ১. বাঁধনহারা (১৯২৭) ২. মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) ৩. কুহেলিকা (১৯৩১)। সুকুমার সেন ‘জীবনের জয়যাত্রা’ নামে আরও একটি উপন্যাসের খোঁজ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে কোনও নজরুল গবেষক যেমন তার উল্লেখ করেননি, প্রকাশিত রচনাবলীতেও মেলে না সে উপন্যাসটি। কবি এবং গীতিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরেই নজরুল কথাসাহিত্যে এসেছিলেন। ওঁর উপন্যাসের ঘরাণা, বিষয় বা কথন—কোনওটিই বহুল প্রচারিত হয়নি। কবিতা বা গানের নিরিখে কবির কথাসাহিত্যের কথা ভাবলে তা বেশ স্বল্পও। উল্টো দিক দিয়ে এটাও সত্যি পরিমাণের স্বল্পতা কখনওই লেখার মান নির্ণয়ের সূচক নয়। আমেরিকান সাহিত্যিক মার্গারেট মিচেল সারাজীবনে মাত্র একটি উপন্যাসই লিখেছিলেন— ‘গন উইথ দ্য উইন্ড’ এবং ওই একটি রচনার জেরেই অর্জন করেছিলেন প্রবল জনপ্রিয়তা। পাঁচ বছর পরে যে উপন্যাসের শতবর্ষ পালিত হবে, সেই ‘মৃত্যুক্ষুধা’-ই পাঠ করার পর কিছু কথা বলার খিদে যেন বেড়ে গেল। পড়ার আগে অবশ্য মনে হয়নি ‘মৃত্যুক্ষুধা’য় এত জীবন!
নজরুল ব্যক্তিজীবনে রাজনীতিমনস্ক ছিলেন। ইংরেজ বিরোধিতা করার জন্য হাজতবাসও করতে হয়েছে। ‘মৃত্যুক্ষুধা’ উপন্যাসের নায়ক আনসারের মধ্যে আমরা নজরুলের সেই রাজনৈতিক চেতনার সুস্পষ্ট আভাস দেখি। উপন্যাসটি প্রাথমিকভাবে ‘সওগাত’ পত্রিকায় ১৩৩৪ থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বয়ং সুকুমার সেনও এই উপন্যাসকে কালজয়ী হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এ উপন্যাস লেখার আগে তিনি কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক এলাকায় ১৯২৬-২৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের এই চার বছরের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে ওঁর এই কথনে। পড়তে শুরু করলে স্পষ্ট বোঝা যায় সমসাময়িক সময় ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এ লেখায়। উপন্যাস শুরুই হয় লেখকের অদ্ভুত একটি মন্তব্য দিয়ে, ‘পুতুল-খেলা কৃষ্ণনগর’। আরও বেশ কয়েক জায়গায় এই একই কথার পুনরাবৃত্তি আছে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র কি তবে মানুষকে পুতুল করে রেখেছিল, এ প্রশ্ন পাঠকের মনে কিন্তু উঁকি দিয়ে যায়। খিদে আর মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে-লড়তে কি দেশের মানুষের চেহারার দিকে দৃকপাত করার উদ্দেশেই এ হেন মন্তব্য?
কবিত্বের যে আবেগ তা এ উপন্যাসে বেশ ভালমাত্রায় লক্ষণীয়। মানুষের যে জীবন সংগ্রাম তার কথা পড়লে সে ভাবাবেগ আমাদের দৃশ্যতই ছুঁয়ে যায়। উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র প্যাকালে। কখনও সে সখী সাজে, কখনও গান করে বা থিয়েটার দলে নাচে। কাজ করে রাজমিস্ত্রি হিসাবেও। সাংসারিক বাধ্যবাধকতাও তার আছে। মৃত ভাইয়ের স্ত্রী ও সন্তানদের তাকে প্রতিপালনে নিয়োজিত থাকতে হয়। পরিবারের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য যে জীবন সংগ্রাম, তা প্যাকালে চরিত্রকে অন্তত নিম্নবিত্তের যে শ্রেণিচেতনা ও সংগ্রাম, প্রতিনিধি স্থানীয় করে তুলেছে।
এ হেন জীবনসংগ্রামে থেকেও প্যাকালে প্রেমে পড়েছে কুর্শির সঙ্গে, যে কুর্শি ‘ওমান কাতলি’ পরিবারের সদস্য। কিন্তু কুর্শির পরিবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে যে খুব স্বস্তিতে আছে, এমন নয়। পরিবারের দায়িত্ব অন্যদিকে কুর্শির প্রেম-দ্বন্দ্ব চরম হয়ে ওঠে প্যাকালের মধ্যে। বরিশালে গিয়ে খ্রিস্ট হয়ে সে চাকরি নেয় পিয়নের। কুর্শিকে নিয়ে শুরু করে নতুন জীবন।প্যাকালের অনুপস্থিতিতে চরম দারিদ্রে অন্যদিকে তার পরিবার বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। খ্রিস্টান মিশনারীরা এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়ায়। পরিবারের সদস্য মেজবৌকে যখন আনসার খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেছে, সে উত্তর দিয়েছে, ‘আপনারা আমাকে একটু করে খৃষ্টান করেছেন।’ আপনারা বলতে নিশ্চই এখানে সমাজব্যবস্থার কথাই বলা হয়েছে। যে সমাজ বৈধব্যকে কটাক্ষ করে, সেই সমাজ তার সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেয় না। অস্তিত্ব ও সুরক্ষার কারণে একটি পরিবারের সংস্কৃতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিণতিতেই এই নিয়তি- তা কি আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন?
দারিদ্র্য ও অবস্থার সুযোগে ধর্মান্তরিত করার নিষ্ঠুর বাস্তবতা কতদিন, কতবছর আগে নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন, এ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, ভাবলে চমকে উঠতে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তার উত্তর আধুনিক সংস্করণ ঘটে চলেছে বললেও কি খুব ভুল বলা হবে?
ফিরি আনসার চরিত্রে। যৌবন, বিপ্লব ও রাজনীতির আবেগে সে চরিত্র ভীষণ রোমান্টিক। রাজনৈতিক আদর্শের কারণেই ম্যাজিস্ট্রেট-কন্যা প্রেমিকা, নিজের বোন ফতিমার বান্ধবীকে সে পরিত্যাগ করেছে। যদিও আনসারে রাজনীতি যতটা জ্বলজ্বলে, তার প্রণয়পর্ব ততটা নয়। তবে আনসার চরিত্রের রোবোটিক ভাবাবেগ কেমন যেন তাকে ঠিক রক্ত-মাংসের চরিত্র হতে বাধা দেয়। তার গ্রেপ্তার হবার দৃশ্যে সে রোমান্টিক বিপ্লবী, কিন্তু হৃদয়বান প্রেমিক হিসাবে কেমন যেন নিষ্প্রভ। নজরুল ওঁর পূর্ণ কবিত্বশক্তি ও আবেগ দিয়ে আনসারকে গড়লেও বাস্তবের আয়নায় তাকে কোথাও কোথাও যেন কৃত্রিম লাগে। চরিত্র হিসাবে রুবি সংযত, কিন্তু এক অদ্ভুত নীরব বিষাদের নারীমূর্তি। এ উপন্যাসে নারীচরিত্রের নির্মাণে নজরুল বরং অনেক বেশি যত্নশীল, সচেতন। আনসারের গ্রেপ্তারের দিন কৃষ্ণনগর রেলস্টেশনে দূর থেকে তাকে রুবির বিদায় দেওয়ার দৃশ্যটি মননশীল পাঠককে বেঁধে রাখে।
নজরুলের কথাসাহিত্যে হিন্দু, নাকি মুসলিম জীবন প্রাধান্য পেয়েছে -আলোচিত হলেও খুব অবান্তর প্রশ্ন। আজকে এই রকম এক কঠিন সময়ে নজরুল ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। লক্ষ করে দেখার মতো, যে মুসলিম জীবনকে তিনি নিবিড় করে আঁকছেন, সে ভাষ্যে অহিন্দু বা অমুসলিমদের প্রতিও ওঁর কোনও বিরূপতা নেই। আবার সে বলায় কোনও কৃত্রিমতাও নেই। একেই বলে সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে অসাম্প্রদায়িকতা। সমাজ বাস্তবতায় ধর্মের পর্দা থাকে না। শুধু ধর্ম কেন, রাজনীতি, প্রেম কোনও কিছুরই পর্দা থাকে না। ঔপনিবেশিকতার গোপন ছুরি আর পেষণযন্ত্র নাম বদলে আবার ফিরে এসেছে। চারদিকে ভাসছে শুধু নানা মন্তব্য। সে সব দেখা আর শোনার আগে আসুন জীবন পড়ে নিই একবার —‘মৃত্যুক্ষুধা’-য়।