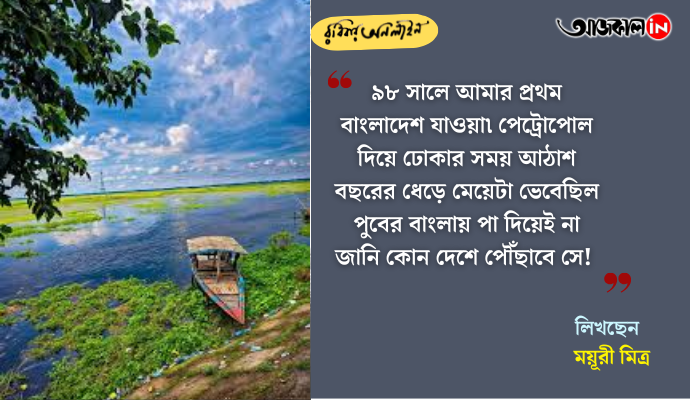
৯৮ সালে আমার প্রথম বাংলাদেশ যাওয়া৷ পেট্রোপোল দিয়ে ঢোকার সময় আঠাশ বছরের ধেড়ে মেয়েটা ভেবেছিল পুবের বাংলায় পা দিয়েই না জানি কোন দেশে পৌঁছাবে সে! হয়ত সে দেশের গাছগুলো মাথায় আরও লম্বা হবে ...এত লম্বা যে ঝড় উঠলেই ছুঁয়ে ফেলবে আকাশ! হয়তো পাখিগুলো নতুন কোনও মিঠে সুর ধরবে! আচ্ছা সেখানের কাকগুলো কি টিয়ের মতো সবুজ হবে! হিমালয়ে যেমন সবুজ টিয়েগুলো মেঘকালো হয়ে ওঠে! চোখে ছবি এঁকে যখন যশোরে ঢুকলাম, দেখলাম বনগাঁ অঞ্চলের গাছপালাই এখানে৷ দু’বাংলার মাটি ভূতাত্ত্বিকভাবে এক৷ এত এক যে দিতে চাইলেও দু’রকম গাছ জন্ম দিতে পারবে না যশোর৷ তখনও শহরে ঢুকিনি৷ দু’পাশে গাছের সারি৷ এক জায়গায় বাস থামল৷ দেখলাম এখানেও শীতের হাওয়ায় পাতা নাচে৷ হাওয়া যেভাবে বইছিল পাতাগুলো পরপর সেভাবে উড়ছিল৷ যেন সীমার ওপারে আমার দেশ থেকে গাছগুলো নদী হয়ে, আমার মায়ের বাপের বাড়ির দেশে এসে পৌঁছোল এই মাত্তর৷ আমার সাথী হয়ে হয়েই এল পশ্চিমবাংলার গাছ৷ আবেগে মানুষের যুক্তিনাশ হয়৷ আমারও তাই হয়েছিল হয়ত৷ কী যে আবোলতাবোল ভাবছিলাম একটি অচেনা পথের ধারে দাঁড়িয়ে৷ যশোর৷ আমার মাতৃদেশ৷ আমার মায়ের বাপের ঘরদুয়োর একদা এখানেই ছিল৷
শীতকাল ছিল৷ দ্রুত চলে যাচ্ছিল বেলা৷ শহরে ঢুকে প্রথমেই ভাত খেলাম৷ ভাত, মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপি, মাছের আলু পিঁয়াজ দিয়ে তরকারি আর স্যালাড৷ বাঁধাকপি, মাছ সবেতে রসুন৷ রান্না চমৎকার তবু এই অপরিচিত গন্ধ মোটে সহ্য করতে পারছিলাম না৷ কী অদ্ভুত মানুষের মন! ফেলে আসা দেশ খুঁজতে এসেছি, তাকে এতটাই নিজের কল্পনার আয়ত্তে আনতে চাইছি যে একটি অচেনা সুন্দরকে মানতেই চাইছে না আমার মন৷ খালি ভেবে চলেছি -তবে যে দিদু বলতেন ...যশোরের রান্নায় ঘি মাস্ট, মাছের ঝোলে আদা জিরে বাটা দিতেই হবে, রাঁধুনি ফোড়নের সুগন্ধ ছাড়া সেখানের মানুষ খাবার মুখে তোলে না ...সব তাহলে ভুল! রসুন মাখা হাত চাটছি আর ভাবছি কবে থেকে এ ভুলের শুরু! মাছের তরকারির সঙ্গে স্যালাড চিবোতে চিবোতে মায়ের বাপের বাড়ির দেশ প্রথমবার আমার কাছে অচেনা লাগল৷ এঁটো হাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগল৷
মা বলে দিয়েছিলেন শহরের মাঝখান খুঁজবি৷ ওখানে আমার হারান কাকার ওষুধের দোকান - রায়চৌধুরী ফার্মেসী৷ দোকানে কাকা এখন আর হয়ত বসতে পারেন না৷ তোর মামা থাকবে হয়ত দোকানে৷ আমার কথা বলবি৷ দেখবি তোকে কত ভালোবাসবেন৷ এমনভাবে বললেন যেন দিনদশেক আগেই হারান কাকার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে এবং আমি যাব বলে রেখেছেন! সেই একলা দুপুরে আমি নিজেও হয়ত তেমনটা ভেবেছিলাম! নতুবা আমিই বা কেন মায়ের কথামতো খুঁজতে শুরু করলাম শহরের মাঝখান!
রায়চৌধুরী ফার্মেসীতে যখন পৌঁছোলাম, বিকেল তখন আমার কোনোদিন না দেখা মামার শরীরে গড়াগড়ি খায়! ঘরটা আধা অন্ধকার! মায়ের নাম শুনে কেবল বললেন- মালপত্তর কোথায় তোমার? চল আগে তোমায় বাসায় পৌঁছে দিই৷ আশরাফ আমার ভাগ্নি এসেছে৷ আমার দোকানটা একটু দেখো ...! আমি বললাম -মামা আজ নাটক৷ সাজানো বাগান৷ কাল যাব দাদুর কাছে৷ ফলের দোকান থেকে চেঁচিয়ে আশরাফ বললেন - লাতিন এসেছে জানলে দাদু যেন ঘরে বসে থাকবে! ও নাটকের হলে হাজির হবে গো!
সন্ধেবেলা নাটক শুরু হল৷ মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান৷ একটি দৃশ্যে ছিল বাঞ্ছারামের মৃত্যুকামনা করে জমিদার কালীপুজো করছে৷ জমিদার গিন্নি ফলপাকুড় কেটে মাকে সাজিয়ে দিচ্ছে৷ পুরুত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে৷ মঞ্চে ধুনো জ্বালানো হয়েছিল৷ ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দেখলাম দর্শক ততো আর হাসছেন না৷ আগের দৃশ্যগুলোতে যে হো হো হি হি চলছিল সব বন্ধ৷ জমিদারগিন্নির অভিনয় সেরে মেক আপ তুলছি, এক ভদ্রমহিলা এসে বললেন -এ দৃশ্য করে উত্তেজনা শুধু শুধু বাড়ানো হল৷ কালীপুজোর দৃশ্য বাদ দিয়েও নাটক দাঁড় করানো যেত৷ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল -সে দাঁড় করানো আপনার বোধের অনুগামী হতো বটে তবে শিল্প হত না৷ শিল্পে কখনও অসৎ এর সঙ্গে সমঝোতা করা যায় না৷ বোরখা পরা মহিলা যথেষ্ট শিক্ষিত, অন্তত ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেম অনুযায়ী তো বটেই৷ বললেন -আমার কথায় অসততা কোথায়? আমি নিজের উত্তর প্রস্তুত করলাম৷ মুক্ত মন না নিয়ে শিল্প উপভোগ অসততা৷ গ্রীনরুমের বাইরে আশরফ উঁকি দিচ্ছেন৷ সঙ্গে এক দীর্ঘ শরীরের মানুষ দাঁড়িয়ে৷ লম্বা নাক, পানপাতার মতো চোখ৷ মেয়েদের মতো চোখ থেকেও মুখ পুরুষালি৷ আমার হারান দাদু৷ আশরাফ হাসছিলেন৷
তুমি কি নিজের কথার মান রাখতে নিজেই দাদুকে টেনে এনেছ কাকু? আশরাফকে বললাম৷ সে রাতেই আশরাফ "তুমি" হয়ে গেলেন৷ আর সেই ভদ্রমহিলা দূরে দাঁড়িয়ে মাপছিলেন তাঁর দেশের দু’ ধর্মের দুই মানুষ আর এক বিদেশিনীকে৷ রাতে শুনলাম, নাট্যকারও ওই দৃশ্য নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন৷ এবং বিন্দুমাত্র বিপন্ন না হয়ে স্পষ্ট জানিয়েও দিয়েছেন -ইসলামকে আক্রমণ করার জন্য আমি কালীপুজোর দৃশ্য আঁকিনি৷ একজন চাষীর ওপর একজন জমিদার যে কতভাবে অপ্রেশন চালাতে পারে, তার সবল থাকার মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিতে পারে সেটা দেখানোর জন্যই কালীর কাছে বাঞ্ছার মৃত্যু চেয়ে জমিদারগিন্নির মানতের দৃশ্য লিখেছি৷ কোনও শর্তে নাটক বদলাব না৷ ইচ্ছে করে ভুল বোঝার দায় আমি নেবও না৷
সত্য৷ ভুলের থেকে ইচ্ছেভুল অনেক বেশি দুই বাংলার মানুষকে ছিন্ন করেছে! ভিন্ন করেছে! পরদিন দুপুরে দাদুর বাড়ির মুগডাল, ভাত, কই তেল আর মোহনভোগ খেলাম৷ মামী খুব শান্ত আর নম্র৷ আমায় আপনি করে কথা বলছিলেন! বললাম -মামী কী কর! আমি তোমার ভাগ্নী৷ খেয়ে দেয়ে সাদা বেসিনে আঁচাতে আঁচাতে বললাম -মামী তোমাদের বাড়ি লম্বা পাইপ লাগানো কল আছে?
এই লম্বা পাইপ লাগানো কল যে কী বস্তু আমি আজও জানি না৷ দিদু শুধু একবার গল্প করেছিলেন - যশোরের মেয়েরা কলকাতা শহরে পড়তে যেত৷ আর ফিরে এসে নিজেকে হদ্দ সাহেবি করে তুলত৷ পুকুরে চান না করে বাড়িতে লম্বা কল লাগিয়ে চান করত৷
ভগবান! সেটাই মনে পড়ল এখন? - আশরাফ বলে উঠল৷ বলতে ভুলেছি, সেও সেদিন নেমন্তন্ন খেতে এসেছিল৷ মানুষটা বড়ো জীবনরসিক৷ এইসব মানুষ মুখে কখনও বলে না, ভাই তোমায় আপন করলাম৷ তাঁদের স্পর্শে মানুষ আপন হতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়৷ আসার সময় মামীর কানে কানে বললাম -
মামী যশোরের কই তেলে জিরে আর সর্ষে একসঙ্গে বেটে দেয়৷ কিন্তু তুমি...! আর মোহনভোগের প্লেটে দুটো তিনটে করে আদ্ধেক গলা চিনি ছড়িয়ে দিও৷ কচকচ করে গালে লাগে! এই চিনিগুলো আগে ঘিয়ে ভেজে তুলে রাখবে –
এবার থেকে খেয়াল রেখো ...কেমন! যদিও তাঁর খেয়াল রাখাটা আর আমার দেখাই হয়নি৷ তবু যশোরের বধূকে যশোরের রেসিপিটা বলে এসেছিলাম৷ আশরাফ বললেন -হয়েছে হয়েছে! আমরা চিনি না ভাজলেও কলকাতা থেকে কিশমিশ এনে মোহনভোগে দি৷ ঢাকা গেলাম৷ ভয় করেনি৷ যশোরের লোকেরা ঢাকাকে আরেক বাংলা মনে করতেন৷ তাঁরা মানসিকভাবে অনেক বেশি কাছাকাছি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের৷ ঢাকা তাই আমার কাছে পরদেশ৷ ভিন্ন হবার ভয় শুধু নিজ দেশের মাঝে৷