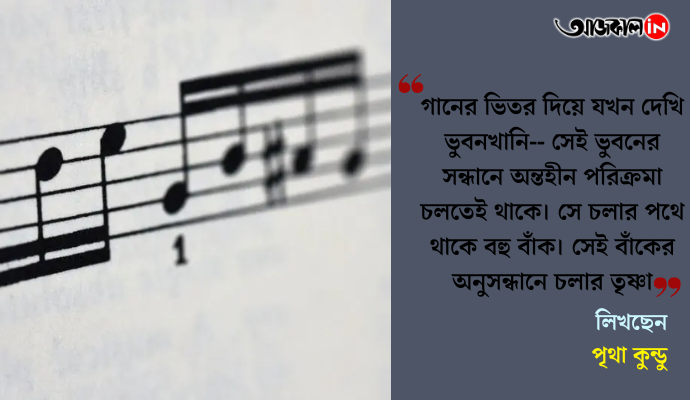গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি-- সেই ভুবনের সন্ধানে অন্তহীন পরিক্রমা চলতেই থাকে। সে চলার পথে থাকে বহু বাঁক। সেই বাঁকের অনুসন্ধানে চলার তৃষ্ণা--
১৯১৪ সালের অক্টোবর মাস। রবীন্দ্রনাথ তখন এলাহাবাদে, তাঁর ভাগ্নে সত্যপ্রসাদের বাড়িতে। সেখানে একদিন পুরনো জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তাঁর হাতে পড়ল একখানি ছবি। দেখে তাঁর মনে হল, “এই কিছুদিন আগে যে আমাদের মাঝে এত সত্য হয়ে, জীবনে এতকিছু হয়ে ছিল, আজ সে কতদূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জীবন ছুটে চলেছে, কিন্তু সে থেমে গেছে ঐখানে।” এই ভাবনারই ফসল ‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থের ‘ছবি’ কবিতাটি, যা পরে রূপান্তরিত হয় বিচিত্র পর্যায়ের এক অনবদ্য গানে, যার মধ্যে প্রেম-প্রকৃতি-পূজা মিলেমিশে একাকার—‘তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা?’ এই গানটিকে তিনি স্থান দিলেন ‘শাপমোচন’-এ— জন্মান্তরে কমলিকার ছবি এসে পড়েছে তার শাপভ্রষ্ট প্রেমিক অরুণেশ্বরের হাতে। কিন্তু মূল কবিতাটি রচিত হয়েছিল যে ছবিখানা দেখে, সেটি আসলে কার, তা নিয়ে বহুদিন ধরে চলেছে বহু জল্পনা। ক্ষিতিমোহন সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এ ছবিখানি কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর, আবার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ জানিয়েছেন, এটি কবির ‘নতুন বৌঠান’ কাদম্বরী দেবীর ছবি। ছবির মানুষটি যে প্রিয়জনই হয়ে থাকুন, ছবি থেকে গান হয়ে ওঠার এই যাত্রা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টির জগতে এক অভিনব দিকের আভাস দেয়। ছবি আর গানের অন্তর্লীন সংযোগ তাঁকে বরাবরই টানত; যৌবনে রচিত একটি কাব্যগ্রন্থের নামও রেখেছিলেন ‘ছবি ও গান’। পরিণত বয়সে ছবির অনুষঙ্গে একাধিক গান রচনার আভাস যেন লুকিয়ে ছিল এর মধ্যেই।
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদার— রবীন্দ্রনাথের দিদি শরৎকুমারী দেবীর দৌহিত্র। ১৯১১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে কলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রবিদাদামশায়’ বা সংক্ষেপে ‘রবিদা’। স্মৃতিচারণমূলক ‘রবিতীর্থ’ বইটিতে অসিতকুমার জানিয়েছেন, কীভাবে তাঁর আঁকা ‘দিব্যপ্রজ্ঞা’ ছবিটি দেখে কবির কলমে সৃষ্টি হয়েছিল ‘তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে’। ১৯১৪ সালের গরমের ছুটিতে অসিতকুমার কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলেন রাঁচিতে। এই সময় একদিন তাঁরই ছাত্র মুকুলচন্দ্র দে কবির কাছে গিয়ে আবদার করলেন, ছবি আঁকার বিষয়বস্তু বলে দিতে হবে। মুকুলচন্দ্রও কবির অত্যন্ত স্নেহভাজন, তাঁর কাছে অবাধ যাতায়াত ছিল এই তরুণ শিল্পীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলে দিলেন, ‘আমার উপযুক্ত একটি সরস্বতী আঁক, দিব্যপ্রজ্ঞা—ক্যালেন্ডারের সরস্বতী চাই না।’ মুকুলচন্দ্র একটির পর একটি সরস্বতীপ্রতিমা এঁকে চললেন, কিন্তু একটিও কবির মনে ধরল না। অগত্যা তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। কবির অচরিতার্থ কল্পনা কিন্তু এত সহজে নিরাশ হতে চায় নি। গ্রীষ্মের ছুটির পর অসিতকুমার শান্তিনিকেতনে ফিরে এলে কবি তাঁকে সব কথা জানালেন। ঠিক কেমন সরস্বতীপ্রতিমা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন ‘দিব্যপ্রজ্ঞা’ রূপে, তার খানিকটা ধারণাও দিলেন। অসিতকুমারের কথায়, ‘তিনি যেভাবে বর্ণনাকালে জ্যোতিদৃপ্ত ভাব প্রকাশ করেছিলেন তাতে তাঁর সরস্বতীর আভাস পেয়ে একটি জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী আঁকলুম। রঙিন ছবিটি সম্পূর্ণ করে রবিদার সামনে ধরতেই তাঁরও মনে সুরের রং ধরল, তিনি তুড়ি দিতে দিতে তাল দিয়ে গুঞ্জন করে রচনা করলেন, ‘তুমি যে সুরের আগুন’। যথানিয়মে দিনুদার মারফৎ এ গান আশ্রমবালকেরা শিখে নিল।’ ছবিটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কেন এই সৃষ্টি কবির মনে সুরের আগুন ধরিয়েছিল। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী প্রতিমার চারপাশে গৈরিক আগুন যেন গলিত সোনার মত ছড়িয়ে আছে।

ছবি - দীক্ষা শিল্পী - নন্দলাল বসু
ছবির অন্তর্নিহিত ভাব অবলম্বনে গান রচনার বিষয়টি কবিকে এতটাই তৃপ্তি দিয়েছিল, যে পরবর্তীকালে তিনি অসিতকুমারের আঁকা গ্রামবাংলার মানুষজন, পথঘাট, প্রকৃতি-বিষয়ক রেখাচিত্রের কিছু নমুনা কবি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এর মধ্যে এক-একটি ছবির ওপর তিনি গান রচনা করবেন, সেই গানগুলি সংকলিত হয়ে প্রকাশ পাবে ‘চিত্রবিচিত্র’ নামে একটি বইতে। এর মধ্যে একটি ছবিতে ছিল, এক গ্রাম্য বধূ ঘড়া নিয়ে ঘাটের ধারে আনমনা হয়ে পড়েছে, জল ভরার কথা ভুলে গিয়ে সে একটি একটি করে পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ছবিটি দেখেই কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে অসিতকুমারকে বলেছিলেন, ‘জানিস তুই এ কী করেছিস? এই ছবিতে তুই লিরিককে মূর্তি দিয়েছিস —এ ছবি গীতিকাব্যসুন্দরী।’ এই ছবির অনুপ্রেরণায় রচিত হল ‘একলা বসে একে একে অন্যমনে’ গানটি।
অসিতকুমারের আঁকা আরও কয়েকটি ছবি থেকে গান রচনা করেছিলেন কবি, তবে ছবি থেকে রচিত গান নিয়ে ‘চিত্রবিচিত্র’ সংকলনটির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। অসিতকুমার জানিয়েছেন, এই প্রস্তাবিত বইটির মলাটের নকশাও এঁকে ফেলেছিলেন তিনি। কবির প্রয়াণের অনেক পরে অবশ্য ‘চিত্রবিচিত্র’ নামে ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কিছু ছড়া ও কবিতার সংকলন প্রকাশ করে বিশ্বভারতী, কিন্তু এই বইটির সঙ্গে কবির নিজের পরিকল্পনার কোনও সম্পর্ক ছিল না।
শান্তিদেব ঘোষ তাঁর ‘রবীন্দ্রসংগীত’ গ্রন্থে এরকম আরও কয়েকটি ‘গানের ছবি’র গল্প শুনিয়েছেন। নন্দলাল বসুর আঁকা ‘দীক্ষা’ ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে কবি রচনা করেছিলেন পূজা পর্যায়ের ‘নিভৃত প্রাণের দেবতা’ (১ জানুয়ারি ১৯১০) গানটি। এই ছবিতে দেখা যায়, এক বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁর পুত্র বা শিষ্যকে পূজারতিতে দীক্ষিত করছেন। ছবিটি ভারতী (১৩১৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। চিত্রপরিচিতি হিসাবে লেখা হয়েছিল, ‘এই চিত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, কেবল কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবিখানি উপলক্ষ্য করিয়া যে গানখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।’ এরপর গানটি দেওয়া হয়েছিল, খানিক পাঠান্তরে। ‘ওগো বধূ সুন্দরী’ গানের পিছনেও রয়েছে আর একটি ছবির ইতিহাস।
রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর কন্যা মঞ্জুশ্রী ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রথম দুই ছাত্রীর অন্যতম—কবির অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। ১৩৩১ সনের চৈত্র মাসে মঞ্জুশ্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। সেই উপলক্ষ্যে উপহার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ লিখে দেন একটি কবিতা—‘ওগো বধূ সুন্দরী নব মধুমঞ্জরী/ সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন’। এর কিছুদিন আগেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকেছিলেন ‘সাত ভাই চম্পা’ নামে একটি ছবি, সাদা, কালো আর হলুদের মিশেলে। সেই ছবির অনুষঙ্গ জড়িয়ে গেল বিবাহের উপহার-লিপিতে। পরে ১৩৪১ সনের বসন্ত উৎসবের জন্য এই কবিতাটিতে সুর দিয়ে গানে রূপান্তরিত করেন তিনি। গানের কথাও একটু বদলে গিয়ে হয় ‘ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী/পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন।’
ছবি - সাতভাই চম্পা, শিল্পী - গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ছবি থেকে গান সৃষ্টি যেমন হয়েছে একাধিকবার, তার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ আগে গান, পরে ছবি— এভাবেও বেশ কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ঘিরে। ‘নটীর পূজা’য় শ্রীমতীর নাচতে নাচতে অলঙ্কার খুলে ফেলে আত্মনিবেদনের দৃশ্যটির অনুষঙ্গে, ‘আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো’ গানটির এক অনবদ্য চিত্ররূপ দিয়েছিলেন নন্দলাল বসু। ‘নটীর পূজা’য় নটরাজ ছিলেন পশ্চাৎপটে, ঋতুরঙ্গশালায় তিনিই নায়ক। এই ঋতুনাট্যে গান সুরের স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু প্রতিটি গানের ভাব আর ভাষ্য চিত্রধর্মী। শান্তিনিকেতনে ১৩৩৩ সনের বসন্ত উৎসবে অভিনীত হওয়ার পর ‘বিচিত্রা’র প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩৪) ‘নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা’ প্রকাশ পায় নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি-সহ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার ধারায় এই সময় থেকে দেখা যায়, গান আর ছবি যথার্থই হাত ধরাধরি করে চলেছে। ‘বৈশাখ-আবাহন’ ছবির সঙ্গে গান ‘এসো হে বৈশাখ’, ‘শরতের ধ্যান’ ছবির সঙ্গে ‘আলোর অমল কমলখানি’, ‘দীপালি’র সঙ্গে ‘হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে’-- ‘নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা’র গানের সামগ্রিক চিত্ররূপ যেন নন্দলাল বসুর অলঙ্করণ ছাড়া ভাবা যায় না।
রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টিযাপনের শেষ পর্বে বিকশিত হয়েছিল তাঁর চিত্রকলা। সবচেয়ে বেশি ছবি এঁকেছেন তিনি জীবনের শেষ দশ-পনেরো বছর। এক বিচিত্র, রহস্যময় জগতের আভাস মেলে তাঁর ছবিতে। অন্যদিকে তাঁর এই পর্বে লেখা গানেও চিত্ররূপময়তা এসেছে অনেক বেশি। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯) নিজেই জানিয়েছেন, “এই টলমলে অবস্থায় এখনকার মত দুটো স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের—গান আর ছবি।” ‘সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে’, ‘প্রহরশেষের আলোয় রাঙা’, ‘আমার প্রিয়ার ছায়া’, ‘দিনান্তবেলায় শেষের ফসল’, ‘ওগো সাঁওতালি ছেলে’-র মত এক-একটি গান যেন চিত্রভাষাকেই রূপ দিয়েছে সুরে সুরে। বিশেষ করে মনে আসে ‘কৃষ্ণকলি’র কথা। কীর্তন-কথকতার ধাঁচে সুরের কাঠামোয় মল্লার আর কেদারার গভীর ছোঁয়ার সঙ্গে যেন মিশেছে তুলির টান, স্তবকের পর স্তবক জুড়ে রূপ নিয়েছে একটি সম্পূর্ণ ছবি। মরমী শিল্পীর কণ্ঠে আর শ্রোতার মননে যখন ছবিখানা তৈরি হয় গানটির সার্থক পরিবেশনে, তখন সত্যি মনে হয়—এ গানের স্রষ্টা শুধু কবি-সুরকার নন, চিত্রকরও। ছবি তো কেবল অবন ঠাকুর লেখেন না, তাঁর ‘রবিকা’ও যে লেখেন, সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন!
(চলবে)