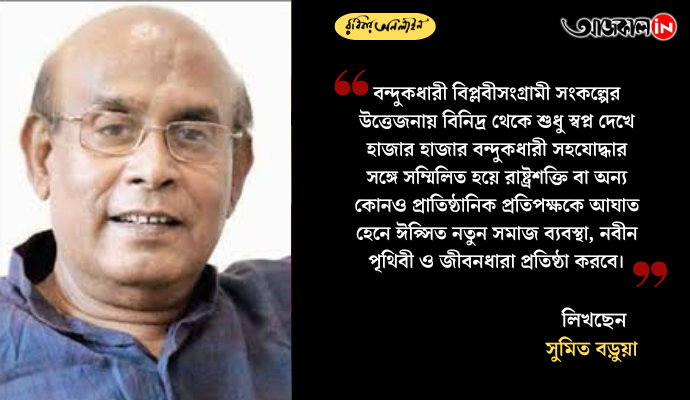
মানুষের বর্তমান সময়ে গাছের মতো মৌনমুখর হয়ে কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে তার ইঙ্গিত ‘গাছ’ কবিতায় রয়েছে। চিরকাল কীভাবে ‘ঠোঁট বন্ধ করে কথা বলতে’ হয়, তা উড়ন্ত পাখির থেকে শেখা যায়। উত্তম পুরুষ কথক ‘বারবার হাজার গানের মাঝখানে গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা, গাছ হয়ে মরে যাওয়ার কথা’ ভাবছেন। গাছ হয়েও সবকিছু ভোলা যায় না, ‘গাছের মান-অপমান, ঘৃণা-প্রেম, মর্মরের মতো কথা বলা না-বলা, সব নিয়েই একটা গাছ অজস্র গাছের ভেতর মিশে থাকে’। গাছ যেমন একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে ‘আরেকটা গাছের শিকড়’ ‘আত্মসাৎ’ করতে চায়, তার মতোই মানুষের যাপনের কথা উঠে এসেছে।৭৩গাছের এই ‘আত্মসাৎ’ করতে চাওয়ার ইচ্ছেটাই অন্যভাবে উঁকি মারে নীল আমস্ট্রং (১৯৯৮) কাব্যগ্রন্থের ‘গাছ’ কবিতায় অন্যভাবে প্রেমের নিঃশর্ত আবেদনে ধরা পড়েছে –
তোমার বুকের কাছে হাত পাতি
পাতা ঝরে পড়ে।
তুমি কি গাছের মতো ডানা মেল
তাঁরা গোনো,
শিশিরে ধোয়াও উরু,
নখর আঙুল?
গাছের গুঁড়ির কাছে হাত পাতি
দুধ ঝরে পড়ে।৭৪
বুকশেল্ফের সার্থকতা তার মধ্যে বই থাকা এবং ব্যবহার করার মধ্যে। বইয়ের ব্যবহারহীন তাক আসলে অজস্র বৃক্ষনাশের ইতিহাস। ‘বুকশেল্ফ’ কবিতায় এই সচেতনতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।৭৫‘কবি’ কবিতায় কবির নিজের মুখোমুখি ও আত্মোপলব্ধির প্রসঙ্গ এসেছে। কবির প্রতিবিম্বটি যখন তাঁকে তাড়িয়ে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বলবে ‘বেঁচে আছো, দ্যাখো সুখী রয়েছো তুমিও পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত ও মৃতদের সঙ্গে’– তখনই কবি হারিয়ে যাওয়া কবিসত্ত্বা ফিরে পাবেন।৭৬‘কালি’ কবিতায় কলমের জন্য কাগজের, কালির জন্য কলমের অপেক্ষা বা কালির অন্যতর অপেক্ষা কথা, গ্রীষ্মকালের প্রতীক্ষায় ছোট্ট টেবিলের ওপর গালে হাত দিয়ে কবির অঘোরে ঘুমিয়ে পড়বার কথা উঠে এসেছে।৭৭‘পেন’ কবিতায় কবির ইচ্ছের প্রকাশ ঘটেছে –
কুচকুচে কালো রক্তের ভেতর ভেসে থাকে কুচো কুচো অজস্র অক্ষর,
তাদের যখন ছুঁচলো ঠোঁট দিয়ে সাজাই
শাদা পাতার ওপর, তাদের
বিশ্বাসঘাতক হতে বলি বারবার।৭৮
‘চামচ’ কবিতায় মেরুদণ্ডহীন, চাটুকার মানুষদের জবানিতে কবি লিখেছেন, যার মধ্যে আত্মসমালোচনাও বাদ যায়নি। আগামী জন্মে ‘চামচ’ হয়ে জন্মাবার ইচ্ছে, ‘লক্ষ লক্ষ হরেক রকম চামচের’ জন্ম দেওয়ার কথা, ‘চামচ-সঙ্গীত’, ‘চামচ-কবি’, ‘চামচ-গদ্যকার’, ‘চামচ-ফিল্ম-ডিরেক্টর’, ‘চামচ-সভ্যতার ওপর ডক্টরেট’– সর্বত্র ‘চামচ’ প্রসঙ্গ কবিতাটির মধ্যে অস্বস্তিকর ক্ষেত্র তৈরি করেছে।৭৯ মানুষের জীবনসংগ্রামের এত তীব্রতা, পারিপার্শ্বিকের প্রবল চাপ অন্তরে অন্তরে আমাদের সকলকেই বার্ধক্যগ্রাস করছে। উদ্যমের অভাব, প্রাণশক্তির অপচয়, প্রত্যাশার ক্ষয়, আকাঙ্ক্ষার বিলোপ, আমাদের অন্তঃসত্ত্বাকে এক ধূসর আচ্ছাদনে ঢেকে ফেলেছে। তাই মানুষের রাতদিন না হতে থাকা মানুষ ছুটে আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেই আঁতকে ওঠে, কুঁকড়ে যায়, কুঁজো হয়ে ভয়ংকরভাবে কাশতে থাকে। ‘যেখানেই যাও’ কবিতায় ক্রমাগত এই না হয়ে ওঠা মানুষের কথা ফুটে উঠেছে।৮০ ‘স্টান্ট’ কবিতায় সকালবেলা খবরের কাগজের ‘এক স্টান্টম্যানের কথা’ থেকে ‘তোমার বাবা’ বা ‘আসলে তুমিও একজন স্টান্টম্যান’ এই বোধ জেগে উঠেছে।৮১ ‘সারাদিন’ কবিতায় সমস্ত দিন ধরেই ‘একটা পচা গন্ধ’-এর অস্বস্তি প্রকট হয়ে উঠেছে। অবাঞ্ছিত গর্ভসঞ্চারের আততি কবিতাটিকে আরও চাপা উত্তেজনা তৈরি করেছে। মানুষের চোখের ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা ‘ভয়’ আর অবাঞ্ছিত লুকিয়ে থাকা ‘গন্ধ’ এই প্রশ্নের মুখোমুখি করে – ‘তবে কোথায় লুকিয়ে আছে গন্ধ?’৮২ মানুষের ভালোবাসা, থাপ্পড় খাওয়া, রুখে দাঁড়ানো, কেঁচো হয়ে যাওয়া, অপেক্ষা করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে যাপন – সবকিছুর মধ্যে দিয়েই এক দুঃসময়ের মধ্যে যাওয়ার বিষণ্ণতা কবির মনকে ছেয়ে ফেলেছে। এই অস্থির পরিস্থিতিতে ‘ভোরবেলা’ কবিতায় ‘তুমি’কে উদ্দেশ্য করে হতাশাব্যঞ্জক ও অভিমানী কণ্ঠস্বর ধরা পড়েছে–
ভোর হওয়ার জন্য যেন অপেক্ষা করতে না হয় তোমাকে,
যেন সমস্ত সময় রাত্রি, শুধু রাত্রি
আঠার মতো এঁটে ধরে রাখে চোখের পাতা,
যেন জেগে উঠতে না হয় কোনওদিন।...
অদ্ভুত হিম গোলকের মতো চোখের কালো মণি
কোনওদিন যেন ছিটকে বেরিয়ে না আসে,
যেন দেখতে না পায়
ভয়ংকর এক বিস্ফোরণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর ভোরবেলা।৮৩
‘নদী’ কবিতায় দেখি সমুদ্র-অভিমুখী নদী, অসীমতা-অভিমুখী প্রাণপ্রবাহের প্রতীক। নদী কেবল সমুদ্রের দিকে ‘শুধু বয়ে যাওয়া’র কথা জানে। মানুষ যতই নিজেকে নদীর মতো স্বভাবের, ‘উদাসীন’ প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন, তার ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। মানুষ নদীর এই প্রাণময় গতিপ্রবাহের কথা ভুলেই থাকে। বেদনার তীব্রতাই মানুষকে নদীর কাছে নিয়ে যায়। উত্তমপুরুষে লেখা এই কবিতায় নদীর কথা ভুলে থাকা প্রেমিকযুগল বা দম্পতির আত্মোপলব্ধিকে তুলে আনা হয়েছে –
একদিন দেখলাম তোমার চোখের গর্ত দিয়ে
বেরিয়ে এসেছে সেই নদী, মাঝখানে সেই ব্রীজ, ফুলে ফেঁপে সেই জল
ছুটে এল আমার চোখের দিকে।
এবার যেদিন কবিতা লিখতে বসব, আর তুমি নক্সা তুলতে বসবে
সাদা কাপড়ের ওপর,
আমরা নদী ফুটিয়ে তুলব তার মধ্যে।৮৪
‘দেখা যায়’ কবিতায় কবি ঘর, ঘরের পর্দার অন্তরালে থাকা ‘একজোড়া চোখ’ যা প্রেমিক বা স্বামীর জন্যে ‘দুশ্চিন্তা’, উদ্বেগ, ভালোবাসায় উৎকণ্ঠ থাকে। প্রেমিকার ‘লাখ বিন্দু জল’-এর ভয়ে, আতঙ্কে প্রেমিকের চোখের জল আসে। পারস্পরিক ‘দেখা’র সংবেদনে চিত্রটি অসামান্য ব্যঞ্জনা লাভ করে –
সান্ত্বনায় এগিয়ে আসে অন্য এক হাত, হাতের আঙুল
মুছিয়ে দিতে জল,
এবং ঢুকে পড়ে আরও বিশাল, গভীর দুই গর্তে।৮৫
কথার পরে কথা
বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তাঁর সময়ের কবিদের অভিপ্রায় সম্পর্কে বলেছিলেন – “সুব্রত, ভাস্কর, শামসের, আমি-আমরা কেউই কিছু হতে চাইনি। খবরের কাগজগুলোর অফিসে তখন ম-ম করছে ডাকসাইটে কবি। লেখকদের দল। আর নীচের আরও ছোট রাস্তা, মেজ রাস্তা। বড় রাস্তায় লাইন দেওয়া ছোট কবি। সেজো কবি। বড় কবিদের ওপারে রূপকথার কলকাতায় কয়েকজন অদ্ভুত কবি দাঁড়িয়ে থেকেছে। যাদের কিছু হওয়ার বাসনা নেই।”৮৬ কফিন কিংবা সুটকেশ(১৯৭২) কাব্যগ্রন্থে সমসাময়িক সাতের দশকের অস্থির বৈপ্লবিক যুগ যন্ত্রণার যে চিত্রকে কবি তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে নকশাল আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সময়ে হিন্দুদের যুদ্ধে যাওয়া নইলে দেশান্তরী হয়ে পলায়নের পরস্পরবিরোধী দিক উঠে এসেছে। সত্তরের উত্তাল দশকের অকুতোভয় যৌবনকেও কবি চিনে নিতে চেয়েছিলেন। কবি সহজ সরল ভাষায় ও ভঙ্গিতে কবিতার প্রতীক বা রূপকের মধ্যে দিয়ে খুব সাধারণ বিষয়গুলির মধ্যেও কল্পনাশক্তির সুচতুর প্রয়োগে গভীরতার অন্য মাত্রা দিয়েছেন। বামপন্থী চিন্তাধারার অধিকারী হলেও বুদ্ধদেব সমাজ বাস্তবতার ব্যাখ্যায় গতানুগতিক মার্কসবাদী পন্থার স্থানে ‘দৈনন্দিনতা’ নিয়ে কাজ করেছেন। প্রবলভাবে মৃত্তিকালগ্ন হয়ে মাটি ও শিকড়ের কথা, বাস্তবতার সমান্তরালে বিকল্প এক বাস্তবতার পরিবেশন করেছেন।৮৭হিমযুগ-এর কবিতাগুলির মধ্যেও কবির এই সংবেদনের বীজ লক্ষ করা যায়।
হিমযুগ-এর অধিকাংশ কবিতাতেই বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত দেখাতে চেয়েছেন সমাজের পচা-গলা শরীরের স্বরূপ, এবং সামাজিক অব্যবস্থা প্রসূত ভয়াবহতা। এই ভয়াবহতার পেছনে যে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক পটভূমি আছে সে-বিষয়ে যথাযথ বিশ্লেষণ করবার মতো ক্ষমতা বা আগ্রহ কোনওটাই তাঁর নেই। এক সার্বজনীন ভয়াবহতা এবং তজ্জনিত অসম্ভাব্যতা-কে (absurdity) বুদ্ধদেব একের পর এক চিত্রকল্পের সাহায্যে উপস্থিত করেছেন এবং যাতে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই।৮৮কবি বুদ্ধদেবের কবিতার গুণগ্রাহী হলেও তাঁর কবিতার প্রবণতা সম্পর্কে কবি মণীন্দ্র গুপ্ত সতর্ক করেছিলেন। ‘পৃষ্ঠপোষক-পাঠকের আদরও যে একজন প্রতিশ্রুত কবির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে’, বুদ্ধদেবের পরবর্তী হাত, পা, মাথা, জিভ, দাঁত, কান, চোখ, আঙুল, নাক বিষয়ক কবিতাগুলিকে তার উদাহরণ হিসাবে তিনি তুলে ধরেছিলেন। ‘চাহিদার ফলে’ ‘ক্রমে অতিপ্রজ’ কবি বুদ্ধদেব তাঁর ‘একদা-আদৃত বাক-প্যাটার্ন ও প্রতীককৌশলের চূড়ান্ত’ করে চলার ফলে তাঁর কাছে ‘বক্তব্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে প্রতীক’–
বক্তব্য রইল সীমিত হয়ে, ক্রমশ তাৎপর্যও হারাল, কিন্তু সংখ্যাতীত হতে থাকল প্রতীক। এবং এই প্রবৃদ্ধির ফলে স্বভাবতই তাঁর কোনও ভাবের কোনও বিশিষ্ট প্রতীক রইল না – তারা তাদের স্থির ব্যঞ্জনা ও নির্দিষ্ট মূর্তিরূপ হারিয়ে হল গলানো কাঁচা-মালের মতো।৮৯
এই সমালোচনাকে স্বীকার করে নিয়েও কবি বুদ্ধদেবের নিজস্ব কাব্যভাষা গড়ে তোলার ইচ্ছাকে অস্বীকার করা যায় না।হিমযুগ-এর কবি বুদ্ধদেব অনেকটা শীর্ষাসন করবার ভঙ্গিতে ‘জীবনকে একটু উল্টো’ দিক থেকে দৃষ্টিপাত করেন’। এই মানসিকতা পূর্ব ইউরোপের ভাস্কো পোপা (১৯২২–১৯৯১), চিলির নিকানর পারা (১৯১৪–২০১৮), এবং আংশিকভাবে বাংলা কবিতায় ষাট দশকের দুজন কবি- দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪২–২০১৬) এবং শামশের আনোয়ারের (১৯৪৪–১৯৯৩) ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বুদ্ধদেব ইতিমধ্যেই একটা নিজস্ব পৃথিবী তৈরি করে ফেলে রূপক এবং প্রতীকের সাহায্যে আমাদের জীবনের অন্তর্নিহিত অসম্ভাব্যতা, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের অরাজকতা, এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রকৃতি অত্যন্ত সফলভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। তাঁর কবিতা পাঠকের চেতনাকে আঘাত ও উদ্দীপ্ত করে।৯০
হিমযুগ-এ কাব্যগ্রন্থে রূপক অবলম্বনে কবি তাঁর অব্যবহিত দেশকালের পটভূমিতে বিধৃত মানুষ-সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থিত করার যে প্রবণতা স্বরচিত কবিতাতেই সূচিত করেছিলেন, সেই ধারা তাঁর অন্যতর রচনারীতিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কফিন কিংবা সুটকেশ-এর মতই হিমযুগ, ছাতাকাহিনী(১৯৮০), রোবটের গান (১৯৮৫), ভোম্বলের আশ্চর্য কাহিনী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯০), উঁকি মারে নীল আর্মস্ট্রং (১৯৯৮), ভূতেরা কোথায় থাকে (২০১৭), বেঁচে থাকা জিন্দাবাদ (২০১৮) ও একলা একা চেয়ার-এ (২০২২) ফ্যান্টাসির বিস্তারে বাস্তবের অন্তঃস্বরূপ চিনে নেওয়ার ও চিনিয়ে দেওয়ার লক্ষণীয় প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে এই ফ্যান্টাসির প্রয়োগ যেন উকি মারে নীল আর্মস্ট্রং কাব্যগ্রন্থে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এই কাব্যগ্রন্থে রূপক একেবারে বর্জিত না হয়ে প্রায়শই বাস্তব পরাবাস্তবে লীন হয়ে গেছে, আর প্রত্যক্ষ বর্ণনা ও বিবৃতি আবেগ, অনুভূতি, কল্পনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের কবিতার রচনারীতিতে কবির পাশাপাশি চলচ্চিত্র-স্রষ্টার মেলবন্ধন ঘটেছে। তাঁর চলচ্চিত্র সৃষ্টির অভিজ্ঞতা, চলচ্চিত্রের প্রয়োগ-কৌশল, দৃশ্যবিন্যাসের ধরণ তাঁর কবিতায় অনেকসময় ভাষা পেয়েছে। কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ‘নিজের জন্য’ কবিতায় নিজেকে যাচাই করে নেওয়ার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন – “তুমি কিছু চেয়েছিলে? কিছু হওয়া কি ঠিক ছিল?”৯১ কবি-বাসনায় অনাসক্ত নয়, অনুরক্ত কবি বুদ্ধদেবের যাত্রার কথাই তার অভিজ্ঞানের স্মারক!
তথ্যসূত্র
১।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (জানুয়ারি ২০১৭)।‘অসহায় আকুলতা’। কথাসমগ্র ১। কলকাতা: পরম্পরা।পৃ. ৭
২।গুপ্ত, মণীন্দ্র (সেপ্টেম্বর ২০১৯)। ‘ষাট-দশকের কবিতা’। দ্রাক্ষাপুঞ্জ, শুঁড়ি ও মাতাল। কলকাতা: অবভাষ। পৃ.৬২-৬৩
৩।বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত (পৌষ ১৪১১)। ‘স্বাধীনতা উত্তর পঞ্চাশ বছরের বাংলা কবিতা : একটি রূপরেখা’। কবিতা নিয়ে। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। পৃ. ১৬৬
৪।দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ডিসেম্বর ২০১৬)। গুপ্ত, মণীন্দ্র। ‘ষাট দশকের কবিতা’। আধুনিক কবিতার ইতিহাস। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং। পৃ. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ডিসেম্বর ২০১৬)। পূর্বোক্ত।পৃ. ১৯০
৫।পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯০
৬।দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ডিসেম্বর ২০১৬)। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। ‘প্রাসঙ্গিক সময়ক্রম’। আধুনিক কবিতার ইতিহাস। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৫৫
৭।পৃ. ১৬৭
৮।দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু (ডিসেম্বর ২০১৯)। চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার (গ্রন্থনা)। ‘হিমযুগ; বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত’।গদ্যসংগ্রহ। কলকাতা: দশমিক। পৃ. ১০০, ১০৪
৯।পূর্বোক্ত। পৃ. ১০০-১০১
১০।সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত, জানুয়ারি ২০০৬)। ঘোষ, অরুণকুমার। ‘চোখের আগুনে ঝলসানো ভাঁড় ও ভাড়াটের মুখ ; বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা’। বাংলা কবিতা: সৃষ্টি ও স্রষ্টা। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: এবং মুশায়েরা। পৃ. ২৫০-২৫১
১১।দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন ও বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত, ডিসেম্বর ২০১৬)। ‘ষাট দশকের কবিতা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯১
১২।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)। ‘পৃথিবী’। হিমযুগ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৪৭
১৩।‘চলো যাই’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০
১৪।‘চলো যাই’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০
১৫।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (জানুয়ারি ২০১৭)।রহস্যময়। কথাসমগ্র ১। কলকাতা: পরম্পরা।পৃ. ৩৯-৪০ ।
১৬।পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৬
১৭।পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৬
১৮।পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৮
১৯।পূর্বোক্ত। পৃ. ৫০-৫১
২০।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (২০১৭)। ভূতেরা কোথায় থাকে। কলকাতা: অভিযান পাবলিশার্স। পৃ. ৪২
২১।পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৩
২২।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)। ‘মানুষ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০
২৩।‘হাসি’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৫
২৪।‘আকাশ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৩
২৫।‘যেখানেই যাও’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৫
২৬।‘হাড়’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৬
২৭।দ্রষ্টব্য: ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (পৌষ ১৪০২)। কড়ি ও কোমল। রবীন্দ্র রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী। পৃ. ১৯৫-১৯৯
২৮।দ্রষ্টব্য: বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক (অক্টোবর ১৯৯৯)। রায়, অলোক প্রমুখ সম্পাদকমণ্ডলী (সম্পাদিত)। রচনাসমগ্র। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পৃ. ৩৩৩-৩৩৮
২৯।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)।‘হাত’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৯
৩০।‘নুলো হাট’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২
৩১।‘মাথা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৬
৩২।‘কান’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৭
৩৩।‘জিভ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৮
৩৪।‘পা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২০
৩৫।‘আঙুল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৯
৩৬।‘নাক’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫২
৩৭।‘চোখ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৬
৩৮।‘দাঁত’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৩
৩৯।সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত, জানুয়ারি ২০০৬)। ঘোষ, অরুণকুমার। ‘চোখের আগুনে ঝলসানো ভাঁড় ও ভাড়াটের মুখ ; বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা’। বাংলা কবিতা: সৃষ্টি ও স্রষ্টা। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: এবং মুশায়েরা। পৃ. ২৫০-২৫১
৪০।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (ডিসেম্বর ২০০৪)।‘একদিন’, ‘এপ্রিল ’৭১’, ‘মৃত আশুকে’, ‘মা’র জন্য চিঠি’, ‘স্বপ্ন, স্বপ্ন’, ‘ভোর হয়েছে, তবু’, ‘যারা’। কফিন কিংবা সুটকেশ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং। পৃ. ২০, ২৪, ২৬, ২৬, ২৭, ২৮
৪১।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)।‘তৈরি হও’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩০
৪২।‘বন্দুকের গল্প’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮
৪৩।‘যখন দাঁড়াই’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১
৪৪।‘ক্রমশ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৩
৪৫।‘হেমন্তকাল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৫
৪৬।দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু (আগস্ট ২০১৯)। চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুমার (গ্রন্থনা)। ‘হিমযুগ : বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত’। গদ্য সংগ্রহ। কলকাতা: দশমিক। পৃ. ১০২
৪৭।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)।‘১৯৭৩’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১১
৪৮।‘সে আছে’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬১
৪৯।আলাউদ্দিন মণ্ডল সম্পাদিত। ‘আলাপচারিতা: পাঁচ: লিরিক: শাহাদুজ্জামান’।আখতাররুজ্জামান ইলিয়াস চূর্ণভাবনা ও চূর্ণকথা সংগ্রহ। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ। পৃ. ৪৫-৪৭
৫০।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)।‘সে আছে’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬১
৫১।‘১৯৭৬’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৪
৫২।‘শাদা পোকা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৯
৫৩।‘ঢুকে পড়ছে’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০
৫৪।‘ইঁদুর’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৫
৫৫।‘বিড়াল’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৪
৫৬।‘টিকটিকি’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৫
৫৭।‘মাগুরমাছ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৩
৫৮।‘গাধা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩২
৫৯।দ্রষ্টব্য: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Encyclopedic Edition. Oxford: Oxford University Press 1992, p. 554, 798;Thomasy, William Rose Benet(Edited, July 1968). The Readers Encyclopedia. New York: Crowell Company.p. 888; Elliott, Julia; Knight, Anne and Cowley, Chris (Edited, 2001). Oxford Dictionary & Thesaurus III. Oxford: Oxford University Press. p. 66.
৬০।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)।‘গাধা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩২
৬১।‘গাধা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩২
৬২।‘কেঁচো’।পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৯
৬৩।দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু (আগস্ট ২০১৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৪
৬৪।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)।‘গোরু’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩১
৬৫।‘ডিম’ পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯
৬৬।‘খচ্চর’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৮
৬৭।‘বাঘ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৪
৬৮।‘সাঁড়াশি’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৪
৬৯।‘প্রেসার-কুকার’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৬
৭০।‘হ্যাঙ্গার’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৭
৭১।‘উড়ো-জাহাজ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৬
৭২।‘শেষ মিনি’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৩
৭৩।‘মেশিন’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৩
৭৪।‘পাহাড়’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬০
৭৫।‘গাছ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫৯
৭৬।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (ডিসেম্বর ২০০৪)।‘গাছ’।উঁকি মারে নীল আমস্ট্রং। পূর্বোক্ত।পৃ. ১২৭
৭৭।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭)।‘বুকশেল্ফ’।পূর্বোক্ত। পৃ.৫০
৭৮।‘কবি’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪২
৭৯।‘কালি’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০
৮০।‘পেন’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪১
৮১।‘চামচ’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৫১
৮২।‘যেখানেই যাও’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৫
৮৩।‘স্টান্ট’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৩৮
৮৪।‘সারাদিন’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২২
৮৫।‘নদী’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৪
৮৬।‘ভোরবেলা’। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮
৮৭।‘দেখা যায়’। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬২
৮৮।উদ্ধৃত অংশটির জন্যে দ্রষ্টব্য: সরকার, অলোক। দাস, দীপ্তি (সম্পাদিত, জানুয়ারি ২০২৩)। সাহা, গৌতম। ‘কিছু না-হতে চাওয়ার সাধনা : বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতা’। তাবিক : ‘বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত : বহুমুখী স্বপ্নের ভুবন’।কলকাতা।পৃ. ৮১
৮৯।সরকার, অলোক। দাস, দীপ্তি (সম্পাদিত, জানুয়ারি ২০২৩)। চক্রবর্তী, সুরেলা। ‘বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত : একটি জার্নি’। পূর্বোক্ত।পৃ. ১১৭
৯০।দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু (আগস্ট ২০১৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০১
৯১।গুপ্ত, মণীন্দ্র (সেপ্টেম্বর ২০১৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৬৮
৯২।দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু (আগস্ট ২০১৯)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১০৪
৯৩।দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব (ডিসেম্বর ২০০৪)।‘নিজের জন্য’। কফিন কিংবা সুটকেশ।পূর্বোক্ত।পৃ. ২৫