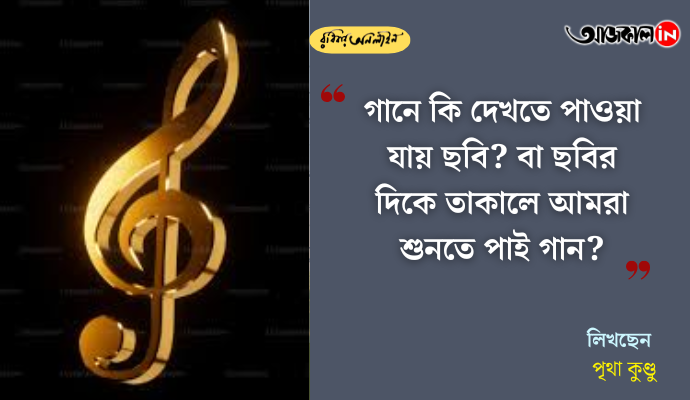গানে কি দেখতে পাওয়া যায় ছবি? বা ছবির দিকে তাকালে আমরা শুনতে পাই গান? রবীন্দ্রভুবন যেন আমাদের দেখার চোখ আর শোনার কানকে অন্য চেতনা দিয়েছে--
রবীন্দ্রনাথের গানে রঙের অনুষঙ্গ এসেছে কখনও চিত্রকল্পের প্রয়োগে, কখনও বা ধ্বনিঝঙ্কারের উপমায়। তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের আলোচনায় জানা গেছে, তাঁর দৃষ্টিতে একটি বিশেষত্ব ছিল—তিনি সব রঙ পরিষ্কার দেখতে পেতেন না, বিশেষ করে লাল রঙ। কেতকী কুশারী ডাইসন এবং সুশোভন অধিকারী তাঁদের গবেষণামূলক ‘রঙের রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিছু রঙের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত ছিল। বাংলার নিসর্গচিত্রে সাধারণভাবে লাল ও সবুজের ব্যবহার বেশি হয়। এই দুটি রঙের ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ রাঙা ও শ্যামল শব্দদুটি ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। স্নিগ্ধ, শীতল, শান্তিদায়ী বিস্তৃত ছায়ার প্রকাশে ‘শ্যামল’, ‘শ্যাম’ এবং ‘নীল’ রঙের ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর গানে—‘নীল আকাশ শ্যাম ধরা’, ‘শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল’, ‘শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে’, ‘নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়’ ইত্যাদি। তাঁর নিজের আঁকা নিসর্গচিত্রেও এই দুটি রঙের প্রয়োগ চোখে পড়ে।
কালো আর লালের প্রাচুর্য তাঁর ছবিতে দেখা গেলেও, লাল রঙ সরাসরি তিনি ব্যবহার করেন না। গাঢ় মেরুন, কমলা-মিশ্রিত লাল বা মেটে, গৈরিক রঙের বিভিন্ন ‘শেড’ তিনি ব্যবহার করেছেন। লাল সম্পর্কে তাঁর অস্বস্তি সম্ভবত এক অপূর্ণতার, না-পাওয়ার বেদনাবোধ সৃষ্টি করেছিল। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বলা চলে, এক ধরনের বিপ্রতীপ আকর্ষণের ক্ষেত্র থেকেই বোধহয় এমন বহুমুখী ভাবনার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের গানে লালের বহুরকম বিন্যাস। কখনো তীব্র, কখনো হালকা। কখনও বা ছন্দের সুতোয় গাঁথা, যেমন-- ‘ঝরে পড়ে আছে কাঁটাতরুতলে রক্তকুসুমপুঞ্জ’(৩/৩/৩/৩), অথবা ‘আমি রাখব গেঁথে তারে, রক্তমণির হারে’(২/২)-- এখানে কানের মধ্যে দিয়ে মর্মে এসে প্রবেশ করে রক্তিমতার ধারণা। রবীন্দ্রনাথের সৃজন-কল্পনায় লালের ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক, কখনও বা পরস্পরবিরোধী।
বেশিরভাগ শিল্প সমালোচকের মতে, রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে ইয়োরোপের ‘এক্সপ্রেশনিজম’-এর সাদৃশ্য আছে। পরিতোষ সেন, যোগেন চৌধুরী প্রমুখের মতে, রবীন্দ্র-চিত্রকলায় ‘এক্সপ্রেশনিজম’-এর প্রভাব থাকলেও তা পুরোপুরি ইয়োরোপের শিল্পীদের অনুসরণ নয়, তা স্বতন্ত্র। আবার অনেকে তাঁর ছবিতে ‘ইম্প্রেশনিজম’(প্রতিচ্ছায়াবাদ)-এর উপাদানও লক্ষ্য করেছেন। বিশেষ করে তাঁর নিসর্গচিত্রে আলোছায়ায় ব্যবহার পুরোপুরি রেখাবিহীন না হলেও, কিছুটা প্রতিচ্ছায়াধর্মী তো অবশ্যই। আর রবীন্দ্রচিত্রকলায় ‘ছায়া’র ধারণাটিকে অনুভব করতে গেলে ফিরে যেতে হয় তাঁর গানের কাছেই। ‘যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলাম পণ’— প্রেম পর্যায়ের ‘গান’ উপপর্যায়ের অন্তর্গত এই গানটিতে কবির ছায়াবাদী প্রবণতার এক বিশেষ আবেদন ফুটে উঠেছে— ‘এই শরতের ছায়ানটে/মোর রাগিণীর মিলন ঘটে/সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কন।’ এ গানে পাই রূপের ছায়া, ধ্বনির ঝঙ্কার, সুরের আবর্তন। নির্দিষ্ট আকার, রেখা বা রূপের কাঠিন্য এখানে মুখ্য নয়, তার পরিবর্তে কল্পনার ছায়া, ভাবের ছায়াই এখানে শিল্পী বা শিল্পরসিকের মননে রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। এটিই প্রতিচ্ছায়াবাদের নান্দনিক তত্ত্বের মূল কথা।
শৈলীর দিক থেকে তাঁর নিসর্গচিত্র পুরোপুরি প্রতিচ্ছায়াবাদী না হলেও ভাবের দিক থেকে অনেকটাই মেলে। তাই নির্দিষ্ট নাম-পরিচয় ছাড়াই, অনেক আগে লেখা এক-একটি গানের ভাবের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় পরবর্তীকালে আঁকা কোন না কোন ছবিতে। কবি-শিল্পীর অবচেতনে ছবি আঁকার সময় গুঞ্জরিত হয়ে কি ওঠে না তাঁরই কোন গানের পংক্তি? এই মিল খোঁজার বিষয়টি অনেকাংশেই সঙ্গীতপ্রেমী এবং শিল্পরসিকদের নিজস্ব অনুভবের বিষয়, এবং এই নান্দনিক অনুভবের স্বাধীনতা প্রতিচ্ছায়াবাদীরা স্বীকার করেন, রবীন্দ্রনাথও অস্বীকার করেন নি। সেই অনুভবের নিরিখেই ভাবা যায় ‘আমি চঞ্চল হে’ গানটির চিত্র-সহযোগে পাঠ। ১৯০২ সালে রচিত একটি কবিতার গীতরূপ হিসেবে বিচিত্র পর্যায়ের এই গানটি আমরা পাই, ১৯১৭ সালে ‘ডাকঘর’-এর প্রথম অভিনয়ের সময়, যদিও ডাকঘরের মুদ্রিত সংস্করণে শেষ অবধি কোন গান রাখা হয় নি। গানের সঞ্চারী অংশে ‘রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়/ তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়/ কী মুরতি তব নীল আকাশে/ নয়নে উঠে গো আভাসি’— যেন এক নিসর্গচিত্রের ভাবকেই ফুটিয়ে তোলে। সুর ভৈরবী-আশ্রিত, কিন্তু সঞ্চারী অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্যভাবনায় অপরাহ্ণের আভাস। ‘ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর’-এর সুরে অসীম, অনন্তের ব্যঞ্জনা। এবার কবির পরিণত বয়সে আঁকা দুটি নামহীন ছবির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। গানের বাণীর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায় ছবি দুটিতে রঙ্গের প্রয়োগ। একটিতে পড়ন্ত বেলার সোনালি রোদ আর ছায়ার খেলা, অন্যটিতে দূর থেকে ভেসে আসা অসীমের হাতছানি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে নীল আকাশের প্রান্তে ফুটে ওঠা ঊষার আলোর রক্তিম আভায়। ‘সুদূর’রূপী অনন্তের প্রতিচ্ছায়াই গানে আর ছবিতে রসোত্তীর্ণ হয়েছে-- কখনও বাণী আর সুরের মেলবন্ধনে, কখনও বা রেখা আর রঙের যুগলবন্দিতে।
রবীন্দ্রনাথের গানে প্রতিচ্ছায়াবাদের আরও উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়-- প্রায়ই বর্ষার অনুষঙ্গে। ‘কদম্বেরই কানন ঘেরি’ বা ‘কাঁপিছে দেহলতা থরথর’ গানে মেঘের ছায়াকে পাই। কিন্তু শুধু বর্ষার মেঘচ্ছায়ার দৃশ্যবর্ণনাতেই আটকে থাকে না রবীন্দ্রনাথের ছায়াবাদ। তাই মাঝে মাঝেই ছায়া থাকলেও ছায়ার উৎসকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ধরা যাক, ১৯২২ সালে রচিত ‘ওই যে ঝড়ের মেঘের কোলে’ গানটির কথা। ছায়া এখানে বর্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও বর্ষার অধীন নয়। স্থায়ী আর অন্তরা অংশে পাই ঝড়ের মেঘের যে উদ্দাম রূপ, সঞ্চারীতে তা স্তিমিত হয়ে আসে-- প্রকৃতির ঝঞ্ঝামুখর কলরবের ভিতরে বসেই নিবিষ্ট কবি অথবা শিল্পী দেখতে থাকেন ‘ছায়াময় দূর’-কে। ঠিক পরের বছর লেখা গান ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে’। প্রথম বাক্যের পর ছায়ার আর উল্লেখ নেই; এমনকী আষাঢ়দিনের মেঘগর্জনের উল্লেখ থাকলেও গানে সরাসরি বৃষ্টিপাতের বিবরণ নেই। আছে এক ফুলের কথা—যার নাম কেয়া বা কেতকী। কাঁটার বৃন্তে ঢাকা এ ফুলের অন্তর্নিহিত মাধুরী। রবীন্দ্রনাথের গানে আষাঢ়ের কেয়া যেন এক অভিসারিকা নারী, ‘আপনায় লুকায়ে’ সে আসে কার অভিসারে? এই আত্মগোপন, অন্তরালচারিতার ছলনাই একাত্ম হয়ে গেছে ছায়ার অপ্রকটতার সঙ্গে। অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা রবীন্দ্রনাথের গানে এই প্রকৃতি অথবা নারীর ছায়ারূপেরই এক অভিব্যক্তি। হেমন্তলক্ষ্মীকে তিনি দেখেন হিম-কুয়াশার ধূমল রঙে আঁকা ঘোমটার আড়ালে এক নারী রূপে, যে ‘আপন দানের আড়ালেতে’ গোপন করে রাখে নিজেকেই। বারে বারে তাঁর কবিতায়, গানে যে রহস্যময়ী মানসী প্রতিমার দেখা মেলে, যার উদ্দেশে তিনি গাইতে পারেন, ‘তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি/ কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী’, যে কখনও ‘মানসসুন্দরী’, কখনও ‘লীলাসঙ্গিনী’, কখনও বা ‘বিচিত্রা’— সেই ছায়াময়ীকেই কি তিনি ধরতে চাননি তাঁর আঁকা নারীমুখের ছবিতে?
অনেক শিল্প সমালোচকের মতে, সাহিত্য আর গানের বিপ্রতীপে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নিজের চিত্ররচনার আদর্শ। পদ্ধতিগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই বিপরীতমুখী সৃষ্টি প্রবণতাকে স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ কবিতার ক্ষেত্রে আগে আসে ভাবনা, তারপর তা রূপ নেয় ভাষায়, কবিতাকে সঙ্গীতরূপ দিলে সেই ভাব ও ভাষার সমষ্টি সুরে বাঁধা পড়ে। আর ছবির ক্ষেত্রে আগে আসে খেলার ছলে এলোমেলো রেখা বা রঙের যথেচ্ছ বিহার, পরে সেই খেলার মধ্য থেকে কোন এক ভাবনা বা রূপের আদল ফুটে ওঠে। তাঁর ছবি বিদেশে স্বীকৃতি পেলেও নিজের দেশে সমাদর পায় নি, তাই হয়তো অভিমানের সুরেই কবি বলেছিলেন—দেশের জন্য রইল তাঁর গান, আর ছবিগুলি তিনি রেখে আসতে চান বিদেশের শিল্পরসিকদের জন্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে— ছবি আর গানের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। বরং একটু অন্যভাবে ভাবলে দেখা যায়, সুরের অনির্বচনীয়তায় জীবন ও শিল্পের বাইরেও ‘অন্য কিছু’র যে সন্ধান করেছেন তিনি, ছবিতেও সেই ‘অন্য কিছু’কেই খুঁজতে চেয়েছেন। তাঁর ছবিতে বেদনা, সংশয়, বিপন্নতা, রহস্য সবই ব্যক্ত হতে চায় রেখায়, রঙের বিচিত্র প্রকাশে, আর গানে তাঁর হৃদয় শিল্পী ও শ্রোতার হৃদয়কে সম্পৃক্ত করতে চায় আভাসে, ইঙ্গিতে। তুলি-কালিতে, রঙে যে ছবি তিনি এঁকেছেন, তা কবির আপন মনস্তত্ত্বের আপাত-দুর্বোধ্য প্রকাশ, আর গানের ভাষায় যে ছবি এঁকেছেন, তা তাঁর নান্দনিক স্বরূপকে সহৃদয় শিল্পী ও সঙ্গীতরসিকের কাছে মাধুর্যে, রমণীয়তায় পৌঁছে দিতে চায় সঙ্গোপনে। রবীন্দ্রনাথের ছবি ও গান, রঙ ও সুরের লীলা তাই পরস্পরবিরোধী বা বিপরীত নয়, তারা পরস্পরের পরিপূরক।