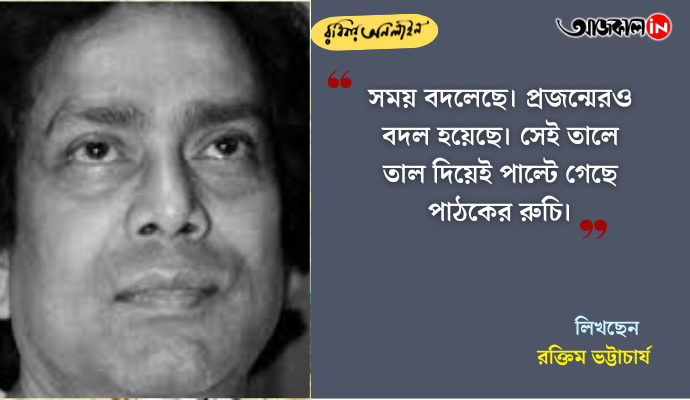সমরেশ বসুর প্রয়াণের পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। সময় বদলেছে। প্রজন্মেরও বদল হয়েছে। সেই তালে তাল দিয়েই পাল্টে গেছে পাঠকের রুচি। এই প্রজন্ম কীভাবে পড়ছে সমরেশ, তারই অনুসন্ধান-
সমরেশ বসুর জন্মশতবর্ষের এই পুণ্যলগ্নের অন্তিম প্রবাহে আমার মতো এক অজ্ঞ, নবীন পাঠ-প্রচেষ্টকের কাছ থেকে প্রণত নৈবেদ্য পাঠককুল গ্রহণ করবেন কি না জানি না, তবে এই ধৃষ্টতা সমরেশের গভীর চোখে বকুনিমিশ্রিত প্রশ্রয়েই ক্ষমার্হ হয়ে উঠবে, নিশ্চিত।
বলতে দ্বিধা নেই, সমরেশ বসু সম্পর্কে জানার বা পড়ার ইচ্ছা যে কোনওদিন ভীষণভাবে মাথাচাড়া দিয়েছিল, তা ঠিক নয়। কারণ, আমার এখনও পর্যন্ত সীমিত ও অগভীর সাহিত্যপাঠের ক্রমতালিকায় তাঁর নাম অনেকটা পরের দিকেই এসেছিল, তাও এক আত্মীয়ের অনুপ্রেরণায়। ততদিনে আমি বুঁদ হয়ে আছি বিভূতিভূষণে (বন্দ্যোপাধ্যায়), শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসে, মানিকের কথাসাহিত্যে। ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকজনও তখনও উপেক্ষিতও। আসলে, পাঠ্যবইতে তখন যে-সকল সাহিত্যিকের লেখা পেতাম, তাঁকেই খানিক পড়ে ফেলার লোভ জন্মাত। সমরেশ সেই বাজারে খানিক পিছিয়েই ছিলেন, ফলত, তাঁর জগতে প্রবেশের জাদুকাঠিটি অন্বেষণ করতে পারিনি তখনও।
এমনই এক শীতের সকালে একটি গোয়েন্দা গল্পের সংকলনে প্রথম পড়া ‘টেলিফোনে আড়ি পাতার বিপদ’ এবং পরিচয় খুদে গোয়েন্দা গোগোলের সঙ্গে। ছোটদের বোধগম্য সহজ লেখা, গল্পের জটিলতাও মারাত্মক কিছু নয়। কিন্তু কৈশোর মনে-মননে-চিন্তনে বাস্তবিক সমস্যাকে থ্রিলের মোড়কে পরিবেশন করে খানিক ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি, এবং সহজ-স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক সন্দর্ভে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছনো – আমাদের ফেলুদা-ব্যোমকেশের জগতে এক নতুন ঝলক। তরুণ পাণ্ডব গোয়েন্দার অ্যাডভেঞ্চার গল্পে ভ্রমণের প্রাধান্য দেখেছি ততদিনে , সে হয়ত ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রামণিক সুরম্য চেতনার খানিক উচ্ছ্বসিত বহিঃপ্রকাশও। কিন্তু, গোগোল একেবারেই পাশের বাড়ির ছেলেটি। বাঙালির দ্বিতীয় বাড়ি পুরীতে গিয়েও (‘সোনালি পাড়ের রহস্য’) সে না চাইতেও জড়িয়ে পড়ে রহস্যের গভীরে, রীতিমতো শাসনের শিকারও হয় বাড়িতে। তাকে উদ্ধার করতে দরকার পড়ে পুলিশ, বা সিনিয়র গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর। সে আচম্বিতে কোনও হারকিউলিয়ান কাজ-কারবার করে ফেলে না, বা অতর্কিতে তার কোনও জাদু-ক্ষমতাও প্রদর্শিত হয় না। বাড়ির শাসনে, পুলিশ-গোয়েন্দার আতিথেয়তায় তার কৃষ্টি ভরে ওঠে সৌজন্যের সতর্কতায়।
সে-ই আমার প্রথম সমরেশ। আমার কাছে তিনি শুধুই শিশু-সাহিত্যিক। তাঁর ছদ্মনাম যে কালকূট, সেও পঞ্চম শ্রেণীর সাধারণ জ্ঞানের বইয়ের দান। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে নেওয়া সেই গোগোল-পাঠের পর যে আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ছিল সমরেশের বড়দের জন্য লেখা উপন্যাস বা গল্পে মনোনিবেশ করা। স্বভাবতই, সে অযাচিত উপদেশ খুব একটা পছন্দ হয়নি। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে নেওয়া সেই গোগোল-পাঠের পর যে আত্মীয়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ছিল সমরেশের বড়দের জন্য লেখা উপন্যাস বা গল্পে মনোনিবেশ করা। স্বভাবতই, সে অযাচিত উপদেশ খুব একটা পছন্দ হয়নি। বাড়ির তাকে মুখ গুঁজে লুকিয়ে থাকা ‘প্রজাপতি’ বা ‘বিবর’ তারুণ্যের সহজাত আকর্ষণের খোরাক হিসেবেও টানেনি একেবারেই।
তখনই এক দৈবযোগে, প্রায় কলেজ-জীবনের পরে, হঠাৎ করেই এক বান্ধবীর খাতিরে একদিন পড়ে ফেললাম সমরেশের একটি গল্প। নাম, ‘আদাব’। সে একটি জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যমে কোনও একটি শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে গল্পটি পড়িয়েছিল। বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলাম (গল্পটিতে)। আর ঠিক তারপরেই, সেই আত্মীয়ের কথা মনে করে, শুরু হল সমরেশের সাহিত্য-জীবনে অনুপ্রবেশের কষ্টার্জিত প্রচেষ্টা।
যে-কোনও সাহিত্যিককে পড়া শুরু করতে আমার ব্যক্তিগত মত, তাঁর লিখিত-প্রকাশিত ক্রম অনুসারেই পড়তে চেষ্টা করা, তাতে তাঁর বিবর্তনের ধারাটিও বুঝতে খানিক সুবিধা হয়। এই ভেবেই, হাতে নিলাম গল্পের বই, ‘মরশুমের একদিন’, আর উপন্যাস হিসেবে ‘নয়নপুরের মাটি’, উত্তরঙ্গ’। সে-ই আমার শুরুর সমরেশ, যে-যাত্রা এখনও অক্ষুণ্ণ।
‘নয়নপুরের মাটি’ সমরেশ বসুর প্রথম লিখিত উপন্যাস, প্রকাশক্রমের তারিখানুযায়ী দ্বিতীয়। ‘উত্তরঙ্গ’ ঠিক তার উল্টো। এবং, উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে জানতে পারি, এই লেখার পরিকল্পনা সমরেশ করেছিলেন ‘আদাব’ রচনারও আগে। ইছাপুর রাইফ্যাল ফ্যাক্টরির অফিসে বসে এই উপন্যাস যখন তিনি লিখছেন, তাঁর বয়স তখন একুশ। উপন্যাসের ভূমিকায় নব্য লেখক নিজে কী ভাবছেন, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক। “’নয়নপুরের মাটি’তে একটা লাইন আছে, ‘আহা! বাঁধা বীণার তারে বেসুর কী গভীর!’ সেই সুর বাঁধারই প্রথম উন্মাদনা ‘নয়নপুরের মাটি’, আমার লেখা প্রথম উপন্যাস।
আমার লেখা ‘উত্তরঙ্গ’-এর বহুপূর্বে (১৯৪৬ সালে) এ বই আমি লিখেছি। অর্থাৎ সাহিত্য আসরের দরজার চৌকাঠটা তখন আমি দূর থেকে উঁকি মেরে দেখছিলাম। এখন দরজার কাছে (বোধ হয় চৌকাঠটা পেরিয়ে?) এসেছি। ইচ্ছেটা আস্তে আস্তে আসরের মাঝখানে গিয়ে বসি।
সুর বাঁধতে গিয়ে হয়তো পেরিয়ে গেছে কোথাও তালের চৌহদ্দি, দিকপাশ না ভেবে সে আপনার মনে এগিয়ে গেছে। একে যদি বেসুরো বলা যায়, তবে বলি, জীবনের সুর-তালভঙ্গের বেদনাই না বারবার মানুষকে নতুন করে সুর বাঁধতে শিখিয়েছে।“
শুধু এইটুকু ভূমিকার অংশ থেকেই একটা কথা স্পষ্ট, নিজের প্রথম উপন্যাস-রচনার যে মাদকতা, তা তাকে স্পর্শ করেছিল বেশ উচ্চকিত মাত্রাতেই। তিনি নিজেই নিজের রচিত লাইনে উচ্ছ্বাসিত হচ্ছেন, নিজের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয়েও তিনি তা অস্বীকার করছেন না, বরং, সেই-সব ভুলগুলিকে নিজের একান্ত সস্নেহ মমতায় পরম-যত্নে লালিত করছেন। তিনি আবেগের শেষতম বিন্দুতে উন্নীত হয়ে আগলাতে চাইছেন নিজের খোদাই করা অক্ষর-আত্মজদের, যা তাঁকে পরবর্তী পথের এক অন্যতম সম্রাট করে তুলেছিল অচিরেই।
“উত্তরঙ্গ” প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, এবং দ্বিতীয় লেখা- সে-কথা সর্বজনবিদিত, পূর্ব-উল্লিখিতও। এই লেখা আরেকটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এই লেখার মাধ্যমেই (সম্ভবত) সমরেশ লেখাকেই তাঁর পেশাগত বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে তখন তাঁর চাকরি বিগত। ফলত, এই বইয়ের বিক্রি নিয়ে তিনি নিজেও খুব উল্লসিত ছিলেন, উৎকণ্ঠাতেও ভুগছিলেন। উপন্যাস প্রকাশের দিনের ঘটনা, বই বিক্রয়ের খবর সমরেশ নিজেই লিখে রেখেছেন তাঁর আত্মকথায়। প্রেসিডেন্সি জেলে কারাবাসকালীন এই লেখার বীজ তিনি অনুবাদ করেন মননে, এবং প্রোথিত করেন কল্পের গল্প-খাতায়। ভূমিকায় সমরেশ বলছেন, “যে উপাখ্যান আমি রচনা করেছি, তা উপাখ্যান হলেও ইতিবৃত্তও বটে।…জগদ্দলনগরের কথার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই তার বিস্তারের জটিলতার, এ উপন্যাসও তেমনি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও স্বয়ং সমাপ্ত নয়। এ শুধু তার ভূমিকা মাত্র।“
চাকরিজীবনে চটকল শহরের গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই উপন্যাসের যে ভাবনা সমরেশের মনে এসেছিল, তাকে নিজের সাহিত্যজীবনের ডেমোগ্রাফির এক সূচনা বলেছেন উপন্যাসিক স্বয়ং। এবং, এই ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হবার কোনও অবকাশ নেই যে, সমরেশ তাঁর জীবনের একটি বিরাট পর্ব জুড়ে শুধুমাত্র এই হুগলী জেলা, গঙ্গা নদীর পাড়, চটকল, শ্রমিক-জীবনকে আত্মস্থ করেছেন তাঁর গদ্যভাষার দৃপ্ত গরিমায়, যেখানে আজন্মলালিত হয়েছে তাঁর তরুণ দীপ্তি, ঐতিহ্য এবং অভিজ্ঞতার পুনর্বাসন। তৃতীয় উপন্যাস ‘বি টি রোডের ধারে’তে জগদ্দলের শ্রমিকাঞ্চল এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, চতুর্থ উপন্যাস ‘শ্রীমতী কাফে’তে তারই প্রতিবেশী শহর নৈহাটির একটি নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক পটপ্রবাহ, পরবর্তীতে ‘ছিন্নবাধা’ বা ইপোনিমাস ‘জগদ্দল’ – সবক্ষেত্রেই সমরেশ তাঁর নিজের ছাপ রেখে গেছেন। জীবনের কাছে আদ্যন্ত সৎ সমরেশ এই ব্যাপারে কোনও মফঃস্বলের চেনা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভোগেননি, বরং, দূরদৃষ্টিতে তাঁর অন্তর্বর্তী যাপনকে মেপে নিয়েছেন অতি-বাস্তবিক দুরুহ গাম্ভীর্যে।
সমরেশ লেখক হিসেবে যেমন, আমার মতো নবীন পাঠকের হিসেবে তেমনই। অর্থাৎ, তাঁর নিজেকে নিয়ে শুরুর দিকের আপাত-দার্ঢ্যে যেমন কোনও খাদ নেই, আমিও যে-কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি, এখনও সমরেশকে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে না পারা নিয়ে আফশোসও নেই। কেন আগে বেশি পড়িনি- এ কখনোই আমাকে তাড়িত করেনি। বরং, সময় নিয়ে ধীর সন্তরণেই বিশ্বাস। সমুদ্রমন্থনের ঘনায়মান গভীরে অমৃতপ্রাপ্তির প্রাক্কালে যেমন ‘কালকূট’ উঠে আসে, তাকে ধারণ করেই নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠেন দেবাদিদেব – সেও কালকূটের সময়-চিন্তিত অনুসন্ধানেই পরাপাঠের তাত্ত্বিক লয়েই খুঁজে পাওয়া যাবে সমরেশের অমরত্বের খনি – এ নিয়েও কোনও দ্বিধার অবকাশ, অন্তত এই অজ্ঞ পাঠকের কাছে, একেবারেই নেই।