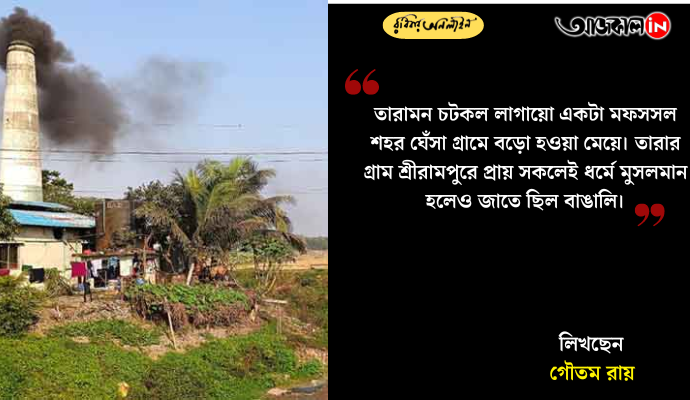
নৈহাটি-ভাটপাড়া লাগোয়া গ্রাম থেকে চটকলে কাজ করতে এসে মাঝে মাঝেই আশেপাশের গ্রামের লোকেদের কেমন একটা ঘোর লাগত প্রথম প্রথম। তখনও লালমুখো সাহেবদের বড় প্রতাপ ছিল চটকলের ভিতরে। ভবাগাছি, দোগাছি থেকে পেটের তাগিদে চটকলে লেবারের কাজ করতে আসা মানুষগুলো প্রথম প্রথম বুঝতেই পারতো না সামনে সাহেব বা মেম সাহেবেরা পড়ে গেলে কী করতে হয়।
সাহেব মানেই মালিক। মালিকের জাত মানেই সাহেবের জাত-গাঁ-গঞ্জে তখন তেমনটাই ভাবত লোকজনেরা। তাই জমির মালিকের মতই একটু ঠাকুর-দেবতা জ্ঞানে যে মিলে, কারখানায় সাহেবসুবোদের দেখতে হবে, সেটা কলে কাজের জন্যে প্রথম যারা গ্রাম থেকে বুঝিয়ে শুনিয়ে লোকেদের ধরে আনত, তারা বলেছিল। তাদের কথা মাথায় রেখেই গাঁয়ের লোক যখন আশেপাশের পাটের কলে কাজে যেতে শুরু করল, তখন প্রথম প্রথম দেশি সাহেব আর বিদেশি সাহেব -এটা কেমন গোলমাল হয়ে যেত গাঁয়ের মানুষজনদের।
মেমসাহেবে তো আরও গোলমাল। গাঁয়ের লোকজনেরা জীবনে ক’দিন খাঁটি মেম দেখেছে, সে হাতে গুণে বলা যেত সেকালে। ছেলে-মেয়েদের বয়সের হিসেব রাখতে মেমেদের গাঁ দেখতে আসার দিন দিয়ে বলবার রেওয়াজ ছিল তখন। যেমন ছিল ঝড় দিয়ে। এমনকি টাইটনিক জাহাজ ডুবির সময় দিয়েও অনেক বুড়িরা সেসময়ে নিজেদের বয়সের হিসেব-নিকেশ করতে চেষ্টা করতেন। যেমন নবীনের ঠাকুমা বলত; সেই যে গ্যো যেইবারে সেই কোন্ সমুন্দুরে বরোফে নেগে একখান পেল্লাই জাহাজ ডুবি গেচিলো না, সেকালের শীতের তো আমার জম্ম। মায়ে তো তাইই কয়ে গেছে জীবনভোর।
এমনসব সেকেলে নারীদের জবানী শুনলে ঘটি-বাঙালের ফারাক করা যেত না। নবীনের ঠাকুমা জীবনে পদ্মা পেরোয়নি, তবু পদ্মাপারের একটা টান কী করে যে তার কথা বলবার অভ্যাসের মধ্যে চলে এসেছিল, কে জানে!
আসলে ঘটি-বাঙালের ভিতরেও তখন গরীব-বড়লোকের মধ্যে ছিল এক দারুণ মিল। গরীব বাঙালের মুখের ভাষা, কথার ভঙ্গি আর গরীব-চাষাভুষো বাড়ির ঘটির লব্জ একটু হলেও কাছাকাছিই ছিল। যেমন ছিল বড়লোক ঘটি আর বড়লোক বাঙালের লব্জ।
লব্জ ঘিরে তখন হাসি মস্করার অন্তছিল না। সেই মস্করার ভিয়ানে নতুন করে যেন চিনির ড্যালা পড়ল গাঁয়ের লোকেদের কেউ চটকলে চাকরি নেওয়ার পরে। পাটকলে কত জায়গাকার মানুষজন গিজগিজ করছে। কত রকমের ভাষা। পাটকলে যে মেয়েরাও কাজ করে, কলি কামিনের কাজে মেয়েরাও এখন দেহাত থেকে আসে, এসব কথা গাঁয়ের মজলিস থেকে শুনে যখন পুরুষেরা বাড়ি ফিরে বৌদের বলে, মেয়েমহলে তৈরি হয় একটা বড় রকমের কৌতুহল। মেয়েরা আবার ঘরকন্নের কাজ ছেড়ে, বিদেশ বিঁভুইতে এসে কলের কাজে কী করে নাগে গো? -আদুরে গলায় বৌ জানতে চায় সোয়ামীর কাছে।
সোয়ামীর তখন বৌয়ের এত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মত শরীরের তাগদ নেই। কলে সারাদিনের খাটনি তাকে বিছানায় পড়া মাত্রই ঘুমের রাজ্যে টেনে নিয়ে যায়। বৌয়ের কথার জবাব দেবে কী-- স্বামীর নাসিকা গর্জনে তখন বিরক্তির একশেষ একরত্তি বৌয়ের। একবার দু’বার বরের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা যে করেনি বৌ, তা নয়। কিন্তু সে চেষ্টা বিফলে গেছে। তখন আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে কখন যে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের রাজ্যে নেতিয়ে গেছে বৌ, তা সে নিজেই জানে না।
এমনটাই তখন আশেপাশের গাঁগুলো প্রায় রোজ ঘটতে থাকল। মেয়েমহলে সকালে বর্তিবিল থেকে বেরিয়ে আসা বোগাইয়ের ধারে নিত্যকর্ম করতে গিয়ে এমন সব গল্পে ভোরের বাতাস ভ'রে উঠতে লাগলো। কিষাণী বৌ যত রাতে সোয়ামীর সোহাগের কথা বলে, ততই মুখ ভারি হতে শুরু করে চটকলের কুলিবৌয়ের। আশেপাশে নানাজনের নানা কথায় তার মনের মধ্যেও উঠতে থাকে নানা ধ্বন্দ। তৈরি হতে থাকে সংশয়। কখনও মনে হয়, তার কি গতরে পোকা পড়েছে, যে রাতের বেলায় বেশিরভাগ দিনই সোয়ামীর নজর তার দিকে প্রায় পড়েই না।
এই যে বিচানায় পড়া কি মরার মত ঘুমোনো, একটু কতা নয় কো। সোহাগ নয় গো। আরও কিছুর তো ধারই না ধরা -এসব কীসের লক্ষণ? পাটকলের সাহেবসুবোর ভূতে কি তার সোয়ামীর মতিগতি বদলে যেতে শুরু করল? সোয়ামীকে কি ভর করেছে ভিন দেশি ডাকিনী-যোগিনী? এই ভাবনা যেন কিষাণবৌয়ের ফুসমন্তরে কেমন একটা চাগাড় দিয়ে ওঠে চটকলের কুলিবৌয়ের মাথায়? বৌগাই নদীর জলের স্রোতে ভেসে আসা কচুরিপানা গায়ের উপর উঠে এলেও সেদিকে নজর পড়ে না কুলিবৌয়ের। দু’হাত দিয়ে কচুরিপানা সরানো আর কচুরিপানার মধ্যে সেই পটলপানা একটা মোটা সবুজ অংশ, সেটাকে কে আগে পট পট করে ফাটাতে পারে, তা নিয়ে আর দশজন পাড়া ঘরের বৌদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা -সেসবও কেমন যেন একটু করে ফিকে হয়ে উঠতে শুরু করে। তিরতিরে জলে আর সাঁতার কাটার উৎসাহ পায় না অনেকেই।
চটকলে কাজ করতে যাওয়া মরদদের বৌয়েদের এই অদলবদল চোখ এড়ায় না আর দু’দশজন বৌ, ঝিয়েদের। প্রথম তারা ব্যপারটা দেখে। লক্ষ্য করতে থাকে। এই দেখা আর লক্ষ্য করবার ভিতরেই কেটে যায় অনেককটা দিন। সেই দিনগুলোর মধ্যেই আবার হয়ে ওঠা কুলিকামিনদের মধ্যে কখনও কখনও জেগে ওঠে সেই আগের মত উছলে পড়া জীবন-যৌবনের আবেগ। সেই আবেগ তখন আছড়ে পড়ে বোগাইয়ের জলেও। ঝাপানের উদ্দামতায় বুঝতে পারা যায় জীবন-যৌবনের পাখা মেলা বাতাসের কৌতুকভরা কাকুতি।
বোগাই নদী, বোগাইয়ের মত আরও কত নাম জানা বা নাম না জানা অজস্র নদী, পন্ডিতেরা যাদের কে হয়তো কখনও নদী বলে স্বীকৃতিই দেবে না- সেইসব সচল জলের স্রোত -তারা তো এমনি করেই বয়ে নিয়ে চলে আশেপাশের মানুষের জীবনের প্রতিদিনকার চলমান জীবনের স্রোতের দিয়াকে। হাওয়ায় কখনও কাঁপে সেই দিয়ার শিখাটি। আবার কখনও বা অঞ্চল থেকে সে জানান দেয় জীবনের অনিঃশেষ বেঁচে থাকাটাকে। সেই অচঞ্চল শিখাটাকে দেখে কোনও এক অচেনা-অজানা গাঁয়ের পল্লীবালা নিজের জীবন-যৌবনের স্বর্গরাজ্যের কল্পিত কামনায় নিজের চঞ্চল মনকে একটা অচঞ্চল, স্থির, স্ফটিক স্বচ্ছ জলের মত করে তুলতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা যে তার কেবল আজকের সকল থেকে শুরু হয়েছে, তা তো নয়। যবে থেকে সে বোগাইয়ের মত তিরতিরে জলে বা নন্দীপুকুরের জলে ঝাপানের অধাকার পেয়েছে নিজের বয়সের দৌলতে, কিংবা ভিন-গাঁ থেকে এ গাঁয়ে বৌ হয়ে এসে, বিয়ের জল ঝরিয়ে ঘর-গেরস্তালি সামলাতে স্রোতের উজানে জীবন তরী বাইবার অধিকার অর্জন করেছে- ঠিক যেন সেই দিনটা তাকে এই স্রোতের দিয়ার কালনির্ণয়ের অধিকার অর্পণ করেছে।
এগিয়ে যাওয়া জীবনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকেই তো মানুষের স্বভাব প্রবণতা। কে আর চাইবে এগোনো জীবনকে পিছন পানে টানতে। আর টানতে চাইলেই জীবন নামক ব্যক্তিটি কেন তার নিজের স্বাভাবিক ধর্মকে জলে ভাসিয়ে আবার পিছন পানে নিজেকে টেনে আনতে দেবে সময়কে?
গাঁয়ের মানুষ যেমন প্রথম পাটকলে গিয়ে গাঁয়ের সহবতের সঙ্গেই নতুন করে পাঠ নিতে শুরু করেছিলো পাটকলের সহবতের, কারন; এই পাঠ না নিলে যে সে নতুন চাকরির আদব-কায়দার সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে মিশ খাওয়াতে পারবে না। আর নিজেকে যদি সে চটকলিয়া এবাদতের সঙ্গে মিশ খাওয়াতে নাই পারে, তবে কেমন করে টিকিয়ে রাখতে পারবে তার নতুন চাকরি? জমি যে আর তার নিজের নেই। জমি চাষ দিয়ে যে আর বছর তো দূরে থাক, মাসের খোড়াকিই সে ঘরে জোটাতে পারে না।
(চলবে)