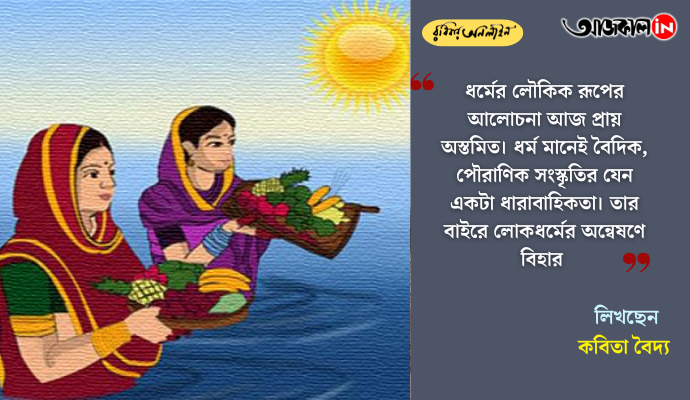
ধর্মের লৌকিক রূপের আলোচনা আজ প্রায় অস্তমিত। ধর্ম মানেই বৈদিক, পৌরাণিক সংস্কৃতির যেন একটা ধারাবাহিকতা। তার বাইরে লোকধর্মের অন্বেষণে বিহার আর ঝাড়খণ্ডে ক্ষেত্রসমীক্ষা-
লোকায়ত আঙ্গিক আমাদের দেশের আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশে কতখানি মরমী একটা ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, সেটা গ্রামীণ ভারতকে না দেখলে বোধহয় সবটা বুঝে ওঠা যায় না। প্রত্যেকটি রাজ্যের আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে লৌকিক ধর্ম, আচার-আচরণ এবং গৌণ ধর্ম একটা বড় রকমের জায়গা করে রেখেছে। বহু রাজ্য আমাদের দেশে আছে, যেখানে বৈদিক দেব-দেবতা অপেক্ষা, লৌকিক দেব-দেবতারা অনেক বেশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন।
সাধারণ মানুষের যাপনচিত্র, তাঁদের খাদ্যাভ্যাস, তাঁদের নানা ধরনের লোকাচার, আচার-আচরণ -যার সঙ্গে ব্রত-পার্বণ ইত্যাদির একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। সেই সমস্ত আঙ্গিকের সঙ্গে কীভাবে লোকায়তধারা সংস্থিত হয়েছে সেটা গ্রামীণ ভারতকে না দেখলে খুব একটা বুঝতে পারা যায় না। আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গে থেকে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষদের ধর্মীয় উৎসবগুলি দেখবার সুযোগ পেয়ে থাকি, সেই সুযোগের মধ্যেও এই পারস্পরিক সহাবস্থান সম্প্রীতি এবং নানা ধরনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশ মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যায়।
বিহারের ছটপুজোকে কেন্দ্র করে পাটনা শহরের যে আড়ম্বর, যে বৈভবের প্রতিযোগিতা -যেমনটা অনেকটা আমাদের কলকাতা শহরের দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা দেখি, তা কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না গ্রামীণ বিহারে বা এককালে বিহারের অংশ হিসেবে থাকা আজকের পৃথক রাজ্য ঝাড়খন্ডে। ঝাড়খণ্ডের বড় শহর রাঁচি বা জামসেদপুর, যে অঞ্চলগুলিতে অর্থনীতির বুনিয়াদটা অনেক বেশি সবল, সেখানে কিন্তু সাবেক বিহার, আজকের ঝাড়খন্ডের হিন্দিভাষী মানুষজন ছটপুজোকে কেন্দ্র করে যেভাবে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, তার মধ্যে দিয়ে যেমন আঞ্চলিক সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে ঠিক তেমনভাবেই এই শহরগুলিতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে রুটি-রুজির টানে যে সমস্ত মানুষেরা অবস্থান করেন, চাকরি করেন, সেই সমস্ত মানুষদের সঙ্গে একটা সাংস্কৃতিক একাত্মতা তৈরি হয়। সেটাও কিন্তু এই ধরনের লোকায়ত ধর্মপালনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রিক যে কোনও ধারা প্রবাহের ভিতরে সব সময় একটা সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং ভালোবাসার ছবি ফুটে ওঠে।
ঝাড়খণ্ডের বড় বড় শহরগুলোতে এ দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে আমাদের চোখে পড়ে। যেমন ধরা যাক, জামশেদপুর টাটা স্টিল বা তার অনুসারী শিল্পগুলির দৌলতে এখানে এক অসাধারণ মিনি ভারতবর্ষকে আমরা দেখতে পাই। সেই মিনি ভারতবর্ষের মধ্যে কিন্তু ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী জনজাতি জীবনের ছবিটাও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়। ঝাড়খণ্ডে যাঁরা সামাজিকভাবে একটা ভালো অবস্থানে রয়েছেন, সেই সমস্ত মানুষরা কিন্তু সেখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যে সমস্ত ধর্মীয় আচার-আচরণ, সেগুলি পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের সুযোগ করে দেওয়ায় যথেষ্ট রকম যত্নশীল থাকেন। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা দর্শক হিসেবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সে সমস্ত উৎসবে অংশ নেন। একটা অদ্ভুত সম্প্রীতির বাতাবরণ সেটা জাতি, ধর্ম,ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে সেখানে তৈরি হয়। ভারতের এই চিরন্তন সম্প্রীতির ভাবনাটা যেভাবে বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের নানা জায়গায় নানাভাবে প্রতিফলিত হয়,সেটা কিন্তু ভারতের জাতীয় সংহতির একটি বড় রকমের ইতিবাচক, ইঙ্গিতময় ধারা।
প্রতিটি গৌণ ধর্মে 'জল' একটা বিশেষ আঙ্গিকের বার্তা দেয়। লৌকিক ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে জলকে কেন্দ্র করে যে ধরনের আচার-বিচার, বিশেষ করে স্ত্রী-আচার আবর্তিত হয়, তার মধ্যে সব সময় কিন্তু লুকিয়ে থাকে জনজীবনে নানা সমস্যাকেন্দ্রিক ধারা উপধারা। সেই ধারায় প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠে আসে, পানীয় জলের বিষয়। জল হল জীবনধারণের একটি এক এবং অনবদ্য অধ্যায়। এই অধ্যায়কে জীবন সংগ্রামের প্রতিটি আঙ্গিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবার তাগিদ থেকে লোকধর্মের নানাদিকের প্রকাশের প্রাসঙ্গিকতায়, এই জলকে একটা প্রধান উপজীব্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়।
বৈদিক সংস্কৃতিকেন্দ্রিক ধর্মীয় আচারগুলির মধ্যে জলের একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব আছে। ঠিক তেমনি ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির লোকধর্মের প্রকাশের মধ্যেওজলের একটা বৈশিষ্ট্য ভূমিকা আছে। সেই জলের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনও নদী, কখনও পুকুর, কখনও দিঘি, আবার নদী-পুকুর-দিঘি কোনও কিছু না থাকলে, খানিকটা গর্ত তৈরি করে, তাতে জল ঢেলে, তাকে খানিকটা পুকুরের, দিঘির আদল কল্পনার মধ্যে নিয়ে এসে, সেই কল্পনার সমুদ্রে ভেসে, লোকধর্ম পালনের নানা আঙ্গিককে উপস্থাপিত করতে আমরা দেখি বিহারে।
ছট, তিইজ, জুহিতিয়া, গোধন ইত্যদি লোকধর্মকেন্দ্রিক ক্রিয়াচার সর্বস্ব গৌণ ধর্ম পালনের মধ্যেও এই জলের একটা বিশেষ রকমের ভূমিকা রয়েছে। ছট সূর্যই হন বা কোনও লোকায়ত দেবী হোন যা নিয়ে বিহার বা আজকে ঝাড়খণ্ডের হিন্দিভাষী মানুষদের মধ্যে কিছুটা অঞ্চল ভিত্তিক বিতর্কও আছে। তবে সেই দেবীর অর্চনার ক্ষেত্রে জলের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।
যেখানে গঙ্গা প্রবাহমান সেখানে মানুষ গঙ্গানদীতে গিয়ে দেবীর কাছে গিয়ে, এই ছট পুজোকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সামগ্রী নিবেদন করে। তার সঙ্গে সূর্যের একটা সম্পর্ক আঞ্চলিকভাবে এক এক জেলায় একেক রকম ভাবে থাকে। কিন্তু যেখানে জল নেই, সেখানে বড় পুকুর দিঘিতে গিয়ে অর্চনা করা হয়। যেখানে পুকুর বা বড় দিঘি নেই, সেখানে কিন্তু গর্ত খুঁড়ে জল ঢেলে, তার মধ্যে ধরনের লৌকিক আচার-আচরণ পালন করা হয়। সেই আচার-আচরণের মধ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রধান এবং নানা ধরনের আয়োজন করা হয়।
বিহারের লৌকিক জনজীবনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য সেখানে সাধারণ সামাজিক জীবনের মধ্যে জাত-পাতের যত বেড়াই থাকুক না কেন, যত বিভাজনই থাকুক না কেন, বাংলার মতো ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে লোকধর্ম পালনের ক্ষেত্রে। গোটা ব্যাপারটাই পরিচালিত হয় মহিলা সমাজের দ্বারা। তাদের জাতিগত পরিচয় যাই থাকুক না কেন, তাঁরা তাঁদের মত করে এই ধরনের লৌকিক দেবতার অর্চনা করে থাকেন।
একটা সময় বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ছট পুজোকে কেন্দ্র করে ঘরে তৈরি করা নানা ধরনের খাদ্য সামগ্রী, তার ব্যবহার ছিল বহুল। এক্ষেত্রে ঠেকুয়া নামক এক ধরনের ঘরে তৈরি আটা, দুধ, গুড়, নারকেল, কিসমিস, মেওয়া ঘি ইত্যাদি সম্বলিত খাবারের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। খাদ্যবস্তুটি এমনভাবে তৈরি করা হতো যার সঙ্গে আজকের নাগরিক সভ্যতার আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত বেকিং ব্যাপারটার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। কোনওরকম আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়াই, এমনকি বহু ক্ষেত্রে কয়লার উনুনের ব্যবহার ছাড়া ঘুটের জ্বালের মধ্যে দিয়ে এই ঠেকুয়া তৈরি করাটা ছিল অনেকটা যেভাবে উত্তরপ্রদেশের কিছু অঞ্চলে তন্দুর সামগ্রী প্রস্তুত করা হতো, রুটি বিভিন্ন ধরনের মাংসের উপাদান প্রস্তুত করা হতো ঠিক তেমন পদ্ধতিতেই।
বাংলায় যাকে বলা হয় স্যাঁকা, সেই রেওয়াজের মধ্যে দিয়ে এটা ঠেকুয়া প্রস্তুত করা হতো এবং এই প্রস্তুত প্রণালীর মধ্যে এমন একটা বিজ্ঞান কাজ করত যাতে কোনওরকম রেফ্রিজারেশনের উপায় অবলম্বন না করেই পাঁচ-সাত দিন যথেষ্ট গরমের মধ্যেও এই ঠেকুয়াটিকে সংরক্ষিত করতে পারা যেত। প্রচুর পরিমাণ ঘি, বিশেষ করে মোষের দুধের ঘি, বিহারের গ্রামাঞ্চলে যাকে বলা হয়, ভৈঁইসা ঘি,তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই যে ঠেকুয়া প্রস্তুত করা হতো, তাতে কিন্তু নারকোল ইত্যাদি সহজে নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও এগুলি কিন্তু সহজে নষ্ট হতো না।
দীর্ঘদিন এগুলিকে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত করতে পারে পারে যেত। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়েছে, বিহার বা আজকের ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে যে অভিজ্ঞতাটি বর্তমান নিবন্ধকারের হয়েছে সেটি হল বিহারে কিন্তু গরুর দুধের ঘি, যেটাকে আমরা বাঙালিরা গাওয়া ঘি বলে থাকি, সেই গাওয়া ঘিয়ের প্রচলন যথেষ্ট কম। সেখানে কিন্তু মোষের দুধের ঘি, যেটার বর্ণটা সাদাটে হয়, সেই ঘিয়ের ব্যবহার অনেক বেশি। আর মোষের দুধের ঘি বা ভৈঁসা ঘি নামে যেটি দেহাতি অঞ্চলে পরিচিত, সেটির স্বাদের মধ্যেও কিন্তু গাওয়া ঘিয়ের থেকে অনেকখানি তারতম্য রয়েছে।