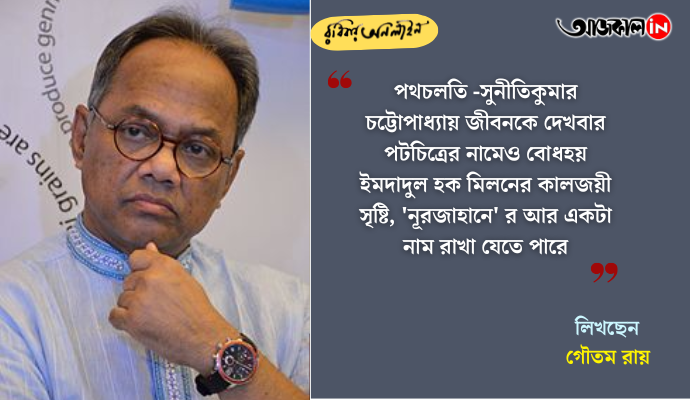
পথচলতি -সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জীবনকে দেখবার পটচিত্রের নামেও বোধহয় ইমদাদুল হক মিলনের কালজয়ী সৃষ্টি, 'নূরজাহানে' র আর একটা নাম রাখা যেতে পারে-
দবিরগাছি যখন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে বেশ একটু তার মত পরিপাটি হয়ে তামাক খাচ্ছে, তখন নূরজাহান বাড়িতে নেই। নূরজাহান গেছে রাস্তা তৈরি দেখতে। ঢাকা থেকে বিক্রমপুরের দিকে একটা খুব বড় রাস্তা তৈরি হচ্ছে। মাওয়া হয়ে সেই রাস্তা চলে যাবে খুলনায়। মাওয়ার পরেই রয়েছে বাংলার গর্ব, বাঙালির গর্ব পদ্মা নদী।
ইমদাদুল হক মিলন এই পদ্মা নদীর আগে বিশেষণ ব্যবহার করছেন, 'রাজকীয় নদী পদ্মা।' এ বিশেষণের মধ্যে দিয়েই বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি, পদ্মার দিগন্ত বিস্তৃত আকুল আহ্বানে দেশকালের সীমাকে অতিক্রম করে, প্রতিটি বাঙালি, বুকের মধ্যে অনুভব করে একটা শিহরণ। গঙ্গা-পদ্মা এই দুটি নামই বাঙালির হৃদয়ে কেমন যেন একটা মোচড় দেওয়া আনন্দ, অভিমান, দুঃখ, বেদনা, হতাশা –সব কিছুর একটা সম্মিলিত মিশ্রণের ধারা প্রবাহ তৈরি করে।
আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মানুষ, তাঁদের কাছে যেমন গঙ্গা নদী ঘিরে একটা আবেগ আছে আবার ঠিক তেমনিই ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, যাঁদের হয়ত কখনও কোনও শিকড় ছিল না ওপার বাংলায়, তাঁদের মধ্যেও একটা শিহরণ জাগে এই পদ্মা নদীর নাম ঘিরে। পদ্মা নদী মানে কিন্তু কেবলমাত্র ইলিশ মাছ নয়। পদ্মা নদী মানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশের একটা অধ্যায়। যেমন ভাবে গঙ্গা নদী মানেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশের একটা অধ্যায়। যে অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান রয়েছে বাংলা ও বাঙালি অন্তরে। রাজনৈতিকভাবে দেশ বিভক্ত হয়ে গেলেও বাঙালির অন্তর লোকের যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, অভিমান, যন্ত্রণা -সব কিছুর সঙ্গেই মিলেমিশে রয়েছে এই পদ্মা নদী।
তাই লেখক যখন এই পদ্মা নদীর আগে 'রাজকীয় নদী' শব্দটা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করছেন, সেই বিশেষণের মধ্যে দিয়ে যেন আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে, সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের প্রেক্ষিতগুলি। নদী কেন্দ্রিক সভ্যতা আমাদের ভারতীয় সভ্যতা। সেই নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার পরস্পর ধারাবাহিকতায় এককালে নামকরণ হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতার। সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু নদের ধারাবাহিকতার প্রবাহমানতার ছিল একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।
আর নদী কীভাবে সভ্যতার উত্থান পতনের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার একটা পর্যায়তে আজকের প্রজন্মের মানুষকে উত্তোরিত করেছে, সেটা লেখক এই উপন্যাসের প্রায় সূচনা পর্বে, পদ্মা নদীর উল্লেখের আগেই নতুন একটি সড়ক নির্মাণের কথা উল্লেখ করছেন। এই সড়ক নিছক একটা রাস্তা নয়। নিছক একটা যোগাযোগের মাধ্যম নয়। এই সড়ক ধীরে যে কাহিনীর ঘূর্ণাবর্ত 'নূরজাহান' উপন্যাসে লেখক উপস্থাপিত করেছেন, তার মধ্যে থেকে আমরা দেখতে পাই, সময়ের সঙ্গে সেতুবন্ধনের একটা ভাবক্ষেত্র হিসেবে এই সড়ক বিষয়টি কিন্তু উঠে আসছে।
সাধারণভাবে আমাদের উপন্যাসটি পড়তে গেলে মনে হবে একটা কাহিনীর পারস্পরিক সংযোগ হিসেবেই সড়ক, এটির উল্লেখ লেখক ইমদাদুল হক মিলন করছেন। এবং পরবর্তীকালে এই সড়ককে ঘিরে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরজাহানের জীবনের নানান ওঠাপড়া, তার সঙ্গেও হয়তো আমরা একটা চরিত্রগত সাজুজ্য অনুভব করব এই সড়ককে ঘিরে। কিন্তু উপন্যাসটির যে বিস্তৃত পটভূমি, যার মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকের নয়, কেবলমাত্র বাঙালি জনজীবনের অত্যন্ত অপাক্তেয় স্তরে থাকা এক তুচ্ছ নারী নূরজাহান তার জীবন কেন্দ্রিক কাহিনী বিন্যাস নয়। এই সড়ক যেন মানুষের সঙ্গে মানুষের, সময়ের সঙ্গে সময়ের, নারীর সঙ্গে নারীর এবং নারী-পুরুষেরও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার একটা সোপান।
নূরজাহান উপন্যাসে কাহিনীর পারস্পর্য যে নানা চাপান উতরের মধ্যে দিয়ে বিন্যাস পর্বে, মানুষের হিংস্রতা, ধর্মের বিকৃত ব্যবহার -এই সমস্ত কিছু দেখতে পেলেও কিন্তু উপন্যাসের শুরুতে এই সড়ক নির্মাণের বিষয়টির উল্লেখ যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়; পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা যেসব চলতি হওয়ার পন্থী -ঠিক এই কথাটারই অনুরণন লেখক ইমদাদুল হক মিলন 'সড়ক' শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ঘটাচ্ছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর বা তারওপর যখন পরিবর্তিত বিশ্বের একজন পাঠক এই উপন্যাসটি পড়বেন তখনও তাঁর কাছে এই সড়ক শব্দটির দ্যোতনা, সময়ের নিরিখে একটা নতুন রকমের বার্তা বয়ে আনবে।
কাহিনীর ধারাবাহিকতা নির্মাণের ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের একটা রূপকল্প সৃষ্টির আভাস, সেটি কিন্তু যে কোনও কালজয়ী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়। এইভাবেই একটি কালজয়ী সাহিত্য, তার নিজস্ব আঙ্গিক বিকাশ করবার ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করে। ঠিক সেভাবেই ইমদাদুল হক মিলন তাঁর এই নূরজাহান উপন্যাসে রাজকীয় নদী পদ্মার উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই নির্মীয়মাণ এক মহাসড়কের কথা বলছেন। সেই সড়কটি ঢাকা খুলনা মহাসড়ক।
বাংলাদেশের প্রচলিত ধারায় বিভিন্ন এলাকার নাম ভিত্তিক রাস্তার নামকরণের একটা রীতি আছে। যেমন ধরা যাক, বরিশাল শহরে জীবনানন্দ দাশ, যে বাড়িতে থাকতেন তার সংলগ্ন রাস্তাটির নাম বগুড়া রোড। আবার একেবারে ঢাকা মহানগরীতে ইতিহাসের বহু ঘটনাক্রমের সাক্ষী হিসেবে যে ইন্টারকন্টিনাল হোটেল আছে, একটা সময় যার নাম শেরাটন হয়েছিল। আবার সেটির নাম বদল হয়ে ইন্টার কন্টিনাল হয়েছে। এখন আবার সেই শেরাটার নামেই ফিরে এসেছে।
সেই পাঁচতারা হোটেলটি যে রাস্তার উপরে অবস্থিত সেই রাস্তাটির নাম ময়মনসিংহ রোড। এই যে অঞ্চলভিত্তিক রাস্তার নামকরণ সেই বৈশিষ্ট্যের দিকটি উপন্যাসের সূচনা পর্বে লেখক এভাবে তুলে আনছেন যে সড়কের মাঝখানে স্বমহিমায় জেগে থাকা রাজকীয় নদী পদ্মা, তবুও সেই সড়কের নাম হবে ঢাকা খুলনা মহাসড়ক। দেশের এই প্রচলিত ধারাকে মর্যাদা দেওয়া, সম্মান দেওয়ার ভেতর দিয়ে লেখক বুঝিয়ে দিচ্ছেন, চিরন্তন বাঙালি জীবনের রীতিনীতি, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সমন্বয়ী চেতনা -সমস্ত কিছুর একটা মেলবন্ধনের ভাবনা নিয়েই তিনি কাগজে কালির আঁচর উৎকীর্ণ করতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।
লেখকের এই সমর্পণের মধ্যে কোনও লোক দেখানো আড়ম্বর নেই। নেই এতোটুকু নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবার চেষ্টা। নিজের সময়কে মেলে ধরবার ক্ষেত্রে একটা স্বরূপ, একটা পথ, কীভাবে আগামী সময়ের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে পারে -আর সেই সম্পর্কের ভিত্তি কীভাবে মানুষের জীবনের নানা স্তরকে জীবিকার নানা স্তরকে, সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়কে, সভ্যতার একটা ধারা উপধারাকে পরিস্ফুট করতে পারে -সেটি যেন এই রাজকীয় নদী পদ্মা আর ঢাকা খুলনা মহাসড়ক, যাকে তিনি উল্লেখ করছেন; 'একটা কারবার হচ্ছে দেশগ্রামে' বলে। এই যে উক্তি এই সমান্তরাল দুটি ধারার মধ্যে দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেই যেন চার্লস ডিকেন্সের টেল অফ টু সিটিজের মতো একাধারে সুসময় আর একাধারে দুঃসময়ের এক পরস্পর সমান্তরাল সহাবস্থানকে।
এই সহাবস্থানের ভেতর দিয়েই কিন্তু কেবলমাত্র বাঙালি নয়, গোটা মানব সমাজ চিরদিন বেঁচে থেকেছে। তাই নূরজাহান উপন্যাসের সূচনা পর্বের এই দুটি ব্যঞ্জনা আমাদের উপন্যাসটির গভীরে প্রবেশের আগেই এই প্রত্যয়ে উপনীত করে যে, মানুষের বেঁচে থাকার কাহিনী বলে দেওয়াই কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য। সেই বেঁচে থাকার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর হাতছানি আছে। এমনকি আক্ষরিক অর্থে মৃত্যুও আছে। কিন্তু জীবন আর মৃত্যু দুটির পাশাপাশি সহাবস্থান, তার মধ্যে দিয়েই তো মানুষের জীবনধারা প্রবাহিত হয়। তার মধ্যে দিয়েই তো জগত সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম কানুনগুলো প্রসারিত হয়। সেই প্রসারণ আর সেই সংকোচনের মধ্যে দিয়েই লেখকের ভাষায়, 'কত নতুন নতুন চেহারা যে দেখা যাচ্ছে।'
লেখকের এই প্রসারিত দেখার চোখের মধ্যে দিয়েই উপন্যাসটির ব্যপ্তি, আমাদের দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে, চিন্তা চেতনার দুনিয়ার প্রসারনের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ একটা মাইলফলক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করছে। আসলে বাঙালির দেখার চোখের প্রসারণ, এই বিষয়টিও কিন্তু ইমদাদুল হক মিলনের আলোচ্য উপন্যাস নৃরজাহানের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। কেবল একটি দেশের, একটি সময়কালের যন্ত্রণায় উপাখ্যান নয়। একটি নারীর একক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু ও উপন্যাসের একমাত্র বিষয় নয়। ধর্মান্ধতা-মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই এই উপন্যাসের কথা শেষ হয়ে যায় না।
এই উপন্যাস যেন সেই নচিকেতার গানের মত; 'অন্তবিহীন পথ চলায় জীবন।‘ সেই জীবনের সন্ধান আমাদের কাছে বারবার দেয়।
চলবে..