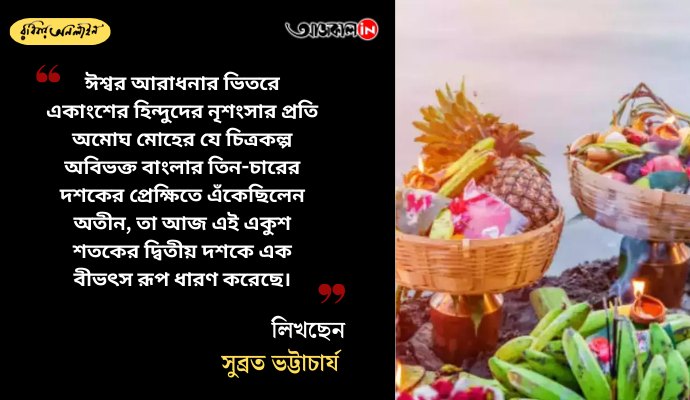
ঈশ্বর আরাধনার ভিতরে একাংশের হিন্দুদের নৃশংসার প্রতি অমোঘ মোহের যে চিত্রকল্প অবিভক্ত বাংলার তিন-চারের দশকের প্রেক্ষিতে এঁকেছিলেন অতীন, তা আজ এই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এক বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। সেদিন ঈশ্বর আরাধনার নামে পশুবলি দিয়ে একাংশের হিন্দু পৈশাচিক আনন্দে ধর্মীয় মৌতাত অনুভব করত। আর আজ পশুকে (তথাকথিত গোমাতা) রক্ষা করবার নাম করে নরহত্যা করে বিভৎসতায় মাতে রাজনৈতিক হিন্দুরা। মানুষের মাথা নিয়ে গেন্ডুয়া খেলার যে পৈশানিক শব্দবন্ধনীর সঙ্গে আমাদের কেবল বইয়ের পাতাতেই পরিচয়, সেই পরিচয়কে এখন ধর্মের রাজনৈতিক কারবারীরা বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে।
অতীনের রচিত চিত্রকল্পে এই বাস্তবতাই আমরা দেখছি, সে যুগে ঈশ্বর আরাধনার নামে নির্বিচারে প্রাণী হত্যার মতো নৃশংসতা নিয়ে একাংশের হিন্দুদের ভিতরে কোনও অপরাধবোধ ছিল না। আজও সেই একই মানসিকতায় একাংশের হিন্দু, যারা রাজনৈতিক গতিপ্রবাহকেই তাদের 'হিন্দু' পরিচয়ের সবথেকে বড়ো মাধ্যম মনে করে, তাদের ভিতরেও তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মরক্ষার তাগিদে নরহত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ নিয়ে এতোটুকু অপরাধবোধ নেই। অতীনের বৈশিষ্ট্য এখানেই এই ধর্মোন্মাদনাতেই তিনি থেমে থাকেন। ধর্মের নামে মাতলামোর পাশাপাশি আবহমানকালের সম্প্রীতির বাংলাকে তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। ছোঁয়াছুঁয়ির একটা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল, অতীন দেখিয়েছেন; সেই প্রতিবন্ধকতার আবহের ভিতরে থেকেও হিন্দু-মুসলমান কিন্তু একে অপরের শোকে-দুঃখে-আনন্দে-বিষাদে পাশাপাশি থেকেছে। ভৌমিক বাড়ির সব থেকে কাছের মানুষ ছিলেন ঈশম শেখ। এই ভৌমিক বাড়ি বা ঈশম শেখ কিন্তু কেবলমাত্র অতীনের 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' একটি চরিত্র নয়। এঁরাই তখন ছিলেন গোটা বাংলা জুড়ে। এঁরাই ছিলেন গত শতকের দুই-তিন-চারের দশকের বাংলার কঠিন-কঠোর বাস্তব চরিত্র। ঠাকুরবাড়ির গিন্নিমারা যেমন একপেট খিদে নিয়ে আসা জোটনকে মাছ-ভাত খাইয়ে মনের আনন্দ পেতেন, তেমন জোটনও তখন ছিল গোটা বাংলা জুড়ে আর ভৌমিকবাড়ির গিন্নীমারাও ছিলেন বাংলার আনাচকানাচ জুড়ে। মুড়াপাড়ার জমিদারেরা যে মন্দিরের সঙ্গে মসজিদের জন্যেও জমি দিচ্ছেন –এ দৃশ্য অবিভক্ত বাংলায় একটি স্বাভাবিক ছবি ছিল জসিমের হাতে গোটা একটা হাতি তুলে দিয়েছিলেন মুড়াপাড়ার জমিদারেরা। এই বাংলা আর রইল না -এটাই ছিল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের সবথেকে বড়ো আক্ষেপ।