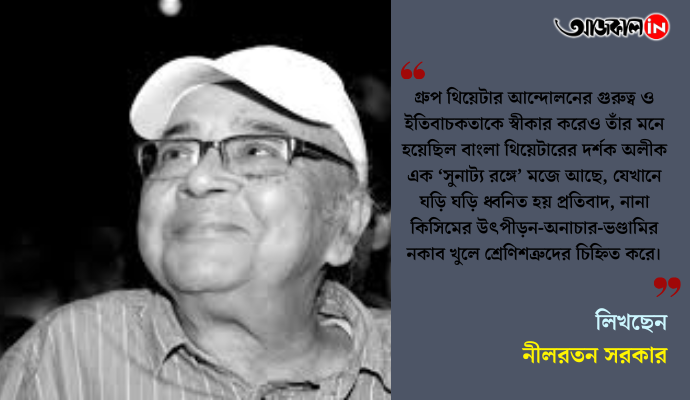
সমাজসচেতনতার এক সুসংবদ্ধ পথের পথিক মনোজ মিত্র। রাজনৈতিক বোধে পরিপূর্ণ একজন কালজয়ী স্রষ্ঠা। কিন্তু সেই বোধকে কখনও দলীয় আবর্তে আবদ্ধ না করা একজন শিল্পী-
মনোজ মিত্রর নাটকের এক চরিত্র বলেছিলন, ‘বাংলা থিয়েটার … মৌলিক নাটক… অরিজিনাল প্লে বছরে দেড়খানাও পয়দা হয় না!’ আম বাঙালিও একথাটা খানিক মানে। ব্যাপক অর্থে এইকথায় কিছুটা সত্য থাকলেও থাকতে পারে। বছরভর বাংলায় যে-পরিমাণ নাটকের মঞ্চায়ন হয় তার অনেকটাই বাংলা কথাসাহিত্যের নাট্যরূপ অথবা বিদেশি কোনও নাটকের ছায়ায় রচিত। কিন্তু এই সংলাপ-রচয়িতার নাট্যকৃতি সম্পর্কে বোধ হয় এ-কথাটা ঠিক খাটে না।
মনোজ মিত্র বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছেন মৌলিক নাটকের রচয়িতা হিসেবেই। একথাও বললে ভুল হয় না, বিশ শতকের শেষ দুই দশকে তিনিই ছিলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রধান নাটককার! নিজের দল 'সুন্দরম' তো বটেই, সেই সময়ের অন্য গ্রুপগুলোও তাঁর নাটকের মঞ্চায়ন করেছে, এমনকি থিয়েটারপাড়া ছাড়িয়ে অফিস ক্লাব, স্কুল-কলেজে অভিনীত হয়েছে। মৌলিক নাটক হিসেবেই সেগুলি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কান্না-হাসি-আশা-নিরাশার দোলায় ‘চাক ভাঙা মধু’ থেকে শুরু করে ‘গল্প হেকিম সাহেব’, ‘কেনারাম বেচারাম’ থেকে ‘চোখে আঙুল দাদা’, ‘দর্পণে শরৎশশী’ থেকে ‘অলকানন্দার পুত্রকন্যারা’ এবং সর্বোপরি ‘সাজানো বাগান’ প্রতিটি নাটক সম্পর্কেই একথা খাটে। বিশ শতকের শেষ দুই দশকে টেলিভিশনের ক্রমবর্ধমান দাপটে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির জনজীবনে থিয়েটারের জন্য পরিসর যখন কমে আসছিল, নাট্যকার মনোজ মিত্রর জীবনের সেটাই সব থেকে সৃজনশীল সময়। মঞ্চ-চলচ্চিত্র-দূরদর্শন তিনটি ধারাতেই অভিনেতা মনোজ সমান সফল। গত শতকের তিনের দশক থেকে থিয়েটার ও চলচ্চিত্র দুটি সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে।
কিন্তু আট-নয়ের দশকে পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় থিয়েটার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। টেলিভিশনের মাধ্যমে নিয়মিত চলচ্চিত্রের সম্প্রসারণ ও ধারাবাহিকের দেদার আয়োজনে মধ্যবিত্ত বাঙালি থিয়েটার পাড়াকে ভুলতে শুরু করে। ফলস্বরূপ ১৯৯০-এর দশকে স্টার, বিশ্বরূপা, রঙ্গনা, রঙমহলের মতো পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মৃত্যুঘণ্টা বেজে যায়। গ্রুপ থিয়েটার মূলত বাণিজ্যিক থিয়েটারের সমালোচনা ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে বিকশিত হয়েছিল। খোলা বাজারের হাওয়ায় এই দ্বন্দ্বটিই যায় ঘুচে! তারপরেও পেশাদার থিয়েটারের যে দর্শকরা রয়ে গেলেন তাঁদের চাহিদা মেটানোর দায় নিতে হয়েছিল গ্রুপ থিয়েটারকেই। মনোজ মিত্র এই দায় কখনও অস্বীকার করেননি। সুন্দরমের কাজ শুধুমাত্র শহুরে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর জন্য নয়, প্রতিটি প্রযোজনার আবেদন ছিল সর্বজনীন। সেই কারণেই বোধ হয় আর্থিক উদারীকরণের পর একের এক প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের উত্থানের যুগে, থিয়েটারের পরিসর যখন আরও কমে আসছে, তখনও মনোজ মিত্রকে কোনও অনুযোগ করতে শোনা যায়নি। তারই মধ্যে থিয়েটারের ধ্বজাটিকে জাগিয়ে রেখেছেন। মঞ্চ থেকে তাঁর নাটক উঠে এসেছে রূপালি পর্দাতে। তপন সিনহার পরিচালনায় তৈরি হয়েছে ‘বাঞ্ছারামের বাগান’ -এর মতো জনপ্রিয় ছবি। তার পরেও মঞ্চের ‘সাজানো বাগান’ বন্ধ হয়নি।
মনোজ মিত্রর স্মৃতিচারণে পাওয়া যায় ‘বাঞ্ছারামের বাগান’ -এর কাজ চলাকালীন দিনভর শ্যুটিং সেরে সন্ধ্যায় ‘সাজানো বাগান’ -এর বাঞ্ছা সেজে সটান স্টেজে উঠে পড়েছেন। নতুন শতাব্দীতে, যখন সিডি-ডিভিডি বা ইন্টারনেটের কল্যাণে ‘বাঞ্ছারামের বাগান’ ছবিটি যে-কোনও সময় সহজলভ্য, সেই সময়েও ‘সাজানো বাগান’ -এর হাউসফুল শো হয়েছে। সেলুলয়েডের বাঞ্ছাকে নতুন প্রজন্মের দর্শক মঞ্চে খুঁজতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে চলচ্চিত্র মঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে সহযাত্রী হয়েছে। মনোজ মিত্র নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন, একটি মাধ্যম আর একটি মাধ্যমকে পরিপুষ্ট করে। বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসে এ ঘটনা নিঃসন্দেহেই বিরল। ১৯৫৯ সালে একুশ বছরের যুবক মনোজ মিত্র কলেজের বন্ধুদের নিয়ে গড়া সুন্দরম দলের জন্য ‘মৃত্যুর চোখে জল’ নামে একটি নাটক লেখেন, যার কেন্দ্রস্থলে ছিল সংসারে অবহেলিত, রুগ্ন, মুমূর্ষু এক বৃদ্ধ। বৃদ্ধর জিজীবিষা—বেঁচে-থাকার উদগ্র বাসনাই নাটকটিকে অনন্য করে তুলেছিল। এই বৃদ্ধটি পরেও নানা সময় নতুন নতুন বেশে তাঁর নাটকে ফিরে ফিরে এসেছে। অনেক পরে এক স্মৃতিলেখায় বলেছিলেন, বার্ধক্য সম্পর্কে ভীতিই তাঁকে বার বার বৃদ্ধদের কাছে নিয়ে গেছে—কখনও তাঁদের নিয়ে তিনি কৌতুক করেছেন, কখনওবা হয়েছেন সমব্যথী।
ছাত্রবয়েসের সুন্দরম অল্পদিনেই ভেঙে যায়। ১৯৬১-তে চাকরি নিয়ে তিনি চলে যান কলকাতার বাইরে। মঞ্চ থেকে দূরে গেলেও নাটক রচনায় ছেদ পড়েনি। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরে মঞ্চের সান্নিধ্যে এলেন আবার। তখনও পুরোদস্তুর নাট্যকর্মী হতে আরও কয়েক বছর। ১৯৭৭ সালে ‘সাজানো বাগান’ নাটক দিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া সুন্দরম-কে নতুন করে জাগিয়ে তুললেন। উত্তাল সত্তর তখন শেষ হয়ে আসছে—কয়েক দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতিতে রাজ্যে এসেছে নতুন বামপন্থী সরকার—আপাত-স্থিতাবস্থার আগমনী। কিন্তু পরবর্তী একটি দশকেই আন্তর্জাতিক স্তরে বামপন্থীরা একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়তে শুরু করে, সোভিয়েতের পতন হয়ে ওঠে অনিবার্য। আর এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন বামপন্থীরা তখন প্রশাসনিক অলিন্দ ছাড়িয়ে সামাজিক নানা ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে শুরু করেছে —তার শিকড় ডুবে যাচ্ছে ক্ষমতার কুর্সিতে। এটা সেই সময়, ষাট-সত্তরে দেখা বিপ্লবের স্বপ্ন যখন অস্তমিত, ঘরে-বাইরে নানা প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছে বামপন্থা, যা ছিল বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শগত অবলম্বন। নতুনতর সেই সময়ে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন যেমন কৌলিন্য হারিয়েছে, তেমনি প্রকট হয়ছে তার মতাদর্শগত প্রতর্ক। তারই মাঝে চেনা বিষয়ের অভিনব উপস্থাপন নিয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা মনোজ মিত্র।
বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের ধারা প্রথম থেকে প্রখর রাজনৈতিক বোধে আন্দোলিত হয়েছিল—থিতু হতে চেয়েছিল ঝাঁঝালো সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক চেতনায়। জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিরিখে গ্রুপ থিয়েটার সেই সময় নিঃসন্দেহে জরুরি বিষয়কে মঞ্চে তুলে এনেছিল। সে যুগের গ্রুপ থিয়েটার নিছক শিল্পীত অভিব্যক্তি ছিল না, ছিল এক রকমের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের হাতিয়ার। স্বল্প পুঁজি নিয়ে গ্রুপ থিয়েটার যেন যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে চেয়েছিল। জনপ্রিয়তাকে স্পর্ধাভরে প্রত্যাখ্যান করে পেশাদার থিয়েটারের থেকে দূরে স্বতন্ত্র এক বৃত্ত গড়ে তুলেছিল কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার। মনোজ মিত্র কিন্তু বিষয়টিকে দেখেছিলেন একটু অন্যভাবে। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের গুরুত্ব ও ইতিবাচকতাকে স্বীকার করেও তাঁর মনে হয়েছিল বাংলা থিয়েটারের দর্শক অলীক এক ‘সুনাট্য রঙ্গে’ মজে আছে, যেখানে ঘড়ি ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ, নানা কিসিমের উৎপীড়ন-অনাচার-ভণ্ডামির নকাব খুলে শ্রেণিশত্রুদের চিহ্নিত করে। এক কথায় গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনা সুগভীর কোনও বক্তব্যবাহী— মনোজবাবুর নিজস্ব লব্জে তা ‘বক্তব্যকৈবল্যবাদী’। অথচ এ সবের মধ্যেই—মনোজ মিত্রের মনে হয়েছিল —নাটক হারিয়ে ফেলছে মানুষকে, ‘আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের মানুষ আমাদের ছেড়ে গেছে’। নিজের নাট্যপ্রয়াসে জীবনভর মনোজ মিত্র এই আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষকে খুঁজে গেছেন।
মনোজ মিত্র নিজে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না, তেমনি তাঁর চরিত্ররাও বড়ো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের শরিক নয়, ব্যক্তিচেতনাকে লুপ্ত করে দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে না তারা—কেউ নিজের বাগান রক্ষায় বদ্ধপরিকর, কেউ বা মানুষের নিরাময়ের জন্য আশ্চর্য এক প্রতিষেধকের খোঁজ করে চলেন। ব্যক্তি মানুষের সংকট, তার আশা-স্বপ্ন-কল্পনায় আন্দোলিত হয় মনোজ মিত্রর নাট্যভুবন। ব্যক্তিমানুষ, তার অবিশ্বাস্য রহস্যময় গোপনীয়তা, যেখানে সে নানা প্রবৃত্তিকে লুকিয়ে রাখে—কখনও সে আশ্রয় নেয় ব্যক্তিস্বার্থের কোটরে, আবার কখনও সেই হয়ে ওঠে শ্রেণিস্বার্থের মুখপাত্র। মনোজ মিত্রর নাটকে নানা চরিত্র ও ঘটনার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ ও শ্রেণিস্বার্থের কথা জানা যায়, কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার যেভাবে নিজের শ্রেণি অবস্থান নিশ্চিতভাবে স্পষ্ট করে, শ্রেণিশত্রুদের নিকেশের বার্তা দেয়, মনোজ মিত্র তাঁর পাত্রপাত্রীদের নিয়ে যান এই ভাবনার থেকে ঢের দূরে, সবসময় তাদের বিশেষ কোনো পক্ষপাতও থাকে না। তীব্র সমাজ সচেতন শিল্পী দায়বদ্ধ সাহিত্যিকের মতো সবসময় শ্রেণিসংগ্রামের জন্য জেহাদ ঘোষণা করেন না, অনেকক্ষেত্রেই তিনি সময়, সমাজ ও মানুষের অপারগতা, অসহায়তা, সীমাবদ্ধতাকে নিজস্ব উপলব্ধিতে শিল্পীত করে তোলেন, সহৃদয় সহানুভূতিতে যাবতীয় ক্ষতের মুখে ঢেলে দেন মায়াময় শুশ্রূষা। এর মধ্যে মতলবি কোনও আপোষকামিতা নেই, আছে নির্বিশেষ এক মানবতাবাদী প্রত্যয়। এই মানবতাবাদী উত্তাপের জন্য, এই শুশ্রূষার জন্যই বাঙালিকে বারবার ফিরতেই হবে মনোজ মিত্রর নাটকের কাছে।