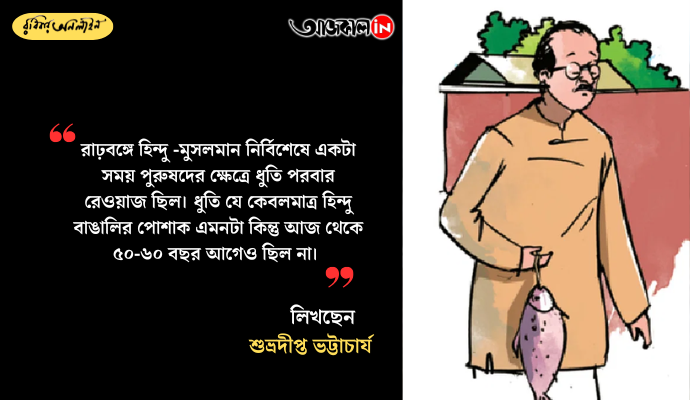
বাঙালিয়ানা কোনও পড়ে পাওয়া চোদ্দয়ানা জিনিষ নয়। বাঙালিয়ানা একটা প্রাকটিস। যুগ যুগ ধরে এই বাংলার বুকে বাংলাভাষী হিন্দু- মুসলমান একসঙ্গে থেকে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের ভিতর দিয়ে ভারতের প্রবাহমান মিশ্র সংস্কৃতির বুকে সৃষ্টি করেছে এক আদিগন্ত নীলিমা -
বিজয় দশমী ঘিরে খাওয়া-দাওয়ার সেকাল-একাল -এমন একটা তুলনামূলক আলোচনায় যদি আমরা আসতেই চাই, তাহলে প্রথমেই বলতে হয়; সেকালে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই যে পরিমাণ ম্যানপাওয়ার ছিল, আজ প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কিন্তু তা নেই। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে। দুই ভাই একত্রে থাকে এমনটা খুঁজতে গেলেও বোধহয় জাদুঘরের সাহায্য নিতে হতে হয়! প্রায় প্রতিটি একক ইউনিট। মা-বাবা আছেন টিমটিম করে। দাদু-ঠাকুমা বয়সের কারণে না থেকে, না থাকার লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। মাসি-পিসির দল সেসবও প্রায় এখন গেরস্থের বাড়িতে পালা-পার্বণে, অর্থাৎ; বিয়ে-পৈতে-আকিকা-কুলখানিতে দেখতে পাওয়া যায়।
তবে বাঙালি হিন্দুর পারিবারিক বিন্যাস আর বাঙালি মুসলমানের পারিবারিক বিন্যাসের মধ্যে যে কিছুটা ফারাক আছে, তা ঘিরে শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষজন যাপদের মধ্যে বেশিরভাগই বাঙালি হিন্দু, তাঁদের খুব সতর্ক দৃষ্টি নেই। বাঙালি মুসলমান পরিবারগুলিতে এমনকি অ-বাঙালি মুসলমান পরিবারগুলিতেও বিধবা এবং স্বামী পরিতক্তা নারীদের যে সম্মান এবং মর্যাদা দেওয়া হয়, তা ঘিরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, উনিশ শত বা বিশ শতক, যখন হিন্দু বাঙালি ঘরের বিধবার বেশিরভাগই ঠাঁই হতো কাশীধাম বা বৃন্দাবনে। তখন বাঙালি মুসলমান পরিবার, এমনকি অ-বাঙালি মুসলমান পরিবারে এমনটা খুব একটা ঘটত না। তাঁদের মধ্যে যদি কোনও স্বামী পরিতক্তা নারী পরিবারের মধ্যে থেকে উঠে আসতেন বা বিধবা হয়ে কেউ বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন, তবে হিন্দু পরিবারগুলি মুসলমান পরিবারগুলিতে কিন্তু সেই সব নারীদের সম্মান-মর্যাদা-অধিকার, নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও হিন্দু নারীর থেকে বেশ খানিকটা বেশি ছিল। তেমন নারীরা কখনও মুসলমান পরিবারের কাছে বোঝা বলে বিবেচিত হতেন না। তাঁদের ধর্মের নামে দূরে, একাকী, নিঃসঙ্গ জীবনেও ঠেলে দেওয়া হত না।
সামাজিক বিন্যাসের কারণে নানা ধরনের অর্থনৈতিক চাপান-উতোরের দরুন, শহরে বাঙালি হিন্দুর মতই, বাঙালি মুসলমান পরিবারেও একক ইউনিট গড়ে ওঠা প্রায় দস্তুর হয়ে উঠছে। তবে যদি আমরা একটু গ্রাম বাংলার দিকে চোখ ফেরাই, তাহলে দেখতে পাব, বাঙালি মুসলমান পরিবারগুলিতে কিন্তু নারীর মর্যাদার প্রশ্নটি বেশ অন্যরকম। পর্দা প্রথার আঙ্গিকে যদি মুসলমান সমাজকে দেখে আমরা ধরে নিই, মুসলমান সমাজে নারীর অধিকারের প্রশ্নটিকে, তাহলে সর্বত্র আমরা মুসলমানদের সম্পর্কে যে খুব সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হব, তা কিন্তু নয়। বিশ শতকের সূচনাকালে বা মধ্যবর্তী সময়ে বাংলা কথাসাহিত্যের ভিতরে আমরা বাঙালি মুসলমান পরিবারে নারীর যে মর্যাদা এবং সম্মানের বিষয়টি দেখেছি ,সেইসব পরিবারে কিন্তু তখনও কথ্যভাষা হিসেবে বাংলার রেওয়াজ খুব একটা হয়নি। অথচ তাঁরা কিন্তু ছিলেন বাংলাভাষী। আবার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজে উনিশ শতকে আইন আদালতের ভাষার ক্রম পরিবর্তনে পর্যবসিত হওয়া ফার্সির একটা বিশেষ রকমের প্রচলন ছিল। নবাবী আমলে আইন আদালতে যে ফার্সি ভাষার ব্যবহার ঘটত, ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন ঘটে। সেখানে স্থান পায় ইংরেজি ভাষা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অভিজাত, বিত্তবান পরিবারে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, আইন আদালত সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা সহ বিভিন্ন বৈষয়িক ক্ষেত্রে ফার্সি ভাষার ব্যবহারের একটা বিশেষ রকমের প্রচলন ছিল। আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উনিশ শতকে ঘিরে বিখ্যাত উপন্যাস 'সেই সময়' উপন্যাসে, 'বিধুশেখর' চরিত্রটির মধ্যে পেশাগত কারণে বিষয় সম্পত্তিগত কারণে অবাঙালি মুসলমানের সঙ্গে অনবদ্য ফার্সিতে কথা বলার বিবরণ পায়।
আজও গ্রামাঞ্চলে বাঙালি মুসলমানের অন্দরমহলে কোনও পালা পার্বনে বহু মহিলা একত্রিত হয়ে নানা ধরনের সুখাদ্য তৈরি করবার রেওয়াজের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে নেন। হিন্দু বাঙালির জীবনে যেমন অঘ্রহায়ণ মাস, নবান্নের মাস। সেই সময় নতুন ধান ওঠে। তাকে ঘিরে বিভিন্ন রকমের অঞ্চল ভিত্তিক মাঙ্গলিক প্রথা আছে। ঠিক তেমনই বাঙালি মুসলমানের জীবনেও এই নতুন ধান ওঠাকে ঘিরে নানা ধরনের আঞ্চলিক মাঙ্গলিক প্রথা আছে। সুখাদ্য তৈরি এবং খাওয়ার রেওয়াজ আছে। সেই সুখাদ্যের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় চালের আটার রুটি। নরম তুলতুলে চালের আটার রুটি। এটি প্রস্তুত করবার প্রণালীর মধ্যেও এক ধরনের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকে। নদিয়া জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি, যেখানে নদিয়া আর কুষ্টিয়া জেলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির একটা মিশ্রণ ঘটেছে, সেখানে এই চালের রুটি তৈরি করবার আগে চালটা আটা মাখার মত প্রস্তুত করবার জন্যে, হাতের দুটি আঙুল দিয়ে একটা অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতিকে নদীয়া-কুষ্টিয়ার মানুষ বলেন 'জলিস করা'। অর্থাৎ; দু আঙুলে টোকা মেরে মেরে ওই চালের লেইটিকে তারা এমনভাবে প্রস্তুত করেন, যার সঙ্গে ওই নরম তুলতুলে হয়ে ওঠা চালের রুটি, একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই পদ্ধতি যে রাঢ় বাংলায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয় এমনটা নয় বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ব্যবহৃত হয়, তাও নয়। বাঙালি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই বৈচিত্র্যময়তা। সেটা ভাষাগত ক্ষেত্রেই হোক, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রেই হোক বা খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেই হোক, বাঙালির সেটা নিজস্ব ঘরানা। এমনকি বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় পোশাক-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও অঞ্চল ভেদে কিছু কিছু ফারাক দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, রাঢ়বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একটা সময় পুরুষদের ক্ষেত্রে ধুতি পড়বার রেওয়াজ ছিল। ধুতি যে কেবলমাত্র হিন্দু বাঙালির পোশাক এমনটা কিন্তু আজ থেকে ৫০-৬০ বছর আগেও ছিল না।
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মত সাহিত্যিক বেশিরভাগ সময় ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুর, যেখানে তাঁর জন্ম এবং সমাধি। সেই গ্রামের পাশেই তাঁর একটি অসাধারণ মর্মর মূর্তি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই মূর্তিটিতে দেখা যাচ্ছে ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে। আবার যখন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একটা চরম পর্যায়, তিনের দশকের অন্তিম লগ্ন, চারের দশকের শুরু। সেই সময় অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের নেতা আবুল হাশিম। যিনি ছিলেন বর্ধমান জেলার মানুষ। ধুতি পাঞ্জাবি পরবার কারনে বহুকাল মুসলিম লীগের অন্দরমহলে তিনি বেশ কিছুটা কোণঠাসা ছিলেন। মুসলিম লীগের বাংলা শাখার সাংগঠনিক নির্বাচনে তাঁর হেরে যাওয়ার কারনও অনেকে সেই সময় বলেছিলেন ধুতি পাঞ্জাবি পড়বার বিষয়টিকে।
পরবর্তী সময়ে তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরিত্যাগ করেন এবং তাঁর দলের সাংগঠনিক নির্বাচনে জিতে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। মেয়েদের জীবনে তখন শাড়িটাই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পোশাক। সেলোয়ার কামিজ ইত্যাদি পোশাকের চল তখন বাঙালি মেয়েদের মধ্যে খুব বেশি ছিল না। তখনও শাড়ি পরবার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈচিত্র্য ছিল। গত শতকের চার পাঁচের দশক থেকে আরো স্পষ্ট হতে শুরু করে এই বৈচিত্যের ধারা। ফিল্মের নায়িকাদের পোশাক-কেশ বিন্যাস ইত্যাদির নিরিখে একটা সময় যখন কানন প্রমথেশের 'মুক্তি' ছবি বাঙালির বিনোদন আঙিনায় বড় রকমের জায়গা করে নিল, তখন নায়িকা কানন দেবীর বেড়াবিনুনী দেওয়া কেশবিন্যাস সেকালের মেয়েদের সাজসজ্জায় বিশেষ রকমভাবে ঠাঁই করে নিয়েছিল।
আবার পুরুষের ক্ষেত্রে যদি আলোচিত হয় তাহলে প্রমথেশ বড়ুয়ার পাঞ্জাবির বৈশিষ্ট্য, একটা সময় 'বড়ুয়া গলা' নামে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিল। ছবি বিশ্বাসের গোলহাতার বেড় অনেক বড়। আবার আরও অনেক পরে উত্তমকুমার বা বিশ্বজিতের চুল ছাঁটার স্টাইল -এগুলো বাঙালিকে তাঁর সাজ, পোশাক রুচি আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। এই প্রভাব ছিল খাঁটি বাঙালিয়ানার প্রভাব। সেকালের বোম্বাই বা একালের মুম্বাই দিয়ে তখন বাঙালি তেমন একটানিজেদের ফ্যাশান, রুচি, খাওয়া- দাওয়া কোনও কিছুতেই প্রভাবিত হত না। বিভাগ পূর্বকালে পূর্ব বাংলায় ছিল বাঙালি রুচির রকমফের ঘিরে জেলায় জেলায় একটা অলিখিত প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা যে এপার বাংলায় ছিল না, তা নয়। তবে সেই লড়াইতে ছিল না কোনও বিদ্বেষ। ছিল অপার আনন্দ। যেন রবীন্দ্রনাথই সেখানে মূর্ছিত হতেন, 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে’।