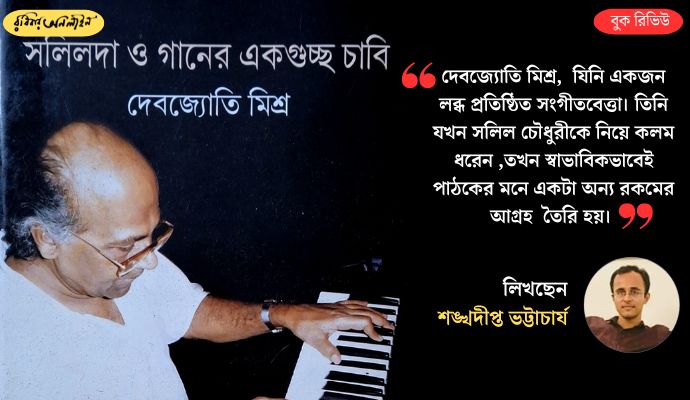
সলিল মানে এক অপার বিস্ময়। সেই বিস্ময় সাগরে দেবজ্যোতির ডুব, আর তুলে আনা মণিমুক্তার চাবির খোঁজ--
ভারতীয় সংগীতের জগতে সলিল চৌধুরীর অবস্থিতি, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিচরণের যে বহুমুখীতা, সে বিষয়গুলিকে একটি গ্রন্থে ধরা সত্যিই অত্যন্ত কঠিন কাজ। সংস্কৃতি জগতের ক্ষেত্রে এহেন কাজ নেই , যেখানে সলিলের অবাধ এবং সাবলীল বিচরণ ছিল না। সলিল যে কেবলমাত্র একজন অতি উচ্চমার্গের সামাজিক বোধসম্পন্ন কবি ছিলেন তাই-ই নয়। সলিল যে কেবলমাত্র একজন ভারতীয় সংগীতের সমস্ত রকমের ধারার সংশ্লেষবাহি এক অনন্য সাধারণ সুরকার ছিলেন তাও নয়।
সলিল যে কি ছিলেন, একমাত্র সলিল চৌধুরীই বোধহয় তার উত্তর। তাঁর এই যে বহুমুখী প্রতিভা, খুব মনে পড়ে যাচ্ছে রবীন্দ্র সদন চত্বরে সলিলের নশ্বর শরীরের সামনে অভিনেত্রী শোভা সেনের বলা সেই উক্তিটি। শোভা সেন সেদিন বলেছিলেন; আমি সলিলকে কেষ্ট ঠাকুর বলে ডাকতাম । যে অসামান্য বাঁশি সলিল বাজাতো, সেই বাঁশি বাজানোর কৃতিত্বের জন্য সলিলকে বলতাম; কেষ্ট ঠাকুর।
দেবজ্যোতি মিশ্র, যিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সংগীতবেত্তা। তিনি যখন সলিল চৌধুরীকে নিয়ে কলম ধরেন ,তখন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে একটা অন্য রকমের আগ্রহ তৈরি হয়। দেবজ্যোতি নিজে সলিলকে খুব অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন। তাঁকে বলা যেতে পারে সলিলের ভাব শিষ্য। সলিলকে তিনি আত্মস্থ করেছেন। সলিলের গান ঘিরে, সংস্কৃতি ঘিরে, চিন্তা চেতনার বারমাস্যার ভেতর দিয়েই দেবজ্যোতির ঘটেছে সলিলকে আত্মীকরণ।
আর সেখানেই সলিলের গানের চাবিকাঠি খুলতে গিয়ে, ব্যক্তিসলিলের জীবন ও জীবনের উন্মেষ, যেভাবে দেবজ্যোতি মেলে ধরেছেন ,সেভাবে প্রাণের ছোঁয়া, সলিলের প্রয়াণের পর, সলিলকে ঘিরে খুব কম লেখার ভেতরেই আমরা পেয়েছি। একদম শৈশব, কৈশোরের দিন, অসমের জনজীবন ঘিরে তাঁর পারিবারিক পরিসর এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে একটা রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ। যে বঞ্চনা- শোষণ- নিপীড়নকে ঘিরে সলিলের বোধের দুনিয়ার উন্মোচন ঘটছে, সেগুলি যেন দেবজ্যোতি ছবি ছবির মতো করে নিয়ে আসছেন।
সলিলকে যাঁদের দেখবার সুযোগ ঘটেছিল, জানবার সৌভাগ্য ঘটেছিল, তাঁদের কাছে মনে হবে, এ গুলো যেন আবার সলিলকে স্পর্শ করতে পারার মতো একটা অনুভূতি। সলিলের প্রয়াণের পর নানাভাবে তাঁকে নিয়ে চর্চা হয়েছে। বেশিরভাগ চর্চাই হয়েছে এমন কিছু লোকেদের দ্বারা ,যাঁরা গানের ' গ ' জানেন না। তাঁদের কাছে সলিল হয়ে উঠেছেন কেবলমাত্র একটা গবেষণার, উপাধি পাওয়ার উপলক্ষ্য মাত্র। সলিলকে স্পর্শ করবার তাগিদ তাঁদের কারো মধ্যে কখনও কিছুই ছিল না।
এখানেই বলতে হয়, দেবজ্যোতি মিশ্রের এই প্রয়াস, সবদিক থেকে একটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। গড়িয়াহাটের মোড়ে যশোদা ভবন। ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দীদের উল্লেখ, এগুলি যাঁরা সলিলকে আত্মস্থ করতে পারেননি, তাঁদের কাছে খানিকটা অহেতুক বিষয় বলেই মনে হবে। কিন্তু যে পরম মমতায় এই সমস্ত মানুষজনদের, বিশেষ করে সলিলের পূর্বসূরী গণনাট্য আন্দোলন, গণসংগীতের ক্ষেত্রে যাঁকে বলা যায় জ্যোতিষ্ক, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সশ্রশংস উল্লেখ এবং তাঁর অবদান ঘিরে সব শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা, যে আলোচনা পড়তে পড়তে মনে হয় , লেখক দেবজ্যোতি, আর দশজন মামুলি সলিল চর্চাকারীর মতো কোন পল্লবগ্রাহী চিন্তা চেতনার মানুষ নন।
সলিল সম্পর্কে এই বইটিতে দেবজ্যোতি একটিও অতিকথন বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ উচ্চারণ করেননি। সলিলকে ঘিরে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা এবং এবং সলিল পরবর্তী সময়কালে একটা দীর্ঘ পর্যায় ধরে, সংগীত জগতের নানা ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে নিজের আত্তিক সম্পর্ক, সেটাই যেন দেবজ্যোতির এই গ্রন্থকে একটা নতুন রকমের স্বাদ এনে দিয়েছে।
তবে ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দীদের উল্লেখ, তাঁদের ভূমিকা, '৪৬ এর দাঙ্গা নিরসনে গণনাট্য আন্দোলনের ভূমিকা, এ সমস্ত কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা থাকলেও অনুল্লিখিত থেকে গেছেন কলিম শরাফি। ব্যক্তি সলিল এবং তাঁর সাঙ্গীতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে স্বাধীনতা, দেশভাগের আগে যেমন কলিমের একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল, ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তান আমলেও সেই সম্পর্কে কোনও ভাঁটা পড়েনি। আবার স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির পরেও সেই সম্পর্ক এতোটুকু ম্লান হয়নি। সলিল বাংলাদেশে গেলে কলিমের সিদ্ধেশ্বরীর বাসাতেই হোক বা এলিফ্যান্ট রোডের বাসাতেই হোক, একবার যাননি, এমনটা কখনও ঘটেনি। আর সলিল তাঁর বাড়ির সামনে এসেছেন, তাঁর গাড়ি থেমেছে কি থামেনি , পড়িমরি উপর থেকে নেমে এসে সলিলকে স্বাগত জানাচ্ছেন কলিম, এই দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন কলিন শরাফি, সলিলের সম্পর্কে রসায়নটি।
দেবজ্যোতি মিশ্রের বইটি সত্যিই যেন সলিলের গানের বন্ধ দরজার চাবি খুলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে সলিলের যে সার্বিক অবদান ,তাকে পরিস্ফুটিত করবার ক্ষেত্রে দেবজ্যোতির এই ভূমিকা কেবলমাত্র সলিলচর্চা নিরিখেই নয় , বাংলার সংস্কৃতি চর্চার এক প্রবাহমান ধারার, ধারাবাহিকতার বর্ণনা প্রদানের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছে। সলিল যে কেবলমাত্র সঙ্গীতেই আবদ্ধ নন, সলিল যে কেবলমাত্র ছোটগল্পে আবদ্ধ নন। সুরারোপের নির্দিষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে সলিল নিজেকে কখনও আটকে রাখেননি। গোটা বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একটা রূপ হিসেবে যদি আমরা কারও কথা চিন্তা করি, সেই চিন্তায় প্রথম তিনজনের মধ্যে বাঙালির মনলোকে অবশ্যই উচ্চারিত হবে সলিল চৌধুরীর নাম।
এই বিষয়টিকেই আলোচ্য গ্রন্থে যেভাবে দেবজ্যোতি তুলে ধরেছেন তা কেবলমাত্র বাংলার সংগীতময় অঙ্গনের একটি পরিপূর্ণ বিবরণ নয়, তাকে সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে, বিশ শতকের বাংলার সমাজ চেতনার প্রবাহমান ধারার এক স্রোতস্বিনী নদীর বর্ণনা। এমন একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপিত করবার জন্য বাংলা আর বাঙালি আজকাল কর্তৃপক্ষের চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন।
সলিলদা ও গানের একগুচ্ছ চাবি
দেবজ্যোতি মিশ্র
আজকাল
৩৫০ টাকা