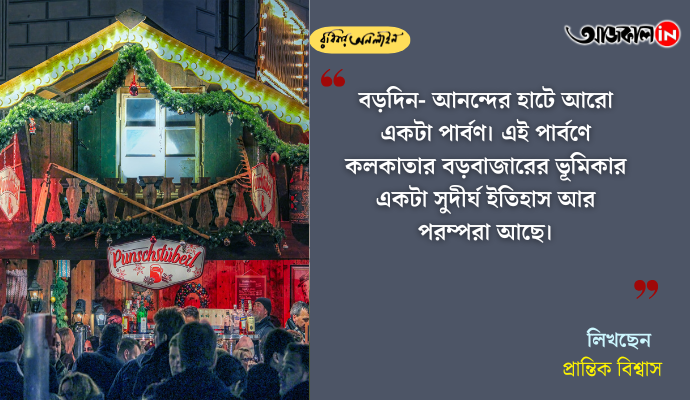
বড়দিন- আনন্দের হাটে আরো একটা পার্বণ।এই পার্বণে কলকাতার বড়বাজারের ভূমিকার একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আর পরম্পরা আছে।তার ই সুলুক সন্ধান--
এসেই যখন পৌঁছেছি বড়দিনের বড়বাজারে তখন আমার আর প্রোফেসর পার্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য তার স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাই চেষ্টা করছি মার্কেটের প্রত্যেকটা দোকান ছুঁয়ে যেতে। সেটাই হবে এক বিরাট অভিজ্ঞতা।
বাড়িতে ঝোলানোর জন্যে সুতোর তৈরি পরী, রেইনডিয়ার, সান্তা বুড়ো, প্রজাপতি ইত্যাদির সম্ভার দেখলাম পরপর কয়েকটা দোকানে। দাম শুরু পাঁচ ইউরো থেকে।
“বিসওয়াস, লক্ষ করেছো কি, এখানে প্রায় সব কিছুই হ্যান্ড মেড! খাবারও সব অর্গানিক, তাই দামও একটু বেশি। মজার ব্যাপার কি জান, সপ্তদশ শতকে, শুরুর দিকে ইংরেজ পিউরিটানরা যুক্তি খাড়া করেছিল যে, ক্রিসমাস মার্কেট মাত্রাতিরিক্ত খাওয়া আর মদ্যপানের মতন কামুক আনন্দের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।”
“ওহ, তাই বুঝি। তো তারপর?” আমি আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম।
“ইউলেটাইড ঋতু বা ক্রিসমাস ঋতুর এই সমালোচনা সত্ত্বেও, পরের শতকের গোড়ার দিকে ক্রিসমাস মার্কেটগুলো ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকটা আজকের মতো। সেগুলো ঐ বিশেষ সময়কালে মাংস, রকমারি বেকড ফুড এবং অন্যান্য পণ্য কেনার জায়গা ছিল। এগুলোর অবস্থান ছিল মূলত গীর্জার কাছাকাছি আর শ্রমিক, গির্জাগামী লোকজন থেকে শুরু করে বিদেশী পর্যটক, অভিজাতবর্গ -- সব ধরনের নাগরিকদের জন্যে একটা মিলনস্থল ছিল।” প্রোফেসর একটা বার্গারের দোকানের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন।
“ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পর ছবিটা কি কিছুটা পালটে গিয়েছিল?” প্রশ্নটার উত্তর পাওয়ার ফাঁকেই আমি একটা দোকানের সামনে একজন বয়স্ক লোকের বার্গার খাওয়ার একটা ছবি তুলে নিলাম।
প্রোফেসর সেটা টের পেয়ে আঁতকে উঠলেন, “করছ কী? আমাকেও পুলিশে ধরবে তো?”
আমি একটু কপট সংকোচ মাখানো গলায় বললাম, “আসলে এমন ছবির লোভ সামলাতে পারলাম না!”
“চল, এবার একটু এগোই।” মনে হল প্রোফেসর অকুস্থল থেকে পালাতে পারলেই বাঁচেন।
আমরা চলে এসেছি একটু দূরে একটা ফুলের দোকানের সামনে। দুটো মেয়ে আর দুটো ছেলে নানা ডিজাইনের ব্যোকে বানাচ্ছে। মেলায় আসা লোকেরা পছন্দমত কিনছেও। সেখানেও আমি চটপট কিছু ছবি তুললাম।
“সঙ্গে ক্যামেরা থাকার এই এক জ্বালা, হাত নিশপিশ করে। ফটোগ্রাফারদের থামানো মুশকিল!” প্রোফেসর কাছে এসে মুচকি হেসে বললেন। লক্ষ করলাম, আমার ছবি তোলার সময় উনি একটু দূরে সরে থাকছেন।
“আমার প্রশ্নের উত্তরটা…” আমি ওনাকে মনে করিয়ে দিলাম।
“ওহ্ ইয়েস। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পর পরিস্থিতিটা কিছুটা তো নিশ্চয়ই পালটে গিয়েছিল। উনবিংশ শতকের ক্রিসমাস মার্কেটগুলোকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল, যেগুলোর ব্যাপকহারে উৎপাদিত পণ্য বাড়িতে এবং হাতে তৈরি জিনিসপত্রের তুলনায় দামে অনেক সস্তা আর সহজলভ্য ছিল। তাই অনেক মার্কেট ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।”
“ওহ্ ...” খারাপ লাগল শুনে।
“এবার শোনো কিছু বিবর্তনের কথা। ক্রমশ বিস্তারলাভ করা নাৎসি শাসন ১৯৩০-এর দশকে ক্রিসমাস মার্কেটের এই পুরনো ঐতিহ্যকে জার্মান মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করে। বার্লিনের মার্কেটকে শহরের কেন্দ্রে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৩৪ সালে সেখানে রেকর্ড-ব্রেকিং ১.৫ মিলিয়ন দর্শক এসেছিল। দু'বছর পরে, দুই মিলিয়ন!”
“একেই বলে প্রপাগান্ডা!” আমি হেসে বললাম।
“তা ঠিক। নাৎসিরা এটাই নিশ্চিত করেছিল যে, ক্রিসমাস মার্কেটগুলো যেন বিশেষভাবে ছুটির সাথে সম্পর্কিত আইটেমগুলোই বিক্রি করে। অনুমোদিত জিনিসপত্রের মধ্যে ক্রিসমাস ট্রি-র সাজসজ্জা, খেলনা, জিঞ্জারব্রেড, পুষ্পস্তবক … এইসবই কেবল অন্তর্ভুক্ত ছিল। আয়োজকরাও উৎসবের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে মালা, কাঁচের বল এবং পরীর আকারের আলো ব্যবহার করেছিল। আরও শোনো, লোকেরা মেলায় আসবে অথচ কিছু মুখে তুলবে না, তা আবার হয় নাকি! তাই মানুষের রসনার তৃপ্তি সবার ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হল।”
এই সত্যের মিল খুঁজতে গিয়ে কলকাতার বইমেলার কথা সাথে সাথে আমার মাথায় এল।
“তিরিশের দশকের শেষের দিকেই, ব্র্যাটওয়ার্স্ট, হেরিং এবং অন্যান্য জার্মান ট্রিট অফার করা খাবারের স্টলগুলো মার্কেটের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে।” প্রোফেসর আরও যোগ করলেন।
আমরা হাঁটছি, কথা বলছি আর তার মধ্যেই বিকেলটা গড়িয়ে সন্ধ্যের দিকে ঢলে পড়েছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার নামছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে লোকজনের ভিড়। আগে বয়স্কদের বেশি দেখা যাচ্ছিল, এখন তারা বাড়ি ফেরার পথে। মাঝবয়সী আর অল্পবয়সীরাই এখন সংখ্যায় বেশি। পানীয়র স্টলগুলোতে উপচে পড়ছে ভিড়। বিয়ার স্টলগুলোতে বিয়ার দেদার বিক্রি হচ্ছে। স্টলের সামনে একটা গোল টেবিল আর তার মাথায় এক বড় ছাতা। ছাতার তলায় টেবিল ঘিরে যুবক যুবতীরা হাসিঠাট্টা, আলাপ-আলোচনায় মশগুল। যে স্টলগুলোয় ওয়াইন পাওয়া যাচ্ছে – সেই স্টলগুলো সব থেকে ঝলমলে।
আমরা এবার 'গেব্রানটে ম্যান্ডেল' (মিষ্টিযুক্ত, রোস্ট করা আমন্ড) আর জার্মান ঐতিহ্যবাহী ক্রিসমাস কুকি 'লেবক্যুচেন' খেলাম শেয়ার করে। দুটোর স্বাদই বেশ নতুন ঠেকল আমার কাছে।
অনেককেই দেখছি ব্যাভেরিয়ার ট্র্যাডিশনাল ড্রেস পরে এসেছে। মেয়েদের পোশাককে বলে 'ড্যান্ডেল' – একটা সাদা ব্লাউজ, রঙিন বডিস, স্কার্ট এবং অ্যাপ্রন। ছেলেদের গায়ে সাদা শার্ট আর তলায় 'লেডাহজেন'। তার দাম শুরুই হয় একশো ইউরো থেকে।
মারিয়ানপ্লাৎস স্টেশন থেকে মার্কেটে ঢোকার মুখে “লেগো” ব্র্যান্ডের খেলনার একটা পেল্লায় দোকান আছে। সেখানে দেখি জনারণ্য, থিকথিক করছে লোক। গেলাম ও'দিকে। অনেক বাচ্চাদের দেখলাম, বাবা মায়েরা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। শোরুমের সামনে একটা কাঁচের ঘরের ভেতরে কত রকমের যে পুতুল সাজানো তার ইয়ত্তা নেই। খুদেরা সেই কাঁচে মুখ লাগিয়ে দেখছে। আমি ইচ্ছেমত ছবি তুললাম বেশ কয়েকটা। দেখে মনে হচ্ছিল কাঁচের দু'দিকেই যেন পুতুলের ভিড়।
প্রায় সাতটা বাজে, চারদিক আলো ঝলমল করছে। দু'জনে ঠিক করলাম এইবার ডিনার গোত্রীয় বেশ ভারি কিছু খাওয়া যাক। প্রথম অপশন, একটা বান পাউরুটির মধ্যে এক ফুট লম্বা 'ব্রাথহোয়াস্ট' বা হোয়াইট পর্ক সসেজ। জোড়ায় জোড়ায় অনেকে একটাই কিনে দু'দিক থেকে দু'জনে সসেজে কামড় বসাচ্ছে। আমি সকালে প্রচুর চিকেন সসেজ খেয়েছি। তাই আর ইচ্ছে করল না। তার বদলে নিলাম 'শাইনেব্রাতেন' বার্গার – ভিনিগার, কর্ন আর অন্যান্য সিজনিং মিশিয়ে পর্ককে খুব আস্তে আস্তে রোস্ট করে সেটা বানানো হয়। প্রোফেসর বুঝিয়ে দিলেন 'শাইনে' হল সোয়াইন বা পিগ, 'ব্রাতেন' হল টক টক ঝোল। এই বার্গার দু'জনেই একটা করে নিলাম – অপূর্ব খেতে কিন্তু একজনের পক্ষে একটু বেশিই বড়।
“মেলাতে স্থানীয় লোক ছাড়া বেশি ট্যুরিস্ট চোখে পড়ল না, তাই না?” প্রোফেসর টিস্যু পেপারে মুখ মুছতে মুছতে বললেন।
“ভিয়েনায় আশাকরি অনেক বেশি লোক থাকবে।”
“বলতে পারছি না বিসওয়াস। ভিয়েনায় প্রায় বারোটা ক্রিসমাস মার্কেট। বাই দ্য ওয়ে, এবার তোমাকে একটু 'গ্লুহ ওয়াইন' চাখাই। ঠাণ্ডায় ভাল আরাম পাবে। ফ্লাইটে দেখছিলাম তুমি রেড ওয়াইন নিয়েছিলে। এই বিশেষ ওয়াইনটায় মেশানো থাকবে কিছু স্পাইসেস আর কিশমিশ, আর সার্ভ করবে একটু গরম গরম ...”
এটা শোনার পর পেট ভর্তি থাকলেও অজান্তেই আমার জিভে জল চলে এল।