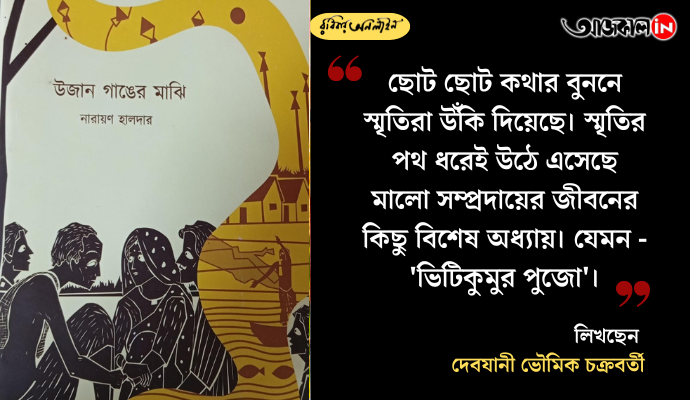
নদীর আশ্রয়ে মানবজীবনে নানান শুশ্রূষা মেলে। কুল ভাসানো নদীর ক্ষয়ক্ষতির হিসেব না রেখে নতুন করে বসত গড়ার পরম্পরাই মানুষ বহন করে চলেছে যুগের পর যুগ। নদীকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলে জীবন ও জীবিকা। সাহিত্যে তাই নদীর অনুপ্রবেশ নয়, ঘটেছে বারংবার প্রবেশ, সেই প্রাচীনকাল থেকেই। কাজেই নারায়ণ হালদারের 'উজান গাঙের মাঝি' উপন্যাসটির নদীকেন্দ্রিকতা নতুন কিছু নয়। কথক উত্তম পুরুষের জবানীতে ফ্ল্যাশব্যাকে কাহিনি বলেছেন। বলাবাহুল্য, সেটিও ইতিপূর্বে একাধিক বার আমরা দেখেছি। তবু পাঠককে এক দুর্দান্ত চৌম্বকশক্তিতে আকৃষ্ট করে রাখেন লেখক তাঁর কথাবয়ন কৌশলের স্মার্টনেসে। যদিও তিনি তাঁর দেওয়া কথা মতো কাহিনির অন্দরে প্রবেশ করেন নিই -একজন নিরাসক্ত উপস্থাপকমাত্রই থেকে গিয়েছেন। যশোর, ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচলিত বঙ্গালি উপভাষার বিশেষ ছাঁদটির প্রয়োগ, পাঠকের জন্য বিশেষ প্রাপ্তি।
এখানে সাঁইত্রিশটি পরিচ্ছেদ জুড়ে কথক স্মৃতিরোমন্থন করেছেন। বর্তমানে তিনি এক হতাশ বৃদ্ধ। গ্রন্থের শুরুতে 'নিবেদন' অংশে যাঁকে 'তেমাথা বুড়ো' বলে উল্লেখ করেছেন লেখক। শারীরিকভাবে বলহীন তথা পরিবারের মধ্যে গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেও লেখকের কথায় -'গলায় মোড়লি আছে।' সেই যে কথায় আছে গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। জীবনের এহেন প্রান্তিক কোণে অবস্থিত বৃদ্ধের বলা ছোট ছোট স্মৃতির কোলাজ পাঠককেও অতীতচারী করে তোলে। সাহিত্যের নিবিড় পাঠকই হোন বা গবেষক, এই কথকের সাহায্যে পৌঁছে যেতে পারেন জীবন্ত ইতিহাসের অন্দরে। এই ইতিহাস নদীজীবী মালোজাতির। তাঁদের সংস্কৃতির পরিচয়ের পাশাপাশি জীবনসংগ্রামের কথা পড়লে সংবেদনশীল পাঠকমাত্রই আবেগতাড়িত হতে বাধ্য। বৃদ্ধ কথক যে বর্তমানে ভালো নেই সেটা বোঝা যায় যখন সংক্ষেপে লেখক 'আধিপত্যের' কথাটি উল্লেখ করেন। এখন যেটা নেই। নদীযাপনের নেশায় নিশ্চিত মাসমাইনের নিরাপত্তাকে তিনি একদিন অবহেলা করেছেন, ফলে এখন তাঁর ছেলে বৌমার তাচ্ছিল্যে জীবন কাটে। নদীও প্রায় শুকিয়ে যাওয়ায় মাছ সেভাবে হচ্ছে না -এ যেন জেলে জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়ে তিনি বলেন -'সেদিন যদি যাতাম! আইজ অভাব থ্যাকতু না। পায়ের উপর পা তুলি খাতাম। এমন ক্যাটক্যাট করিতি প্যারতু! সবই কপাল!'
ছোট ছোট কথার বুননে স্মৃতিরা উঁকি দিয়েছে। স্মৃতির পথ ধরেই উঠে এসেছে মালো সম্প্রদায়ের জীবনের কিছু বিশেষ অধ্যায়। যেমন -'ভিটিকুমুর পুজো'। এটি চৈত্র সংক্রান্তিতে মহা ধুমধাম করে গোটা গ্রামজুড়ে হয়। যেবার খোসপাঁচড়ায় গ্রাম ভরে গিয়েছিল সে'বার এই পুজো বাড়িতে না হয়ে বারোয়ারি তলায় সবাই মিলে করেছিল। ছোট বড় সবাই মিলে ফুল কুড়িয়ে এনেছিল পুজো উপলক্ষ্যে, গ্রন্থে ফুলের নামগুলি এভাবে আছে -মান্দার, কাটালচাপা, পাকড়া, বৈন্নি, ভুইচাপা, ভাটফুল, দুদচাপি ইত্যাদি। বড় বেদি করে তিন থাকের উপর শিবলিঙ্গ বসানো হয়েছিল। যে ছড়া বলে পুজো শুরু হয় সেটিরও উল্লেখ দেখে লেখকের নিখুঁত ক্ষেত্রসমীক্ষার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। 'পুষ সংকরান্তি'র সন্ধেবেলা আলপনা দিয়ে পিঠে গড়ার কথা আছে। সেখানেও আবার গ্রাম্যসংস্কার বশে লতার মা 'ছোঞ্চিই' বসে থাকাকালীন একটিও পিঠে ওঠে না। তিনি চলে গেলে ওঠে নানান প্রকার পিঠে। আবার গঙ্গা দশহরায় খুব বড়ো করে পুজো করতো সব হালদার মিলে। লেখক এই পুজোর স্ত্রী-আচারগুলি খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন কথকের মাধ্যমে। সেদিন বাড়িতে উনুন জ্বলে না। বাসি-পান্তা খেতে হয়। কিন্তু নিতাইয়ের বউ গাজোয়ারি করে উনুন ধরাতে গিয়ে দেখে সাপ বসে আছে, ফলে ভয়ে তার অবস্থা খারাপ। তাতে বৃদ্ধ কথক বলেন দু’পাতা বই পড়ে ঠাকুর দেবতাকে অত অশ্রদ্ধা করতে নেই। গাশশির প্রসঙ্গটিও রয়েছে। গাশশিতে পড়লে ভাল মনে থাকে, কাজল পরলে দৃষ্টি ভাল হয়। রয়েছে চরম দারিদ্র্যের বর্ণনা -'কন্টোলই ভরসা'। গম, ভুট্টা, মাইলো, শাড়ি, ধুতি পাওয়া যেত তাতে। মাছ কমে যাওয়ায় একসময় সংসারে সাত জনের অন্নসংস্থান করতে কথককে বিকল্প রোজগারের ভাবনাও ভাবতে হয়েছে। যেমন, মালগাড়ি গেলেই কয়লা সংগ্রহ। পাটকাঠির মাথায় পঞ্চাশ পয়সা বা এক টাকা বেঁধে ড্রাইভারের হাতে দিলেই ড্রাইভার ঝমঝম করে কয়লা ফেলে দিতেন। এক টাকার কয়লা পাঁচ টাকায় বিক্রি হত। এক্ষেত্রে আবার এলাকা ভাগ করা থাকত -কে কোন অংশটুকুর মধ্যে কয়লা কুড়োবেন। জনৈক বিমল ঠাকুর শীতের রাতে একবার কয়লা কুড়িয়ে বাড়ি ফিরে উঠোনে ঢালতেই নিরঞ্জনের কাটা মাথাটি পান কয়লার মধ্যে। সে এক বিভীষিকা! অবশেষে নিতাই ও হরির সঙ্গে গিয়ে নিরঞ্জনের লাশ খুঁজে সেখানে মাথাটা রেখে আসা সম্ভব হয়। নিরঞ্জনের মৃত্যু কয়লা কুড়োতে গিয়েই হয়। ওই প্রবল ঠাণ্ডায় কথকের পক্ষে কয়লা কুড়োতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তিনি আক্ষেপোক্তি করেছেন -'মরণ থাকলি কিডা ঠেকাতি পারে!' লকা, ছিদাম, ন্যাপালরা ওয়াগন ভাঙত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে -চাল, গম, কয়লা, সার ইত্যাদির আশায়। কথকের ভাইপো লকা ছিল অসীম সাহসী। পুলিশকেও অগ্রাহ্য করে চলন্ত মালগাড়িতে কল্যাণী থেকে মদনপুরের মাঝামাঝিতে অবস্থিত সাহেববাগান থেকে উঠে বটগাছের সামনে নামত সে। একবার পুলিশের গুলিতে সে বেঁচে গেলেও বেচারা মদু সেখানে গরু চড়াতে গিয়ে অসহায়ের মতো মারা গেল। বোঝা যায়, নদিয়া জেলার একটি অঞ্চলের মালোদের জীবন-কাহিনি এই 'উজান গাঙের মাঝি'।
মালোদের সংস্কৃতি তথা জীবনেতিহাস প্রকাশে তাঁদের মুখের ভাষার নিখুঁত প্রয়োগে অতীত জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিছু শব্দ যেমন -পৈটি (বারান্দার সিঁড়ি), আমাচা (পুকুরে চাষ করা হয় না এমন মাছ তবে রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা বাদে), খ্যাপলা(একধরনের জাল), নোকু(নৌকা), আনা দিন( অন্যদিন), জার(ঠাণ্ডা), কুশ(কুয়াশা), ফাঁস জাল (একরকম জাল), নাবাজাল (একরকম জাল), গোদান গোভূত (বলদ গরু গলায় দড়ি নিয়ে মারা গেলে গোদান হয়), খরা ভ্যাসাল (মাছ ধরার এককৌশল)। মালো জীবনের কিছু বিশ্বাসও এখানে উঠে এসেছে কথকের জবানীতে। যেমন, 'খোসপচড়া' সারাতে ১০৮টি নিমপাতা জলে ফুটিয়ে মন্ত্র বলে পাঁচবার ঢালতে হবে। এটিকে 'জলসার' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনবার এমন জলসার করলেই একেবারে 'চালভাজার মতো' শুকিয়ে যাবে সমস্ত খোসপচড়া।
একটি ছোট্ট উপন্যাসে মালো সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের ইতিহাস সামগ্রিক পরিসরে যেভাবে লেখক তুলে ধরেছেন তা অনবদ্য। তাঁদের অনুযায়ী যে ভাষাভঙ্গিমা এখানে গৃহীত, তাতে পড়ার সময় যেন তাঁদের কণ্ঠও আমরা শুনতে পাই। সবমিলিয়ে শৈলীগত অনন্যতায়, এক মাঝির আত্মকথার মাধ্যমে মালোদের জীবনের বাস্তব রূপ চলচ্ছবির মতো ফুটে ওঠে পাঠকের সামনে। একটি যুগকে চিনিয়ে দেন লেখক।
উজান গাঙের মাঝি
নারায়ণ হালদার
পরিধি প্রকাশন, উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩৯০, পশ্চিমবঙ্গ
প্রকাশকাল: ২০২৪
মূল্য: ১০০ টাকা