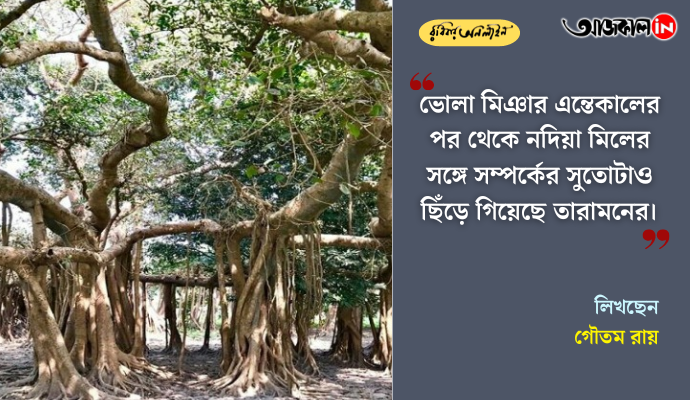
তখনও পৌরভোট হয়নি নতুন সরকার আসবার পর। প্রশাসকই চালাচ্ছেন পৌরসভা। তবে প্রশাসক পদে আগে যিনি ছিলেন, সরকার বদলের পরে তিনিও বদলি হয়েছেন। নতুন অফিসার এসেছে ভাটপাড়া পৌরসভাতে প্রশাসক হিসেবে। সরকার বদল হলেও এই নতুন প্রশাসক সরকার পক্ষের দলের সঙ্গেও বেশি মাখামাখি করেন না। আবার বিরোধী কংগ্রেস দলের লোকজনদের সঙ্গেও না। নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নিরপেক্ষতায় এলাকার সবাইই খুশি। আগে যিনি ছিলেন তার মধ্যে যে খুব একটা নিরপেক্ষতার অভাব ছিল তেমন নয়। কিন্তু এলাকার সেই আমলের ডাকাবুকো এম এল এ অবনীশ ভটচাযকে সেই লোকটা একটু ভয়ই করত। এলাকায় যুব কংগ্রেসের তখন বেশ নামডাকওয়ালা নেতা এই অবনীশ। যদিও পোষাকি নামের থেকে তার বেশি পরিচিতি ছিল ডাক নাম 'গবু' তে।
পাশ্চাত্য বৈদিক বামুন গবুর মূল ভাটপাড়ায় আত্মীয় স্বজন ছড়ানো। আর গবুর দৌলতে তখন প্রায় সবাইই কংগ্রেস করে। করে এই কারনে, যদি একটু আধটু সুযোগ সুবিধে মেলে -এই প্রত্যাশায়। প্রত্যাশা যে সব সময়ে মিটত, তেমনটা বলা যায় না। আবার একদম যে সবাইই খালি হাতে ফিরে আসত, তেমনটাও নয়। তবে গবু যে শান্ত আর অশান্ত আচরণের ভারসাম্য রেখে এলাকায় রাজনীতি করে গেছিল, তার দৌলতে গবুর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরেও এতটুকু রোজগারপাতি না করেই তার ছেলে, ছেলের বৌ, নাতনি সবাইই পায়ের উপর পা তুলে চোর্বচোষ্যলেহ্যপেয় করে উদর ভরিয়ে যাচ্ছে।
রাজনীতির সে এক উত্তাল সময়। তবে সেই উতোল হাওয়ার তাপ ভাটপাড়ার বুকে রাজনীতি ঘিরে বিশেষ একটা পড়েনি। পড়েছিল ওয়াগান ব্রেকিং, সিনেমা হলের টিকিট ব্ল্যাক -এইসব নিয়েই। ছিল এলাকা দখলের লড়াই। সেই লড়াইতে রেললাইনের পূবদিক আর পশ্চিমদিকের মধ্যে বোমা পাইপগানের দৌরাত্ম এলাকাকে করে তুলতো অশান্ত। সেই আশান্তির ভয়ে গেরস্ত সন্ধ্যের পর খুব একটা বাড়ির বাইরে যেতে চাইত না। ছোট ছেলেপিলেদের উপর ছিল বাড়ির কড়া আদেশ; লাইটপোষ্টের আলো জ্বলে গেলেই যেন তারা আর বাড়ির বাইরে না থাকে। বাড়িতে ঢুকে পড়ে। রেললাইনের পশ্চিমপারের তুলনায় পূবপারে যেন রাত একটু বেশি তাড়াতাড়িই নামে। পূবপার, পোষাকীনাম দেউলপাড়া। চলতি নাম দেলপাড়া। চটকলের দেহাতী শ্রমিকদের কাছে আবার এই এলাকাটা পরিচিত বেলপাড়া নামে। উচ্চারণের বৈচিত্র যাই থাকুক না কেন, এলাকায় পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষের বাস বেশি। দেশভাগের পর প্রথম উদ্বাস্তু কলোনী এখানেই তৈরি হয়েছিল। বিজয়নগর কলোনী। সেই কলোনী তৈরির সময়কালে বহু রক্ত ঝরেছে। মানুষের প্রাণও গেছে। কিন্তু সেসব গেছে মাথার উপর এক টুকরো ছাদের প্রত্যাশায়। পাকা ছাদের প্রত্যাশা কেউ করেনি। একটু টিনের বা টালির ছাদ- সেটাই ছিল সেসব ছিন্নমূল মানুষদের কাছে যেন এক একটা রাজপ্রাসাদ।
সেই রাজপ্রাসাদে ছেঁড়া কঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার অভ্যাসে সেই মানুষগুলো কিন্তু তখন নিজেদের দিন গুজরান করত না। কথায় বলে না, বাঙালের গোঁ। সেকালের বিজয়নগর কলোনীকে যারা দেখেনি, এই বিজয়নগর কলোনীর মানুষদের যারা জানেনি, তারা বুঝতেই পারবে না, বাঙালের গোঁ -এটা আসলে কী। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাট অভিনেতা। ব্রিটিশের সঙ্গে বন্দুক নিয়ে, বোমা নিয়ে যাঁরা লড়াই করতেন, তাঁদের কত ভাবে যে ভানু সাহায্য করেছিলেন- সেসব তো এখন জানা যাচ্ছে। কিন্তু এই ভানুকে দিয়েই পরিচালকেরা ফিল্মে অভিনয়ের সময়ে সেকালের পূর্ব পাকিস্থান থেকে চলে আসা মানুষদের মুখের ভাষাকে এমন একটা মজার উপকরণ করে তুলে নিজেদের সিনেমাকে বক্স অফিস হিট করিয়েছিলেন, যার জেরে সেই ছিন্নমূল মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াইটারও যেন ঠিক ঠিক মূল্যায়ণ করা হয়নি।
বিজয়নগর কলোনী, এই কলোনী গড়ে ওঠার আগে এই এলাকা ছিল ফাঁকা, নীচু নাবাল জমি। চারিদিকে জল থইথই। সেকালের বৃষ্টির ধরণ ও একালের বৃষ্টির রকমফের দিয়ে মালুম হবে না। সেই জল থইথই জমি সব এমনিই পড়ে থাকত। জমির মালিকদের বেশিরভাগের বাস ছিল রেললাইনের পশ্চিমদিকে। তবে রেল লাইন পাতার আগে, যখন এই রেললাইন ঘিরে পূব-পশ্চিমের ফারাক ছিল না, সে সময়ে বহু বিত্তশালী পরিবার এই পূবপ্রান্তে থাকতেন। তেমন পরিবারের মধ্যে সবথেকে উল্লেখ করবার মত পরিবার ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবার। তাছাড়াও বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু, পয়সাওয়ালা পরিবারের বাস এদিকে ছিল। রেললাইন পাতবার পর লাইনের পূব দিকের মানুষ আর পশ্চিম দিকের মানুষদের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই ক্রমে দানা বাঁধতে থাকল। পূব পারের মানুষেরা দেশভাগের আগে থেকেই নিজেদের ভদ্রাসন বজায় রেখেই গঙ্গার দিকে আরো একটা বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করলেন। আধুনিক নগর সভ্যতার সুযোগ অনেক বেশি রেল লাইনের পশ্চিমপারে। যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ উন্নত। রেল ছাড়াও বাসরুটের সুযোগ এদিকে অনেক আগে হয়েছে। দেশভাগের সময়কালে পশ্চিমদিকে সাধারাণ মানুষদের চলাচলের জন্যে ঘোড়ার গাড়ির রেওয়াজ ছিল।তবে অতি সাধারণ মানুষেরা তো আর সেই ঘোড়ার গাড়িতে চড়বার মতো ট্যাঁকের জোর রাখতো না। ঘোড়ার গাড়ি চড়ত একটু পয়সাওয়ালা মানুষজনেরা। চাকুরিজীবী মানুষ তখন একটু একটু করে বাড়ছে নৈহাটি, ভাটপাড়াতে। চটকলেবাবুর কাজ, মানে যাকে ক্ল্যারিকাল জব বলে আর কী, সে কাজে স্থানীয় বাঙালিরা আস্তে আস্তে আসছে।
চটকলে কুলি মজুরের কাজেও যে বাঙালি আসছে না, তা কিন্তু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, '৪৩ এর মন্বন্তর বাঙালির জনজীবনে যে অবস্থা তৈরি করেছে, তাতে আর পেটের ভাত জোটানোর তাগিদে কাজ ঘিরে বাছাবাছির অবস্থাতে বাঙালি নেই। বিহারী শ্রমিকদের সঙ্গে বাঙালিদের এই চটকলগুলোতে বা চটকল ঘিরে গড়ে ওঠা নানা রকমের ছোটখাট কারখানাগুলোতে বেশ একটা ঠান্ডা লড়াইয়ের অবস্থা প্রায় শুরু হয়ে গেছে।
বাঙালি এই জায়গাটাতে একটু একটু করে পিছিয়েও পড়ছে। বিহারী শ্রমিকের পরিশ্রম করবার যে ক্ষমতা, সেই জায়গাটাতেই বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলমান -একটু পিছিয়েই পড়ছে। চাষের কাজে শ্রম দেওয়া আর চটকলের পরিশ্রম দুটোর মধ্যে যে ফারাক, মাদরাল, ছেরামপুর, দেবক, পানপুর, আওয়ালসিদ্ধি, রামচন্দ্রপুর, বেল্লে -এসব গ্রাম থেকে আসা মানুষেরা প্রথমে ঠিক মতো ঠাওর করে উঠতে পারেনি। বয়লারে কয়লা ঠুসতে গিয়ে কী ধরণের মেহনত লাগে, এসব জায়গার প্রায় দুবেলা পেটপুড়ে না খাওয়া আসলাম, সাদিক, রঘুনাথ, শিবদাসেরা প্রথমে বুঝেই উঠতে পারেনি। ভেবেছিল জমিতে লাঙল দেওয়া, ধান রওয়া, জমি নিড়েন দেওয়া, জল স্যাঁচা -এসব গায়ে গতরে খাটবার কাজ যখন হাসিমুখে তারা সারা বচ্ছর ধরে করে, তবে চটকলের কাজ পারবে না কেন? মাঠের কাজের থেকে কী আর কঠিন হতে পারে এই পাটকলের কাজ?
পাটকলে সাহেবসুবোর তখনও বেশ আধিপত্য। যদিও 'বাবু' হিসেবে আশেপাশের বাঙালিরা একটু আধটু ঢুকছে। যদিও সেসব বাবুদের মধ্যে আবার বামুনগিরির দাপট ছিল ভয়ঙ্কর। ভাটপাড়া লাগোয়া গ্রাম থেকে তখন সবে বাঙালি আসছে চটকলের শ্রমিক হতে। তারা জানে না কোনও কলে কাজ করবার রকম সকম। জানে না কল চালাবার কৌশল। মাটি থেকে কৃষকের বিচ্ছিন্ন হওয়ার শুরুর সময় সেটা। যুদ্ধের বাজারে জিনিষপত্রের যা দাম মধ্যবিত্তেরই পেট চালানো দায়। তা গরীবগুর্বোর অবস্থা তো সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। নৈহাটি, হালিসহর, গরিফা, ভাটপাড়া, আতপুরের মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি, যাদের চটকলে চাকরি ঘিরে একটা বড় রকমের নাক সিঁটকোনো ব্যাপার ছিল, তাঁদের সেই ট্যাবু তখন পেটের জ্বালায় একটু একটু করে কাটতে শুরু করেছে।
বেশিরভাগ বামুনদের মধ্যে সময়ের সঙ্গে তল রেখে সময়কালের পড়াশুনোর দিকে তখনও খুব একটা আকর্ষণ তৈরি হয়নি। নৈহাটি, বিশেষ করে ভাটপাড়ার একটা অংশের বামুন ঠাকুরেরা চালকলা বাঁধা বিদ্যেতেই নিজেদের জুতে দিয়ে ভেবেছিল, এইভাবেই কেবল নিজের জীবনই নয়, নাতিপুতিদেরও জীবনটা কেটে যাবে। এভাবে যে কাটবে না, সেটা বুঝতে অনেকটা সময়ই তাদের চলে গেল।