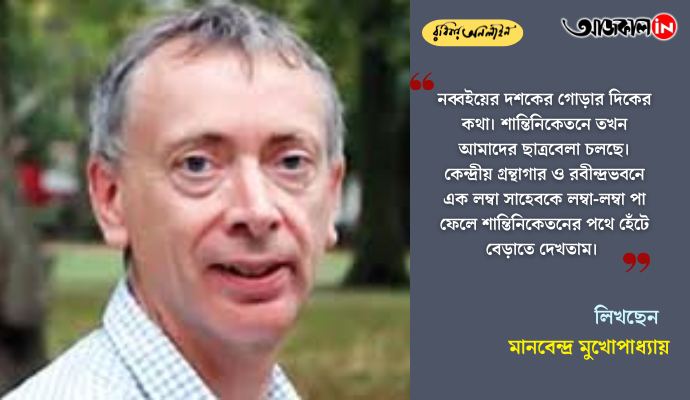
রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সৃষ্টি আজও দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে কতটা আকর্ষণের, কতোটা সম্মোহনের শক্তি নিয়ে চিরজাগরুক হয়ে রয়েছে তার প্রমাণ সদ্য প্রয়াত উইলিয়ম রাদিচে-
নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকের কথা। শান্তিনিকেতনে তখন আমাদের ছাত্রবেলা চলছে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রভবনে এক লম্বা সাহেবকে লম্বা-লম্বা পা ফেলে শান্তিনিকেতনের পথে হেঁটে বেড়াতে দেখতাম। দেখতে পেতাম তাঁকে লাইব্রেরিতে রাশিকৃত বইপত্রের মধ্যে ডুবে থাকতে। বিশ্বভারতীতে দেশ-বিদেশের গবেষকদের আনাগোনা তখন বেশ সুলভই ছিল। মার্টিন কেম্পচেনদা তো এখনও আছেন। কিছুদিনের জন্য একসময় দেখা মিলল জো উইন্টারের। পাঠভবনে তাঁকে ক্লাস নিতেও দেখেছি। সাদাচামড়ার মোহ আলাদা করে সে-বয়সেও মোহিত করেনি। তবে ‘বিশ্বভারতী’-তে তো এমনই হওয়া উচিত মনে করে একরকম ভাললাগা হয়তো ছিল এইসব বিদেশি গুণীজনের প্রতি। বিশেষ করে ওঁরা তিনজনই যখন রবীন্দ্র-অনুবাদক, তখন তাঁদের সম্পর্কে বাড়তি একটা কৌতূহল ছিল তা বলাই যায়।
গত ১০ নভেম্বর রাদিচের প্রয়াণ-সংবাদ পেয়ে সেসময়ের নানারকম স্মৃতি ভেসে উঠছিল মনে। অনেকপরের কথা। ২০০৯ সাল বোধহয়। সম্ভবত তখন উনি গীতাঞ্জলির ‘নিউ ট্রানশ্লেসন’ নিয়ে কাজ করছেন। রাদিচেকে দেখতাম রবীন্দ্রভবনে পৌঁছে যেতেন বেলা দশটার মধ্যে। সারাদিন নিমগ্ন হয়ে তাঁর কাজ করা দেখেছি। মনে হতো, সাহেব খুবই ডিসিপ্লিনড তাঁর কাজের ব্যাপারে। তবে উইলিয়ম রাদিচের সঙ্গে কখনওই তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার তৈরি হয়নি। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে ওঁর সঙ্গে একবার জমাটি আড্ডা দিয়েছি, এইমাত্র। সেবার রাদিচের একটা বক্তৃতা ছিল বাংলা বিভাগে। তারপর বিভাগীয় প্রধানের ঘরে বসে চা খেতে খেতে একটা মজার খেলা শুরু করলেন উনি। কয়েকটা কাগজের টুকরো নিয়ে একটা করে পঙ্ক্তি উনি লিখে দিচ্ছেন আমাদের জন্য। তারপর ছন্দ ও মাত্রা বজায় রেখে বাকি তিনটে করে লাইন আমাদের রচনা করতে হবে। সেটিকে আবার ইংরেজি অনুবাদে তুলে আনার চেষ্টাও করতে বললেন! ভদ্রলোকের ধ্যানজ্ঞান যে ‘অনুবাদ’, সেইটাই যেন মালুম হল আমাদের। প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘মেঘনাদবধকাব্য’ না কি রবীন্দ্রকাব্য— অনুবাদের ক্ষেত্রে কোনটা বেশি চ্যালেঞ্জের কাজ? তৎক্ষণাৎ রাদিচে বলেন, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ। কারণটাও ব্যাখ্যা করলেন। মধুসূদনের মহাকাব্যের অর্থ অভিধান খুললে মিলতে পারে, কিন্তু ব্যঞ্জনা-অর্থ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেকবেশি।
অনুবাদ তো জীবনে কম করেননি রাদিচে! শুধু রবীন্দ্র-অনুবাদ নয়, পুরুষোত্তম লালের ইংরেজি ‘মহাভারত’ থেকে কিছু কাহিনি নিয়ে একরকম পুনর্কথন করেছিলেন রাদিচে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামি পুরাকথাও অনুবাদ করেছেন কিছু কিছু। তাঁর কোনও কোনও অনুবাদ নিয়ে আমাদের অনেকেরই অস্বস্তি হয়েছে। কিন্তু ওরই মধ্যে বোঝবার চেষ্টা করতাম একজন বিদেশি কীভাবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মর্মস্থানটিকে স্পর্শ করার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন! তখন কি আর জানতাম, রাদিচের ইংরেজি গীতাঞ্জলির পুনঃঅনুবাদের প্রকল্পের একটি দিক নিয়ে সমালোচনা করে একসময় আমাকেও প্রবন্ধ লিখতে হবে? মনে হয়েছিল, স্বজাতীয় রোদেনস্টাইন আর আইরিশ ইয়েটসের প্রতি একটু কি বেশিই নিষ্করুণ সমালোচনা করে ফেললেন রাদিচে তাঁর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির পুনঃঅনুবাদের ভূমিকায়? তাতে একটা লাভ অবশ্য হয়েছিল। রাদিচে তাঁর ওই অনুবাদের পরিশিষ্ট ভাগে রীতিমতো একটা টেবিল তৈরি করে যতিচিহ্ন-সমেত রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে ইয়েটসের হস্তক্ষেপের একটা বেশ পাকাপোক্ত হিসাব দাখিল করেছিলেন। সংখ্যার দিক থেকে সেটা বেশ কমই বলা যায়। সাদাচামড়ার প্রতি বিশেষ কোনও পক্ষপাত অন্তত এক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে দেখতে পাইনি।
তবু তর্ক একটা জমছিল ওই অনুবাদ-বইটি পড়তে পড়তে। সে প্রায় বছরদশেক আগের কথা। আক্ষেপ এই যে, আমার উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে রাদিচের কী বক্তব্য হতে পারত তা আর জানা হল না। ততদিনে মর্মান্তিক এক পথ-দুর্ঘটনায় উনি জড়বৎ হয়ে পড়েছেন। রাদিচের মতো সদাকর্মচঞ্চল মানুষের এই পরিণতির কথা শুনে কষ্ট হয়েছিল বেশ। সে যাই হোক, আমার মনে যে তাঁর গীতাঞ্জলির পুনঃঅনুবাদ নিয়ে তর্ক জমেছিল তা তাঁর অনুবাদ নিয়ে ততটা নয়; আমার তোলা তর্কটা ছিল রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির কবিতাগুলির বিন্যাসের প্রশ্নে রাদিচের ‘হাইপোথেসিস’ নিয়ে। আর-পাঁচটা অনুবাদের থেকে রাদিচের ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনুবাদকে আলাদা করে বিচার করতে হবে, কারণ এই অনুবাদ শুধু অনুবাদের লক্ষ্যেই পরিকল্পিত নয়। ২০১১ সালে ‘পেঙ্গুইন বুকস’ থেকে নতুন দিল্লিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে একযোগে প্রকাশিত তাঁর অনুবাদগ্রন্থটির আখ্যাপত্রে উল্লেখ আছে: ‘Gitanjali Song Offerings/ Rabindrnath Tagore/ A New Translation by Wiliam Radice/ with an Introduction / and a new text of Tagore’s translation/ based on his manuscript’। নতুন কথাটা হল তিনি এই অনুবাদে গড়ে তুলতে চাইছেন একটা ‘new text’; যার ভিত্তিমূলে রয়েছে কিনা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির মূল পাণ্ডুলিপি; ‘রোদেনস্টাইন ম্যানুস্ক্রিপ্ট’ নামে যা রবীন্দ্রচর্চাকারীদের কাছে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ এই পাণ্ডুলিপি রোদেনস্টাইনকে উপহার দিয়েছিলেন বলেই তার এরকম নাম হয়েছে। এতে কবিতা রয়েছে মাত্র তিরাশিটি। আমাদের চেনা ইংরেজি গীতাঞ্জলির সঙ্গে কবিতাগুলির বিন্যাসে তার অনেক তফাত আছে। এ-বিষয়ে রাদিচের বক্তব্য বোঝবার জন্য তাঁর পূর্বোল্লিখিত ওই অনুবাদের বইটির দীর্ঘ চুরাশি পৃষ্ঠার ভূমিকা আর ‘দ্য ডেইলি স্টার’ পত্রিকায় প্রকাশিত রিফাত মুনিমের নেওয়া ২০১২ সালের সাক্ষাৎকারটি মিলিয়ে পড়া দরকার। স্বল্পকথায় বলা যায়, রাদিচে মনে করেন ওই পাণ্ডুলিপিতেই অনূদিত কবিতাগুলির ক্রমবিন্যাস, পঙ্ক্তি-বিন্যাস এবং যতিচিহ্ন-প্রয়োগ ছিল যথাযথ। তাঁর অভিযোগ, ইয়েটস কিংবা রোদেনস্টাইন, অথবা উভয়ে, ভারতীয় সাংগীতিক চেতনা না বুঝে, বইটির শিরোনামে ‘গীত’ কথাটির দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে, বাইবেলোচিত যতিবিন্যাস প্রয়োগ করে, কবিতাগুলির পর্যায়ক্রমিক লিরিকধর্ম ক্ষুণ্ণ করে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি বইটার বারোটা বাজিয়েছেন! তাঁর মতে ‘রিয়্যাল গীতাঞ্জলি’ যদি বলতে হয় তবে তা হল পাণ্ডুলিপির সেই প্রথম খাতাখানা, যেখানে ছিল মোটে ওই তিরাশিটা কবিতা। শেষ কবিতার নীচে সেখানে ছিল একটি সমাপ্তিসূচক চিহ্ন।
প্রশ্ন হল, রাদিচের হাতে কি এমন কোনও নিশ্চিত প্রমাণ ছিল যাতে রোদেস্টাইন-ইয়েটসকে এ-বিষয়ে কাঠগড়ায় তোলা যায়? উত্তর হচ্ছে ‘না’। ২৩ অক্টোবর ১৯১২ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রোদেস্টাইনের যে-চিঠির উপর তিনি খানিকটা ভিত্তি করেছেন তাতেও অভিযোগটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না। সেজন্যই রাদিচে ওই দীর্ঘ ভূমিকার একজায়গায় লিখেছেন, ‘আই ডাউট ইট।’ বাকি রইল তাঁর সাহিত্যগত অনুমান। সংক্ষেপে বললে সেক্ষেত্রে রাদিচের বক্তব্য হল, পাণ্ডুলিপির বিন্যাস গ্রন্থরূপে এমনভাবে বদলে ফেলা হয়েছে যে গানের মাঝে-মাঝে এসে পড়েছে নিতান্ত ‘না-গান’ কবিতার এক-একটা কথার ‘ব্লক’। তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে যদি রোদেনস্টাইন-ইয়েটসের কোনও ধারণা থাকত তাহলে তাঁরা এটা কখনওই করতেন না।
এর প্রতিযুক্তি হিসেবে অবশ্য অনেক কথাই বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেছেন গদ্যকবিতা হিসেবে। ফলে মূলে কোনটি লিরিক ছিল আর কোনটি সনেট; কোনটি গান আর কোনটি নিতান্ত কবিতা — অনুবাদে তার চিহ্ন কার্যত মুছে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। মুছে না দিলে দশটি উৎস থেকে নেওয়া গান-কবিতাগুলি একঠাঁই হতই-বা কীভাবে? বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকাব্য তো বলতে হয় এই ইংরেজি গীতাঞ্জলিকেই, পরে ‘পুনশ্চ’-এর ভূমিকায় সেকথা প্রকারান্তরে কবুলও করেছেন কবি। দ্বিতীয়ত, কথা আর গান ‘ভারতীয় সংগীত’-এর নিরিখে পরস্পরের বিবাদী বলে মনে করেছেন রাদিচে। কিন্তু ভারতীয় মার্গসংগীত সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য হলেও বাংলা গান সম্পর্কে কথাটা খাটে না। কীর্তনের আখরকে রবীন্দ্রনাথ ‘কথার তান’ বলেছেন একাধিকবার। ‘সংগীতচিন্তা’ বইটিতে বস্তুত কোথাও বাণীর সঙ্গে সুরের আড়াআড়ির সম্পর্কের কথা তিনি বলেননি। ‘ভারতীয় সংগীত’ নামক একটি বর্গের বন্ধনীতে যাবতীয় ভারতীয় গান অভিন্ন বৈশিষ্ট্যে আঁটে না।
তাহলে রাদিচে এই যুক্তিগুলি খাড়া করছেন কেন? চুরাশি পৃষ্ঠার দীর্ঘ ভূমিকায় উইলিয়ম রাদিচে লিখেছেন, তিনি বাংলা ভাষা জানেন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির যেগুলি গান হিসেবে গীত হয় তার সুরের স্মৃতিও তাঁর মনে অনুরণিত হয়ে চলে। কথাটা ঠিক। যাঁরই স্মৃতিতে জাগ্রত হয়ে আছে রবীন্দ্রসংগীতের শ্রুতি-অভিজ্ঞতা, তাঁরা সবাই কথাটা মানবেন। কবিতা হিসেবে কোনও গান পড়বার সময় তিরতির করে সুরের কাঁপন আমরা সবাই টের পাই। গীতাঞ্জলির কবিতা-গানের ক্ষেত্রেই শুধু এরকম হয় তা নয়। সব গানের ক্ষেত্রেই কথাটা খাটে। সুরের সেই মোহপাশ কাটিয়েই আমাদের বাণীরূপের অনুবাদে প্রবৃত্ত হতে হয়। কিন্তু রাদিচে ধরলেন স্বতন্ত্র পথ। বাংলা-জানা রাদিচে আসলে গানগুলির শ্রুতি-অভিজ্ঞতারই অনুবাদ করছেন। ফলত, উদাহরণ হিসেবে, ‘জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো/সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো’ গানটির স্থায়ী অংশের রাদিচে-কৃত অনুবাদটা দাঁড়ায় এইরকম:
When the life in me dries up
Come with a stream of kindness
When the life in me dries up
Come with a stream of kindness
When the sweetness in me disappears
Come with a song’s nectar
When the life in me dries up
Come with a stream of kindness
এখন এই গানের একটা রেকর্ড চালিয়ে অনুবাদটি লক্ষ করলে দেখা যাবে গানটির চারটি তুক (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ) অনুসারে এখানে অনুবাদ করা হয়েছে। অন্তরা এবং আভোগ অংশটিকে রাখা হয়েছে বাঁকাহরফে, যাতে তুকের তফাত স্পষ্ট হয়। আর গানটি গাইবার সময় যে অংশগুলি ফিরে ফিরে আসে, সেই ফেরতা অংশগুলিও রাখা হয়েছে যথাস্থানে। গানটির ধ্রুবপদ বা ধুয়োও তার যথাস্থানে অনূদিত হয়েছে। ধ্রুবপদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তুক অংশের মাঝে কোনও স্পেস দেওয়া হয়নি। আর ধ্রুবপদ সবসময়ই রাখা হয়েছে সোজাহরফে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু অনুবাদ করবার সময় মনে রাখেননি যে এটি মূলে একটি গান। তিনি এর সহজ-সোজা অনুবাদ করেছেন: ‘When the heart is hard and parched up come upon me with a shower of mercy.’
কেন রাদিচে চুরাশি পৃষ্ঠার দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করে ইংরেজি গীতাঞ্জলির বিন্যাসের ত্রুটি নিয়ে রোদেনস্টাইন ও ইয়েটসকে অভিযুক্ত করবেন তার একরকম কার্যকারণ বোধহয় এতদূরে এসে অনুমান করা যায়। মূলে যা গান, তার থেকে সুর বাদ দিলে তা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে বলে রাদিচের ধারণা ছিল। প্রজাপতির পাখনা ছেঁটে নিলে তার যে দশা হয়, গান থেকে সুর ছিনিয়ে নিলেও তার অবস্থা হয় অনুরূপ। তিনি ইংরেজি গীতাঞ্জলির যেগুলি গান— সেগুলির গীতরূপেরই অনুবাদ করেছেন। আর তার জন্যই সম্ভবত তাঁকে বিস্তার করতে হয়েছে দীর্ঘ এক তত্ত্বপ্রস্তাব। তাঁর এই তত্ত্বপ্রস্তাব নিয়ে তর্ক তোলাই যায়। সেইসঙ্গে প্রয়োজন, সহানুভূতির সঙ্গে অনুবাদকের বাংলা সংগীত-প্রেমিক সত্তাটিকেও অনুভব করা।