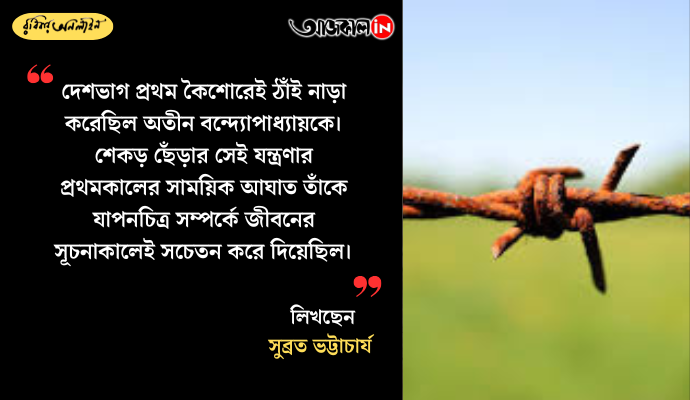
দেশভাগ প্রথম কৈশোরেই ঠাঁই নাড়া করেছিল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শেকড় ছেঁড়ার সেই যন্ত্রণার প্রথমকালের সাময়িক আঘাত তাঁকে যাপনচিত্র সম্পর্কে জীবনের সূচনাকালেই সচেতন করে দিয়েছিল। জীবনের অভিজ্ঞতাতেই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিখিয়েছিল জীবন যন্ত্রণা অতিক্রমেরর মহামন্ত্র। তাই অতীনের জীবন এবং সৃষ্টিতে একটি বারের জন্যে পথভ্রষ্ট পথিকের বাখোয়াজি নেই, আছে বাসায় ফেরা ডানার শব্দ। দেশভাগ- দেশত্যাগের গভীর যন্ত্রণার অবয়ব ভেদ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভবের পটভূমিকা নির্মাণের ভিতর দিয়ে যে 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' অতীতের অনিঃশেষ যাত্রা, তেমন পথশ্রমের নিদর্শন আমাদের বাংলা সাহিত্যই কেবল নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না।
অতীন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার সন্তান। তাঁর শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে অবিভক্ত ঢাকা জেলার রাইনাদি গ্রামে(এই গ্রামটি এখন নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত)। দেশভাগের কালে অতীনের নিজের গ্রাম রাইনাদিতে কোনও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়নি। সংঘর্ষের আতঙ্কের পরিমন্ডলে অতীনের পরিবারের দেশত্যাগ। এ সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে অতীন নিজেই বলেছেন; আমি এসেছি দেশত্যাগের কিছু পর। সেই সময়ে আমার ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। তখনও পর্যন্ত ওপারে টেস্ট পরীক্ষা দিলে এপারে ফাইনাল দেওয়া যেত। দেশভাগের খবর চাউর হতেই আমাদের বিশাল পরিবার, বাবা, জ্যাঠা, কাকা, কাকিমা, জ্যেঠিমা, ভাইবোন ভাগ ভাগ করে এপারে আসতে লাগল(বইয়ের দেশ -এপ্রিল - জুন, ২০১২ তে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার। পৃষ্ঠা-১০১)। পূর্ববঙ্গ থেকে এপার বাংলাতে এসে অতীনের পরিবার প্রথম বসতি স্থাপন করেন মুর্শিদাবাদ জেলাতে। সেখানে তাঁদের এক কঠিন জীবনসংগ্রাম শুরু হয়। অতীনের এবং তাঁর পরিবারের এই লড়াইয়ের পর্বের ছবি মুদ্রিত রয়েছে তাঁর 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে। ঠাঁই গড়তে চাই ট্যাঁকের জোর। তাই জীবনের শুরুতেই পেটের তাগিদে জাহাজের চাকরি নিয়ে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়ে পড়েছিলেন অতীন। বহু পথ অতিক্রম করে শেষে কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতার সামনে দাঁড়িয়ে ডাঙায় থিতু হন তিনি। তারপর নানা ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ইস্কুল থেকে কারখানা, খবরের কাগজের অফিস -অনেক জায়গায় পেশার তাগিদে গেলেও, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে' র তাগিদ যেন অতীনকে চিরদিন তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। এইসব অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর সঙ্গে তুলনা চলে গৌরকিশোর ঘোষের। আর অতীনের জীবনের মহত্তম সৃষ্টি দেশভাগের যন্ত্রণার দলিল নির্মাণের সূচনা পর্বে গৌরকিশোরের 'প্রেম নেই' , 'জল পড়ে পাতা নড়ে' তাঁকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল।
দেশভাগ-দেশত্যাগের আখ্যান নির্মাণের আদিপর্ব জুড়ে আছে অতীনের শৈশব-কৈশোরের সোনালি দিনগুলির অব্যর্থ টিপছাপ। শৈশবের উপবন থেকে বিচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা আমৃত্যু ধারণ করেছিলেন অতীন। সেই যন্ত্রণার অভিব্যক্তি তাঁর দেশভাগের আখ্যানপর্বের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র দেশভাগের যন্ত্রণাবিদ্ধ সৃষ্টিতেই নয়, অতীনের সামগ্রিক রচনাতেই প্রকৃতি একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে। অতীনের এই প্রকৃতিপ্রমের নিরিখে তাঁর সৃষ্টির তুলনা চলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' বা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'তৃণভূমি' র সঙ্গে। দেশভাগের যন্ত্রণার ট্রাজিক উপাখ্যান 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' সম্পর্কে পূর্বোল্লিখ সাক্ষাৎকারে অতীন বলেছেন; বাধ্য হয়ে দেশত্যাগের জন্য অন্যান্য উদ্বাস্তুদের মতো আমিও মুসলিমদের দায়ী করতাম। বেশি বেশি করে বিশ্বাস করতাম গ্রাম লুন্ঠন, নারী অপহরণ, আরও সব নানান খারাপ ঘটনার কথা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অনৈতিহাসিক ভাবনা থেকে সরে আসতে দ্বিধা করেননি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের রাইনাদি গ্রামে তো ওই ধরনের একটিও ঘটনা ঘটেনি। একটা আতঙ্কের ভূগোল নির্মিত হয়েছিল সেইসময়ে গোটা পূর্ববঙ্গ জুড়ে। তৈরি হয়েছিল একটা অবিশ্বাসের বাতারণ। সেই নষ্ট সময় আর ত্রস্ত সংস্কৃতির শিকার হয়ে অতীনের পরিবারের দেশত্যাগ। সময়ের উত্তরণে মানুষ অতীনের চিন্তার পরিমন্ডলকে ছেয়ে দিয়েছে রাইনাদির প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের স্নেহচ্ছায়ার উত্তাপ। বিদ্বেষ, গুজব, অবিশ্বাসকে অতিক্রম করে পরিণত অতীনের কাছে সবথেকে বড়ো হয়ে উঠেছিল রাইনাদির প্রতিবেশী মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনদের ভালোবাসার কথা, স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা-আত্মীয়তার কথা। এই মানসিক নিরপেক্ষতা দেশত্যাগী মানুষদের সিংহভাগের ভিতরেই দেখতে পাওয়া যায় না। আর এই মানসিক নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরে নিজেকে স্থিত করেই অতীন হাত দিয়েছিলেন তাঁর চোখের জলে ভেজা আখ্যানপর্ব 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' তে। আমাদের দুর্ভাগ্য কিছু কিছু কথাকার অতীতেও ছিলেন, আজও আছেন --যাঁরা মানসিক নিরপেক্ষতায় স্থিত হওয়ার তোয়াক্কা করেন না। পক্ষপাতিত্বমূলক মানসিক অবস্থানের ভিতরে দাঁড়িয়ে নির্মাণ করেন তাঁদের সৃষ্টিকে। ফলে সেই সৃষ্টি হয়ে ওঠে একদেশদর্শী দোষে দুষ্ট। অতীনের সামগ্রিক সৃষ্টিতে একটিবারের জন্যেও এই একদেশদর্শীতার দোষে দুষ্ট হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না।
আলোচ্য সাক্ষাৎকারেই অতীন বলেছেন, ওখানে যেসব চরিত্র আছে তাঁরা কেউ কেউ রক্তের সম্পর্কের, বাকিরা পাশের বাড়ির অথবা আমার গ্রামের, পাশের গ্রামের লোক, প্রকৃতি আমার আশেপাশের গ্রামের। এখনও চোখ বুজলে গোটা অঞ্চলটা আমি দেখতে পাই। তরমুজ খেত, সোনালী বালির চর, পুকুরপাড়ে নিমগাছ, নোনাধরা ইটের প্রাচীন মসজিদ। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনও লেখকের কাছে নিজের কৈশোর কালটা ভীষণ জরুরি। দরিদ্র প্রতিবেশী ঈশম শেখকে দিয়ে অতীন তাঁর ' নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' মহাকাব্যের শুরু করেছেন, শেষও করেছেন এই ঈশমকে দিয়েই। একটিবারের জন্যেও ঈশমের যাপনচিত্রে তাঁর ধর্মপরিচয়কে জাবদা ভাবে তুলে ধরে একটা অতিনাটকীয়তার পরিবেশ রচনা করেননি অতীন। ঈশম এক ভূমিহীন, কর্মহীন চরিত্র। এমনতরো চরিত্র সময়ের কষ্টিপাথর অতিক্রম করে আজও আমাদের চোখের সামনে অনেক সময়েই এসে হাজির হয়। এই উপন্যাসের শেষে এক দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে ঈশমের মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা। "তখন মাঠ থেকে কিছু লোক ছুটে আসছে। ওরা এসে খবর দিল ঈশম তরমুজের জমিতে মরে পড়ে আছে। কখন সে মরেছে কেউ বলতে পারে না। জমিতে তরমুজ এবার ভালো হয়নি। শুধু পাতা সার! দুদিনের ওপর হবে জমিতে কেউ তরমুজ তুলতে যায়নি। কেউ জানে না কখন থেকে ঈশম পাতার নিচে মরে পড়ে আছে। এই জমির এক অংশে ঈশমের জন্যে একটু মাটি চেয়েছিল সামু। এই জমির নিচে ঈশম চুপচাপ শুয়ে থাকবে আবহমানকাল। নানারকম ঘাস জন্মাবে কবরে। ফুল ফুটবে ঘাসে। ঈশমের এই কবর থেকেই বাংলাদেশের ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।
ঈশমের কবরে সামু এবার একটা ইস্তাহার লিখে রেখে দিল। ইস্তাহারটার নাম বাংলাদেশ। তারপর ওকে শুইয়ে দিল। নতুন পাজামা পাঞ্জাবি। সাদা দাড়ি ঈশমের। সে লম্বা হয়ে কবরে শুয়ে আছে। ভূমিহীন অন্নহীন ঈশমের কানে কানে মাটি দেওয়ার আগে বলার ইচ্ছা হল, কিছুই করতে পারিনি এতদিন। স্বাধীনতার মানে বুঝিনি। আপনাকে দেখে মানেটা আমার পরিস্কার হয়ে গেল। তারপর সে ঈশমের কবরে মাটি দিতে দিতে বলল, যার মাটি পেলে আপনি সবচেয়ে খুশি হতেন চাচা, সে নেই। সে থাকলে তাকে বলতাম, তুমি এসে একটু মাটি দিয়ে যাও বাবু। ওঁর আত্মা বড়ো শান্তি পাবে। সে বেইমান চাচা। আপনাকে ফেলে সে চলে গেছে। লিখে গেছে জ্যাঠামশাই, আমরা হিন্দুস্থানে চলে গেছি। যেন জ্যাঠামশাই ছাড়া তার বাংলাদেশে কেউ নেই। তারপর থেকেই মাঝেমাঝে আশ্বিনের কুকুর ঈশমের কবরের পাশে ঘোরাফেরা করলে টের পাওয়া যায় মহাবৃক্ষে সেই ক্ষত ক্রমে আবার মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অর্জুন গাছটা আরো বড়ো হচ্ছে। ডালপালা মেলে সজীব হচ্ছে।" এই কান্না যেন আমাদের নিয়ে চলে নরেন্দ্র নাথ মিত্রের কালজয়ী ছোটগল্প 'পালঙ্ক' এর সেই আপ্ত উচ্চারণে;" গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্থানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে ফতি, গোরস্থান আছে।"
ঈশমের চরিত্র নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে আমরা পাই ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী হিসেবে। অভিজাত হিন্দু পরিবারে বিশ্বস্ত মুসলমান কর্মচারী অবিভক্ত বাংলার একটি দস্তুর ছিল। এই দস্তুরটিতে পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুরা যতো না অভ্যস্থ ছিলেন, তার থেকেও বেশি সহজাত ছিলেন পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা। সূচনা পর্বের বিনির্মানে আমরা পাই তেলেজলে বেড়ে ওঠা ঈশমকে। যে ঈশম ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী হিশেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছিল একটা শক্ত বনিয়াদের উপরে। মাটিতে পা দিয়ে আসমানের দিকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ঈশান কিন্তু নিরন্ন ছিল না ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী হিসেবে। ঠাকুরবাড়ির মানুষজনেদের ভালোবাসা থেকেও সে ছিল না বঞ্চিত। তাঁর বঞ্চনার শুরুয়াত কিন্তু সেই পূর্ববঙ্গ কেবলমাত্র মুসলমানদের আবাসভূমি হিশেবে 'পাকিস্থান' রূপে স্বীকৃত হওয়ার পরই ঘটতে শুরু করল। মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে অখন্ড ভারতকে টুকরো করে মুসলমানদের আবাসস্থল পাকিস্থান যাঁরা তৈরি করলেন, সেই রাজনৈতিক মুসলমানদের একাংশের হাতেই গেল ঈশমের তরমুজ খেত, গেল তার জমি জিরিতের শেষ আশাটুকু। অতীন তাঁর মহাকাব্যের শেষে ঈশমের প্রাণাধিক প্রিয় তরমুজ খেতের ভিতরেই দু’তিন দিনের লাশ হয়ে ঈশমের পড়ে থাকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানেই 'পাকিস্থানে' র 'ফাকিস্থান' হয়ে ফুটে ওঠার হিরন্ময় পাত্রে ঢাকা নয়, কয়লায় কালো সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। এই পর্যায়ে এসে অতীনের 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' র প্রত্যয় বাংলা সাহিত্যের ঝড়ের পাখি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কালজয়ী সৃষ্টি 'খোয়াবনামা' অন্তিম উপলব্ধির সঙ্গে কোথায় যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।